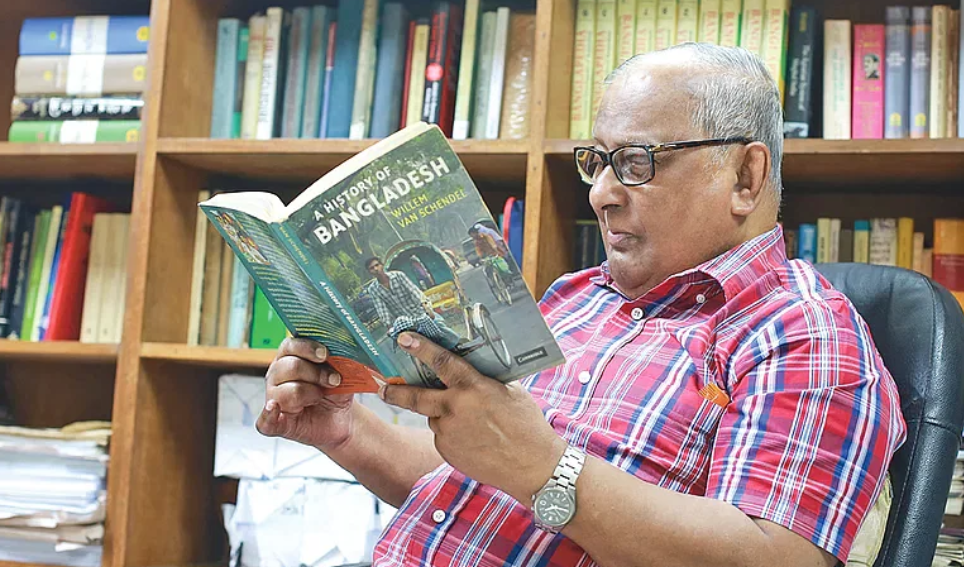
আকবর আলি খান বহুমাত্রিক সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। সাধারণত দুই ধরনের সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ দেখা যায়। একদল নিজস্ব সংকীর্ণ গণ্ডিতেই বিচরণ করতে ভালোবাসেন, তাঁদের আমরা স্পেশালিস্ট বলি। আরেক দল আছেন, তাঁরা নিজস্ব সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে আরও বহুবিধ ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখান, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। আকবর আলি খান ছিলেন দ্বিতীয় ধারার সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসাহ প্রসারিত হয়েছিল বনলতা সেন থেকে দারিদ্র্য বিশ্নেষণ অবধি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশিষ্টতা খোঁজার পাশাপাশি পরার্থপরতার অর্থনীতি অনুসন্ধান, সুশাসন সম্পর্কিত ফ্রেন্ডলি ফায়ার বইটি থেকে আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি। তবে বহুবিধ বিষয়ে বিচরণ করলেও, তিনি প্রথমত ও প্রধানত ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। ইতিহাসচিন্তা তাঁর সমাজচিন্তাকে ধারণ করেছে। তাঁর অর্থনৈতিক বিশ্নেষণকে সমৃদ্ধ করেছে। এসবই জানা কথা। আমি এখানে কয়েকটি বইয়ের সূত্রে, যে সুবাদে আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা করার, সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব।
১. নেশনের প্রাক-ইতিহাস
প্রথমেই আসি তাঁর সবচেয়ে মৌলিক ও সুবিদিত কারণে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ডিসকভারি অব বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। বইটির শিরোনাম শুনে পাঠকমাত্রেরই মনে পড়তে পারে ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া শীর্ষক জওহরলাল নেহরুর বইটির কথা। জওহরলাল নেহরু লিখিত বইটি ছিল মূলত বর্ণনামূলক এবং সময়ের ধারাবাহিকতাকে ধরার চেষ্টা। পক্ষান্তরে আকবর আলি খানের ডিসকভারি অব বাংলাদেশ মূলত বিশ্নেষণাত্মক এবং তাঁর অভিনিবেশ ছিল- কী করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করা যায়।
বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গকে ঘিরে যে ভূখণ্ড বা তার অধিবাসী যারা, তাদের যে বৈশিষ্ট্য, তা তাদেরকে ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে আলাদা করে। শুধু তাই নয়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড-ভূগোলের অধিবাসীদের থেকেও তাদের বিশিষ্ট করে। সেই বিশিষ্টকরণের সূত্র খুঁজছিলেন আকবর আলি খান। সেদিক থেকে এটি একটি চমৎকার পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণজাত গবেষণা গ্রন্থ। এখানে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল কয়েকটি। একটি হচ্ছে- এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সবলতা ও দুর্বলতার দিক কী কী। তিনি সেই ক্ষেত্রে দেখেছিলেন- এই ভূখণ্ড লেস রেজিমেন্টেড, কম শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি যেটা বলেছেন, বাংলাদেশের গ্রাম হচ্ছে ওপেন জিওগ্রাফিক্যাল সেটেলমেন্ট। এর বিপরীতে উত্তর ভারতীয় গ্রামগুলোকে বলেছেন ক্লোজড জিওগ্রাফিক্যাল সেটেলমেন্ট। সেই সমস্ত গ্রামে ঢুকতে গেলে একটা সীমানা প্রাচীর পেরোতে হয়। বাউন্ডারি দেওয়া। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের তুলনাতেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে মনে হয়েছে, সেগুলো অনেক ছড়ানো ছিটানো। সেখানে অনেক ফাঁকফোকর রয়ে গেছে, ফাটল রয়ে গেছে। তিনি বলছেন, এর কারণ বোধকরি এই যে, এই গ্রামগুলো কোনো সবল ক্ষমতাকাঠামোর ভেতর কখনও ছিল না বা মাথা নত করেনি। বরং অন্যান্য জায়গা থেকে অত্যাচারিত বা এক্সক্লুডেড হয়ে যারা এই ভূখণ্ডে এসেছে, তারা সহজে আশ্রয় নিতে পেরেছে। জিওগ্রাফির সঙ্গে সোশ্যাল এক্সক্লুশন এবংপলিটিক্যাল ইসলামের একটি আন্তঃসংযোগ তিনি স্থাপন করেছেন। এই সূত্রে তিনি আরও লক্ষ্য করেন, ইসলাম যে এই পূর্ববঙ্গে একাদশ শতক থেকে বিস্তার লাভ করেছিল, তার পেছনে মূলত কোন কোন উপাদান কাজ করেছে। এ নিয়ে আলাদা করে তাঁর আরেকটি বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম ‘বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য :একটি ঐতিহাসিক বিশ্নেষণ’।
সেখানে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য ছিল- অসির বলে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। তখনকার যুগে বাংলার, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনপদ বলে কিছু ছিল না। এটি ছিল মূলত প্রত্যন্ত এলাকা, যেটিকে এগ্রারিয়ান ফ্রন্টিয়ার বলেছেন তিনি। এক কথায়- জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের শুরুতে আমরা যে রকম বর্ণনা পাই :জঙ্গলাকীর্ণ একটি ভূখণ্ড এবং সেখানে মূলত যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বা নির্যাতিত অথবা সহায়সম্বলহীন, মরিয়া- ডেসপারেট, সেই জনগোষ্ঠীই কেবল বাস করতে উৎসাহী হবে। এই ডেসপারেট জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের তুলনামূলক অনগ্রসর, বিপৎসংকুুুল, জঙ্গলাকীর্ণ, নদীপরিকীর্ণ, শ্বাপদসংকুুল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের জীবনধারণের জন্য বসবাসের স্বার্থে সেই জঙ্গল কেটে জনপদ গড়েছে। এই বন কেটে বসত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন একাধারে ধর্মীয় ও কৃষক নেতা। এই কৃষকদের জন্য যাঁরা বাঁচার লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে পুরোভাগে ধর্মীয় নেতারা ছিলেন। সেই সুবাদে ইসলাম এখানে সহজে বঞ্চিত, অন্ত্যজ, এক্সক্লুডেড মানুষের মাঝে আসন গাড়তে সক্ষম হয়। এই ব্যাখ্যাটি রিচার্ড ইটন আদিতে দিয়েছিলেন তাঁর দ্য রাইজ অব ইসলাম-এ দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার গ্রন্থে। কিন্তু এখানে আকবর আলি খান কিছু কারেক্টিভ এনেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মাজারের কনসেনট্রেশন সম্পর্কিত ম্যাপ তৈরি করে দেখিয়ে বলেছেন- সর্বত্র কিন্তু পীর-আউলিয়ার সমাবেশ এক রকম ছিল না। তারপরও ইসলামের ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি ঘটেছে। সুতরাং এটা শুধু পেজেন্ট কাম রিলিজিয়াস লিডারশিপের ব্যাপার ছিল না। এটার আরেকটা কারণ ছিল- ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়ে যাঁরা এই ভূখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে নতুন ধর্ম ও রীতি অভ্যাসের ভলান্টারি অ্যাডাপটেশন। অনেকটা পুশ-পুল ইফেক্টের মতো দুটি দিকই এখানে কাজ করেছে।
ওই বইতে আকবর আলি খান আরেকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কেন আমাদের দেশে বৃহৎ অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল অর্গানাইজেশনগুলো সফল হয় না। কেন আমাদের দেশে স্তালিনীয় কায়দার সুশৃঙ্খল দল দাঁড়ায় না। কেন আমাদের দেশে বড় যেসব উদ্যোগ আমরা নিতে চাই, সেগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁর ধারণা, যে কারণে আমরা অপেক্ষাকৃত মুক্তগ্রাম, মুক্তসমাজ এবং অন্যকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী (যার একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, প্রায় এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে আমরা অতি স্বল্প সময়ে আশ্রয় দিতে পেরেছি); এসব যেমন আমাদের শক্তির দিক, তেমনি আমাদের দুর্বলতার দিক হচ্ছে- আমরা কারও একক নেতৃত্ব বা লিডারশিপের ধার ধারি না। এর ফলে আমাদের ভেতর একটি সেন্ট্রিফিউগাল টেন্ডেন্সি (কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা) সৃষ্টি হয়। আমাদের সমাজ সংগঠনে একটি অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।
তাঁর উত্তর হচ্ছে, এই ধরনের সমাজ-মানসিক কাঠামোয় সেই ধরনের অর্থনৈতিক সংগঠন বেশি কার্যকর হবে, যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালিজম, ব্যক্তি উদ্যোগ বা স্বল্প পরিসরের গ্রুপ-উদ্যোগগুলো কাজ করবে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি দেখালেন, আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুততম সময়ে ব্যক্তিখাত গড়ে উঠল, বিকাশপ্রাপ্ত হলো। এক কথায় বলতে গেলে মার্কেট লিবারেলিজমের পক্ষে একটা সোশিওলজিকাল আর্গুমেন্ট তিনি উপস্থাপন করলেন। আরেকটি উদাহরণ তিনি দিলেন, কেন গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাকের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো এখানে সফল হলো। কেননা এগুলোর দল সংখ্যা মূলত পাঁচ থেকে দশ, ঊর্ধ্বে ত্রিশ। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলো এই অঞ্চলে কাজ করতে বেশি সক্ষম বা কাজে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি আরও একটি যুক্তি সেখানে দিলেন, সেটি হচ্ছে- অ্যাগ্রো ইকোলজিকাল আর্গুমেন্ট। তিনি বললেন, দক্ষিণ ভারত বা পশ্চিম ভারতে যেখানে অপেক্ষাকৃত শুস্ক মৌসুমি এলাকা, যেখানে মূলত সারফেস ওয়াটার-নির্ভর সেচ ব্যবস্থা করতে হয় কৃষিকাজের জন্য, সে ক্ষেত্রে কৃষকদের রাষ্ট্রের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি নির্ভর করতে হয়। এই কারণে ওইসব এলাকায় আমরা ক্যানাল ইরিগেশন (খাল খনন) সিস্টেম পাই, আমরা হাইড্রোলিক সভ্যতার (জলকেন্দ্রিক সভ্যতা) নিদর্শন পাই। এর বিপরীতে আমরা যখন পূর্ব বাংলায় আসি, দেখি যে নদীমাতৃক দেশ হওয়ার কারণে এখানে গ্রাউন্ডওয়াটার ইরিগেশন অপেক্ষাকৃত সফলতা পায় এবং গ্রাউন্ডওয়াটার ইরিগেশনের মধ্যেও সেখানে ডিপ টিউবওয়েলের চাইতে দেখতে পাই শ্যালো টিউবওয়েল উদ্যোগের ছড়াছড়ি।
এক কথায় বলতে গেলে, আকবর আলি খানের ইতিহাসচর্চার মধ্যে পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্য খোঁজার ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইকোলজি, প্রযুক্তি, মানুষের মনস্তত্ত্বসহ বিভিন্ন ছড়ানো ছিটানো ফ্যাক্টটরকে একত্রে সন্নিবেশিত করতে পেরেছেন। এজন্য তাঁর বিচার-বিশ্নেষণগুলো অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে।
প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে বলে রাখি, তিনি ভূমিকাতে আরও একটি কথা বলেছিলেন। তাঁর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করা। পরবর্তী সময়ে তিনি আমাকে একান্তেও বলেছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মাল্টিপল থিয়েটারে হয়েছিল। মঞ্চের এক অংশের ওপর যদি কেবল আলোকপাত করা হয়, তাহলে ভুল হবে। একই সময়ে অন্য থিয়েটারগুলোতেও সেই নাটকের অন্যান্য অংশ অভিনীত হচ্ছিল। সে কারণে ওই ধরনের কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি লেখার জন্য যে ধরনের পরিশ্রম, যে ধরনের কালেক্টিভের সমবেত সাধনার প্রয়োজন, সেটি নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে তিনি দেখছেন না। বিশেষত সমসাময়িক রাজনীতির বাদানুবাদের কারণে; তাঁর ভাষায়- ডিউ টু কনটেম্পরারি পলিটিকাল স্কোয়াবলস। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তিনি বসে না থেকে যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে- এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ইতিহাসের একটি প্রাক-ইতিহাস রচনা করা। ডিসকভারি অব বাংলাদেশের যে উন্মোচন, সেটি প্রাক-ঐতিহাসিক ন্যারেটিভের একটি নিদর্শন।
বইটি আমাকে এত বেশি আকৃষ্ট করেছিল যে আমি বইটির শুধু একটি বুক রিভিউ নয়, একটি রিভিউ আর্টিকেল রচনা করি। সেটি একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে’ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। সেখানে আকবর আলি খানের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে আমি কিছুটা বাহাস করার চেষ্টা করি। কিছু কিছু অভিযোগ আমি সেখানে এনেছিলাম। যেমন আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম- তিনিও বঙ্কিমের মতো আমাদের বলছেন- বাঙালির ইতিহাস নাই, এই ইতিহাস কে লিখিবে, আমি লিখিব তুমি লিখিবে; সেই রকম একটি জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার উৎসাহে তিনি এই বইটি লিখলেন কিনা? কেননা আমরা যদি দুইশ-তিনশ বছর আগে যাই, সেখানে তো ন্যাশনালিজমের- এজ আ পলিটিকাল কনসেপ্ট- কোনো স্ম্ফুরণ দেখি না। এটি তো অনেক পরের ঘটনা। রেনাঁ এবং তাঁর পরবর্তী যাঁরা পলিটিকাল ন্যাশনালিজমের প্রবক্তা, তাঁদের সময়ের ঘটনা। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে। আমার আপত্তি ছিল এই বইয়ের সাবটাইটেলে। সাবটাইটেল ছিল- এক্সপ্লরেশনস ইনটু ডাইনামিকস অব এ অব হিডেন নেশন। উনি যেটাকে হিডেন ন্যাশনালিজম বলছেন, সেটাকে ফর্মুলা হিসেবে নিলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তা হলো, আমরা এই রকম হিডেন ন্যাশনালিজমের উৎস সন্ধানে চর্যাপদ বা তারও আগে পিছিয়ে যেতে পারি। আর এতে করে ইতিহাসের নিয়মের বরখেলাপ হয় কিনা? তদুপরি আমি কিছুটা রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম গ্রন্থের প্রভাবে জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণের সমস্যাটাকে বড় করে দেখেছিলাম। জাতীয়তাবাদকে এজ এ কনসেপ্ট- স্বয়ম্ভু, অ্যাবসোলুট, অবশ্যপালনীয় কনসেপ্ট হিসেবে অন্তত তখন পর্যন্ত মনে করিনি।
জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রধান বক্তব্য ছিল- জাতীয়তাবাদ শুধু একটি মাত্রায় গড়ে ওঠে না। সেখানে ভৌগোলিক এবং আদর্শিক- এই দুটো মাত্রাতেই প্রভাব আসে। এবং আকবর আলি খান পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে দেখেছেন- এখানে ফেইথ মূলত ইসলাম হলেও, নানা ধরনের সংকর বিশ্বাসের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ফলে ফেইথের মধ্যেও অনেক রকমের বৈচিত্র্য এসেছে। অন্যদিকে আবার আমাদের ভৌগোলিক কিছু অভিন্নতার কারণে, নদীমাতৃক দেশ হওয়ার কারণে, বন্যা-ঝড় এসব প্রাত্যহিক উপদ্রবের কারণে আমাদের কতগুলো জনগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। কতগুলো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা দেখতে পাই, যেগুলো আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের যে পিউরিটি, তার পাশাপাশি ভৌগোলিক ইমপিউরিটির সঙ্গে মিলেমিশে মিথস্ট্ক্রিয়া তৈরি করেছে। বিশ্বাস ও বসতি- এই দুই উপাদান মিলে এমন একটি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পূর্ববঙ্গে, যেটি অন্য কোনো ভূখণ্ডের সঙ্গে মেলে না। কারণ তারা এ দেশের মতো এতটা পরিমাণে নদীনির্ভর দেশ নয়, যতটা পরিমাণে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা ঝড়-বাদল ও নদীর ওপরে নির্ভরশীল। এটিও জাতীয়তাবাদের বিচার-বিশ্নেষণের ক্ষেত্রে তাঁর একটি অনন্য অ্যাপ্রোচ।
এক অর্থে, যদিও এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পুরোপুরি নয়, তবু না মনে করে পারছি না, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও যখন জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিতে সংসদে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন- আমার চোখে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বাংলার মাটি, জল, নদী, আকাশ। এর বেশি আপনারা আর সংজ্ঞায়িত করতে যাবেন না। গেলেই বিপদ বাধবে। আরও বেশি ঠোকাঠুকি হবে। বঙ্গবন্ধু একটা পর্যায়ে বুঝেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ বিষয়টিকে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করতে গেলেই বিপদের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ বিষয়টিকে একটু এমবিগু্যয়াস এবং ইকোলজিকাল ফ্রেমে দেখলে অনেক বেশি নিরাপদ উপস্থাপনা হয়। আকবর আলি খানও অনেকটা এই আলোকেই বারবার জোর দিয়েছেন ফেইথ ও হ্যাবিট্যাটের মিথস্ট্ক্রিয়ার ওপরে। বিশ্বাস ও বসতির পারস্পরিক প্রভাব সমুচয়ের ওপরে।
২. স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অর্থনীতি
আকবর আলি খানের দ্বিতীয় বইটি ছিল পরার্থপরতার অর্থনীতি নিয়ে এবং নামেই এর বৈচিত্র্যের পরিচয়। আমরা জানি, আমাদের সনাতন অর্থনীতি মূলত স্বার্থপরতার অর্থনীতি। কেননা তার প্রথম সবকই হলো- এডাম স্মিথের অনুসরণে- মানুষ যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে, সেটি তার নিজস্ব স্বার্থ দ্বারা প্ররোচিত হয়েই করে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য হাতের কল্যাণে বিভিন্ন স্বার্থমুখী উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সামাজিক কল্যাণ বয়ে আনে।
কিন্তু স্বার্থপরতার অর্থনীতি বা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিপরীতে আকবর আলি খানের বইয়ের নামটি ছিল- পরার্থপরতার অর্থনীতি। পরার্থপরতা, যেখানে স্বার্থের কোনো বালাই নেই, পরোপকার করছি নিঃস্বার্থভাবে; সেটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। এর মানে এই নয় যে, লেখক বলছেন, স্বার্থপরতার অর্থনীতির কোনো জায়গা নেই আমাদের জীবনে এবং আমাদেরকে সব সময় বা বেশিরভাগ সময় পরোপকার, নিজের স্বার্থ ভুলে অন্যের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে আর পুরো দেশ-সমাজটা এভাবে পরিচালিত হবে।
এ ধরনের কোনো ইউটোপীয় ধারণায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি শুধু বলছেন, সমাজ, রাষ্ট্র বা অর্থনীতি যদি কেবল ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর নীতিতে পরিচালিত হয়, তাতে সমাজে কোনো শৃঙ্খলা থাকে না এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কেনেথ এরোর এই উক্তি মনে করিয়ে দিয়েছেন- পুঁজিবাদকে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনীতি চালাতে হলেও, তাকে একটা পর্যায়ে নিঃস্বার্থ, জনস্বার্থমুখিন, ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিস্ট, ওয়েলফেয়ার স্টেটমূলক নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়। এভাবে স্বার্থপরতাকে টিকিয়ে রাখতে হলেও পরার্থপরতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে যে ধরনের পণ্যসেবা ভোগ করে থাকি, তার সবটাই বাজার থেকে প্রাপ্ত না। যেমন আইনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, টিকাদান, জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা। এসব বিষয় বাজারদরে যাচাই করা যায় না। এগুলো সর্বমানুষের মৌলিক অধিকার। যেটা আমাদের সংবিধানেও আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য- এগুলো হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন। এই বেসিক নিডস সব সময় বাজার দ্বারা প্রাপ্ত হয় না। বাজারমুখিন কর্মকাণ্ড এগুলোর প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পারে, সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু শুধু বাজারনির্ভর ব্যবস্থায় কোনো দেশই ১০০ শতাংশ নিরক্ষরতা দূর করতে পারেনি, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তৃত করতে পারেনি এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বেসিক নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনি।
এই বইটি লেখার পেছনে স্পষ্টতই দেখা যায়, সেই সময় আকবর আলি খান ভাবছিলেন কোন ধরনের সমাজ হবে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। সেটি কি কেবলই অবাধ বাজারমুখিন অর্থনীতি হবে, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনীতি হবে, নাকি পাশাপাশি সামাজিক দায়দায়িত্ব বহনকারী প্রতিষ্ঠানাদি সংগঠন আয়োজন গড়ে তুলবে। নিজে তিনি দীর্ঘকাল সরকারের অর্থ সচিব ছিলেন, পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন। তিনি খুব কাছ থেকে সরকার ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেও হয়তোবা তাঁর মনে হয়েছে, বই লিখে জানান দেওয়া উচিত- আমরা বাজার অর্থনীতির দিকে সদর্পে হাঁটছি বটে কিন্তু তার রশিটা থাকতে হবে পরার্থপর জনকল্যাণের অর্থনীতির কেন্দ্রে। এবং এ দুটোরই সম্মিলন তিনি চেয়েছেন : বাজার ও রাষ্ট্র, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, মানুষের ব্যক্তি প্রয়োজন ও সামষ্টিক প্রয়োজন। এক পর্যায়ে তিনি সামাজিক পুঁজি এবং এর মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়েছেন অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য।
এই বইটিরও আমি একটি সমালোচনা লিখি ২০০১ সালে। এটি বিআইডিএস কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ‘উন্নয়ন সমীক্ষা’-তে বেরোয়। সেখানে আমি এই বইটির মূল প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করে বলি, বাংলাদেশের মতো দেশে যদি আমরা ওয়েলফেয়ার স্টেট বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদের নীতিমালার মধ্যে কত শতাংশ আমরা ব্যক্তি উদ্যোগের অর্থনীতির নীতিমালা নিচ্ছি আর কত শতাংশ পরার্থপরতার অর্থনীতির নীতিমালা নিচ্ছি, সেগুলোর চুলচেরা বিশ্নেষণ হওয়া উচিত। প্রতি বছর বাজেট এলে যে কথা আমরা প্রায়ই মনে রাখি না।
৩. তার আগে চাই গণতন্ত্র
২০১০-এর দশকে এসে আকবর আলি খানের রচনায় আমরা বিষয়াদির একটা বিপুল বৈচিত্র্য দেখতে পাই। ক্রমে তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাস, ইকোনমিক হিস্টোরিয়ান অথবা অর্থনীতিবিদের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন। সেখানে তিনি যা কিছু তাঁর কাছে উৎসাহজনক মনে হয়েছে, কৌতূহলকে উস্কে দিয়েছে, তা তিনি অনুসন্ধান করতে পিছপা হননি। অনেক সময় এ ক্ষেত্রে বিতর্কেরও জন্ম নিয়েছে।
যেমন বনলতা সেন আলোচনায় তাঁর একটি মত হচ্ছে- বনলতা সেন বলে সত্যিই একজন ছিলেন এবং বাস্তব জীবনেই তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল। হয়তো প্রেম বা শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল- এ রকমও তিনি স্পষ্ট করে ইঙ্গিত দিয়েছেন। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার- এটির তিনি একটি ফ্রয়েডীয় বিশ্নেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে তিনি ভূমেন্দ্র গুহর ‘জীবনানন্দ দাশের ডায়রি’ ব্যবহার করেছেন, যেটি অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জীবনানন্দের কবিতা বিশ্নেষণে তথ্য বিচারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন আকবর আলি খান।
সুশাসনের বিষয়টি তাঁকে বিভিন্ন সময় ভাবিয়েছে। একটা বড় কারণ, তিনি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। স্বল্পকালীন হলেও তিনি রাষ্ট্রের উচ্চতর মহল, উচ্চতর স্তর থেকে সুশাসনের সমস্যা আমাদের মতো দেশে প্রত্যক্ষ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান হন। সেই কমিশনের অস্তিত্ব এখন নেই।
সেখান থেকেও তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমাদের দেশে কত ধরনের রেগুলেশনের সমস্যা। রেগুলেশন বাস্তবায়নের সমস্যা। যানবাহন, রাস্তার ট্রাফিক, বিদ্যুৎ বিল, ব্যাংকের ঋণ পাওয়া থেকে শুরু করে ওয়াসার জলের কোয়ালিটি, জনস্বাস্থ্য থেকে জনশিক্ষা- সব জায়গায়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণগত মান নির্ণয়ের সমস্যা। একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, একটা প্রমিতীকরণ, একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ধরে গুণমানকে বজায় রাখার সমস্যা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসন নিয়ে তিনি একাধিক বই বাংলা ও ইংরেজিতে রচনা করেছেন এবং সেখানে তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে- একেবারে যে রাতারাতি একটি দুঃশাসনের থেকে আমরা সুশাসনের উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যাব, ব্যাপারটা এমন নয়। মানুষের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে উঠতে হয় এবং সুশাসনের চাহিদাটি গড়ে ওঠে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা বৃদ্ধি- সেগুলোর সাপেক্ষে। কিন্তু এর মানে এ-ও নয়, আমরা নিষ্ফ্ক্রিয় বসে থাকব বা একটা দীর্ঘ সময়ের দিকে মুখ রেখে চলব এবং অজানা সুশাসনের ভবিষ্যতের দিকে এগোব।
সময় লাগলেও কতিপয় ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অবিলম্বে জরুরি। যেখানে আমরা কোনোভাবে ছাড় দিতে প্রস্তুত নই। যেমন- আপনি যদি হাসপাতালে গিয়ে দেখেন এক্স-রে মেশিনটি ঠিকমতো কাজ করছে না, ইসিজি মেশিনটি সঠিক ফল দিচ্ছে না বা সময়মতো সেখানে জরুরি বিভাগে ডাক্তার বা নার্সকে পাচ্ছেন না, যেখানে আপনি আপনার রোগী নিয়ে এসেছেন জরুরি চিকিৎসার জন্য, সেই ধরনের সুশাসনের অভাব কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না বা সাময়িক অসুখ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
একইভাবে আমরা যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে সুশাসনের কথা বলি, ধরা যাক বেসিক এডুকেশনের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকের অনুপস্থিতি থাকে, যদি শিক্ষক স্কুলে না পড়িয়ে কোচিং সেন্টারে পড়াতে বেশি আগ্রহী হন, যদি কোচিং সেন্টারই স্কুলের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়- এ ধরনের সুশাসনের অনুপস্থিতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোত্তম সুশাসনের মাঝখানে আমাদের যে কোনো চয়েস নেই, তা বলা যাবে না। আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবিলম্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যদিও আরও বৃহত্তর বলয়ে রেগুলেশন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগবে। তিনি এ নিয়ে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর ‘ফ্রেন্ডলি ফায়ারস, হাম্পটি ডাম্পটি ডিজঅর্ডার’ বইতে।
এ ক্ষেত্রে বলে রাখি, আকবর আলি খানের রচনার প্রসাদগুণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তিনি সরসভাবে জটিল তত্ত্বের কথা বলতে পারেন। সেজন্য প্রয়োজনে তিনি অনেক সময় নাসিরউদ্দিন হোজ্জার বিভিন্ন গল্প বলে বিষয়টাকে প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর লেখাতে প্রায়ই স্কিট, চুটকি নানা ধরনের এনিকডোটাল রম্য কাহিনি বা বিবরণ থাকে এবং সেটি এত বেশি প্রাসঙ্গিকভাবে আসে যে তা বিশ্নেষণেরই একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর এ রকম একটি বই বোধ করি ২০১৩-এর দিকে বেরিয়েছিল। তার নাম আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি। যেটার রিভিউ হয়েছিল কলকাতার দেশ পত্রিকায়। দেশ পত্রিকার সমালোচক লিখেছেন, বইটি পড়ে এটুকুন অন্তত বলতে পারা যায় যে লেখক কষে বাংলা লিখতে জানেন! তাঁর লেখার যে ধারা এবং লেখার যে সরস রচনাশৈলী, তা দেখে তিনি এ মন্তব্য করেছেন। সেটি মিথ্যা নয়, কারণ তাঁর অত্যন্ত সুলিখিত সাবলীল ইংরেজিতে নির্মিত রচনা এবং পরবর্তীকালে তাঁর বাংলা লেখাগুলোতেও দেখেছি হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে, সহজ যুক্তির মাধ্যমে, কখনও কোনো সামান্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি গুরুগম্ভীর বিষয়টির অবতারণা করেছেন এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে সহজেই তাঁর বিষয়বস্তুটি গেঁথে যাচ্ছে। এটি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।
শেষ পর্যায়ে আকবর আলি খান অনেক লেখা লিখেছেন। এর মধ্যে একটি-দুটি বলে আমি শেষ করব। একটি হচ্ছে, দারিদ্র্য নিয়ে তিনি একটি সুবিশাল গ্রন্থ লিখেছেন এবং সেখানে তিনি দারিদ্র্যের উৎপত্তি, ইতিহাস, তার মূল্যায়ন পদ্ধতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতিমালা- এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা এখানে করতে চাই না কিন্তু যেটি আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, শেষের কয়েক বছরে তিনি বারবার গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায় এবং আগে যদি তাঁর যুক্তি ছিল- আমাদের দেশের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক কারণেই মার্কেট লিবারেল বা বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে পারে, কারণ তারা অনেক বেশি অসামষ্টিক বা অনেক বেশি ইন্ডিভিজুয়াল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক; পরবর্তী সময়ে সেটাকে তিনি কাউন্টার পয়েন্ট ধরে লিখলেন, শুধু মার্কেট লিবারেল ক্যাপিটালিজমের পথে হাঁটলেই চলবে না, পরার্থপরতা বা জনকল্যাণের কথাও ভাবতে হবে। সেজন্য পরার্থপরতার অর্থনীতি লেখা হয়েছিল।
কিন্তু মার্কেটই করি আর নন-মার্কেটই করি, উভয়টাতেই আমাদের লাগবে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, প্রমিতীকরণ, রেগুলেশন, তার বাস্তবায়ন, সুশাসনের বাস্তবায়ন। সেজন্য তিনি সুশাসনকেন্দ্রিক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু এই সুশাসনকেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি এক পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে গণতন্ত্র না এলে আমাদের মতো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এই কনক্লুশনটির আগে থেকে পূর্বাভাস মেলেনি। মার্কেট লিবারেলিজমের পাশাপাশি ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিজম, আবার এ দুইকে বাস্তবায়ন করার জন্য সুশাসনের অর্থনীতি আর সুশাসনের অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন বা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা- এটি যে প্রবলতর পূর্বশর্ত, সেটি আগে তিনি অনুধাবন করেননি। কিন্তু ২০০০ দশকের শেষের দিকে এসে তাঁর বিভিন্ন লেখাতে সেটির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ যে রচনা প্রকাশিত হয়েছে সমকালে, কালের খেয়াতে গত ৯ সেপ্টেম্বর সেখানেও এর প্রমাণ মেলে। আবুল মনসুর আহমদের ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে তিনি বলেন, গণতন্ত্র ছিল না বলে পাকিস্তানে ফেডারেলিজমটা টেকেনি এবং ফেডারেলিজম ভেঙে টু ইউনিটের প্রস্তাবনা করা হয়। পাকিস্তানের সংবিধানে যেসব অধিকার থাকতে পারত, সেগুলো আসেনি। দুই অর্থনীতি গড়ে ওঠে এবং দুই অর্থনীতি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে বৈষম্য, বিশেষ করে আঞ্চলিক বৈষম্য আরও গেড়ে বসে। নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন- ‘তার আগে চাই সমাজতন্ত্র’। আকবর আলি খান লিখতে পারতেন- ‘তার আগে চাই গণতন্ত্র’।
উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, আবুল মনসুর আহমেদের যুক্তি মেনেই বলতে হয়- গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়নের ধারা টিকিয়ে রাখা কঠিন। অন্য অনেক দেশে হয়তো সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র ছাড়াই এবং দীর্ঘকাল সেভাবে চলতে চলতে একসময় গণতন্ত্র আঙুর ফলের মতো জনগণের পাত্রে এসে পড়ে যায়, সে রকম অবস্থা আমাদের নয়। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান বা সিঙ্গাপুরের মতো মডেল নিয়ে আমরা চলতে পারব না। ‘আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র’-এর মডেলটিকে আকবর আলি খান কার্যত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে- অন্তত আমাদের মতো দেশের যে মনস্তত্ত্ব, অস্থিরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আর কাউকে স্ট্যালিনীয় কায়দার এককেন্দ্রিক শাসনের কেন্দ্রে না মানার প্রবণতা- এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের পৃথক জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলে। সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় যেখানে দীর্ঘকাল, ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে চলেছে একদলীয় এককেন্দ্রিক শাসন, তার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা তাই যথাযথ হয় না। সে ক্ষেত্রে তাঁর কনক্লুশন মূলত দাঁড়ায় এই যে- আমাদের দেশের মুক্তি মিলবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়েই এবং এক দলের দীর্ঘকাল শাসনে না থাকার মধ্য দিয়েই এটার সফল পরিণতি হয়তো দেখা যাবে।
আকবর আলি খানের এই বক্তব্যও আমাদের সচকিত করে, কেননা এখানে তিনটি কথা বলেছেন। একটি বলেছেন যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভবন দরকার। ডিসেন্ট্রালাইজেশন দরকার। আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই ডিসেন্ট্রালাইজেশন সহসা সম্ভব নয়, সেটি পাঁচ-দশ বছরের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি কোনোভাবেই ছাড় দিতে নারাজ, সেটি হচ্ছে সময়মতো কারচুপিহীন সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা। সেটি তাঁর দিক থেকে নূ্যনতম পূর্বশর্ত ওই ধরনের সুশাসনসমৃদ্ধ পরার্থপরতার মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতির সফল বিকাশের জন্য এবং সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কার আনতে হতে পারে।
এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হার সাপেক্ষে সংসদ সদস্য বণ্টনের কথা। উইনারস টেক ইট অল- সেই ধরনের প্রচলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমরা কি নিউজিল্যান্ডের মতো বা অন্য যেসব দেশ আনুপাতিক ভোটপ্রাপ্তির বিচারে সংসদে প্রার্থী সংখ্যা নির্ধারণ করবে, সেই দিকে যেতে পারি কিনা। অর্থাৎ প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের সিস্টেমে যেতে পারি কিনা। এতে তিনি বলেছেন, প্রতিযোগী দলের মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে এবং অনেক বেশি স্ট্যাবল গণতন্ত্রের জন্ম হবে। তবে লেখক এ নিয়ে তাঁর শেষ কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, এ নিয়ে আরও গবেষণা করা উচিত।
এ বিষয়টি নজরুল ইসলাম বা অন্যদের লেখায় আগেও এসেছিল, কিন্তু এটি দেখলাম আকবর আলি খানেও খুব বিশদভাবে এসেছে। এই পদ্ধতিটি নিয়ে আরও গবেষণা জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি চান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি, সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পলিটিকাল উন্নয়ন হোক। সমানতালেই হোক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন না এলে যে অর্থনীতির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে এবং সামাজিক উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়তে পারে- এ কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
৪. সংক্ষিপ্তসার
এক কথায় বলতে গেলে আকবর আলি খান ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মননের মানুষ। আটাত্তর বছরের জীবনে তিনি একাধিক ভূমিকা পালন করেছেন- কখনও সরকারি আমলা হিসেবে, কখনও শিক্ষক হিসেবে, কখনও সাহসী প্রাবন্ধিক হিসেবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন, তার একটা দীর্ঘমেয়াদি আঁচড়ও তাঁর মধ্যে থেকে গিয়েছিল এবং এর ফলে তাঁকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, সেটি তিনি কখনও প্রকাশ্যে বলেননি। যেমন বলেননি শেষের দিকে তাঁর স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার পরে তাঁর কত কষ্ট হতো লিখতে এবং এক পর্যায়ে তিনি লিখতেই পারতেন না, যেহেতু তাঁর ডান হাতটাই তখন কাজ করত না। তখন তিনি মুখে বলে যেতেন এবং অন্যরা লিখতেন এবং তিনি সেটাকে সেভাবেই কারেকশন করে বা কম কারেকশন করে প্রকাশের জন্য তৈরি করতেন।
এটি যে কোনো লেখকের পক্ষেই যন্ত্রণা এবং তাঁর মতো এত খুঁতখুঁতে লেখক, এত পুর্ণাঙ্গ লেখকের পক্ষে তো এ যন্ত্রণা আরও বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি একপ্রকার নিজের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেই এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার ফলে আমরা অনেক রচনা পেয়েছি। এটি আমাদেরকে তাঁকে সব সময় মনে করিয়ে দেবে।
আকবর আলি খানের রচনা, তাঁর সব লেখাপত্র সবাই আরও মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, বিতর্ক করবেন, আলোচনা করবেন এবং আরও উন্নত গবেষণার দিকে অগ্রসর হবেন- এই আশা রাখছি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্যই তাঁর রচনাবলির সংগ্রহ অবিলম্বে প্রকাশ হওয়া এখন জরুরি।



