 বিনায়ক সেন
বিনায়ক সেন
১. আধুনিক যুগের ‘অবসান’ নেই?
ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে সময়কে তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে_ যথাক্রমে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগের জন্ম এবং পাঠ্যবইয়ের যুক্তি অনুসারে এই যুগ এখনও চলছে। আধুনিক যুগের অবসান নেই। এক অর্থে আধুনিক যুগে উত্তরণের পর থেকে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। এখন বড়জোর যেটা চলতে পারে তাহলো মূল ইতিহাসের বাইরে থেকে যাওয়া বিশ্বের অধিকাংশ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মেষশাবকের মতো ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন। পাশ্চাত্যের যুক্তি_ সেটা সম্ভব কেবল আধুনিকায়নের মাধ্যমে। এটা শুধু এন্ড অব হিস্ট্রিখ্যাত ফুকোয়ামার যুক্তি নয়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট তাত্তি্বকদের প্রায় সবাই কমবেশি এই মতে জড়ো হয়েছিলেন। তার মানে এই নয় যে, এদের মধ্যে মতবিভেদ ছিল না। কিন্তু তা ছিল আধুনিকায়নের মধ্যেই মতবিভেদ। এনার্কিজম, সিন্ডিক্যালিজম, বলশেভিজম নানা মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল উন্নত-মাঝারি, পুঁজিবাদী নানা দেশে এই সময়ে। তবে এসব ডিসকোর্সে উপনিবেশের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না, কেননা উপনিবেশের অধিবাসীদের এনলাইটেনমেন্ট-পরবর্তী ইউরোপ কখনও সমকক্ষ মানুষ বলেই স্বীকার করেনি। নইলে আমাদের ‘হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন’ বলে ভাবাটাই সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। আরিস্ততলের গণতন্ত্রে যেমন দাসত্বের স্থান ছিল না, কান্ট-হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসে বা বৃহত্তর অর্থে বিশ্ব-শান্তির চর্চায় উপনিবেশের নিজস্ব কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না। আর বোবা ভাবলে বা করে রাখলে যা হয়, উপনিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিথ্যাচারকে ক্রমাগতভাগে পুনরুৎপাদিত করা হচ্ছিল ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বা প্রাচ্যবিদ্যা নামক জ্ঞান কাণ্ডে। এসব তথ্য অবশ্য আমাদের ইতিমধ্যে এডোয়ার্ড সাইদের রচনা ও রণজিৎ গুহের নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার কল্যাণে জানা হয়ে গেছে। এরা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার আদি-প্রেরণা হিসেবে ছিলেন এবং আছেন মার্কস।
আধুনিকতা অথবা উত্তর-আধুনিকতা যে পথেই আপনি থাকুন না কেন মার্কসের কাছেই আপনাকে ফিরে যেতে হবে। অন্তত মার্কসের স্টেশনে কিছুক্ষণ হলেও আপনাকে জিরোতে হবে। এর কারণ, মার্কসের রচনাবলীর মধ্যে যেমন পাওয়া যাবে আধুনিকতার অনিবার্যতা, তেমনি পাওয়া যাবে এর সমালোচনাও। অনেক সময় তিনি তার লেখায় যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন তা নিয়েই শতখানেক পিএইচডি অভিসন্দর্ভ লেখা হয়েছে। একটা উদাহরণ দেই। মার্কস এক পর্যায়ে বলেছিলেন, হেগেলের রচনায় ডায়ালেকটিকসের তত্ত্ব ‘মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে’। তার মানে এখন তাকে ‘সোজা করে নিলেই’ বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে নিষ্কাষণ করা যাবে। এ রকম একটা ব্যাখ্যা হতেই পারে। যেমন, একটা ব্যাখ্যা হতে পারে হেগেলের মন ভাববাদী, কিন্তু তার পদ্ধতি ডায়ালেকটিক্যাল যাতে কোনো ভুল নেই। ফরাসি দার্শনিক লুই আলথুসার এতে বাধ সাধলেন। তার যুক্তি, মাথার উপরে দাঁড়ানো হেগেলীয় পদ্ধতিকে সোজা করে নিতে গেলে নাট-বল্টু সবকিছুতে এলোমেলো হয়ে যায়। মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস হেগেলের লেখা থেকে নয়, মার্কসের নিজের লেখা থেকেই আবিষ্কার [নিষ্কাষণ] করে নিতে হবে। সে সূত্রে তিনি মার্কসের মধ্যেই হেগেলীয় ‘তরুণ মার্কস’ আর স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর ‘পরিণত মার্কস’_ এ দুইয়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন ‘জ্ঞানতাত্তি্বক ভেদরেখা’ [এপিস্টেমোলজিক্যাল ব্রেক] । যা হোক এসব তর্ক ও ধন্দের কারণে মার্কসকে কখনও আধুনিকতাবাদীরা তাদের দলে টানার চেষ্টা করেছেন। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের অনেকেই মার্কসের রচনায় আধুনিকায়নের ‘নষ্ট রক্ত’ খুঁজে পেয়েছেন। আবার ফ্রেডেরিক জেমেসনের মত উত্তর-আধুনিক মার্কসবাদীরা মার্কসকে তাদের আদি-প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যরা যারা প্রথম দিকে বেশ সোচ্চারেই মার্কস-বিরোধী ছিলেন বা সেদিকেই তাদের কণ্ঠ বেশি করে শোনা গেছিল, পরবর্তীতে তারাও তাদের মত কিছুটা বদলেছেন। বিশেষভাবে এটা ঘটেছে ফরাসি দার্শনিক জাঁক দেরিদার রচনায়_ স্পেক্টর অব মার্কস গ্রন্থের পর থেকে। ফুকোর শেষের দিকে রচনায় জোরেশোরে ফিরে এসেছে ইতিহাসে কর্তার [সাবজেক্ট] ভূমিকা, ফলে মার্কসের রচনার মতোই তরুণ ফুকো ও পরিণত ফুকোর মধ্যে বেশ খানিকটা ভেদরেখা সৃষ্টি হয়ে গেছে।
এসব বিভিন্নবিধ সমালোচনা ও পাল্টা সমালোচনার পেছনে মূল তাগিদ হচ্ছে সমাজকে বদলানো। আর সমাজকে বদলাতে গেলে প্রথাগত ব্যবস্থার দুই প্রধান সহায়ক শক্তি_ রাষ্ট্রযন্ত্র ও অর্থনীতি_ এদেরকেও যে বদলাতে হয়। আর এই পাল্টে দেয়ার ব্যাপারটা তো পুরোনো দালান ভেঙে নতুন দালান করার প্রকল্প নয়। একেক রাষ্ট্র ও একেক অর্থনীতি একেক ধরনের সমাজ ও সেই সঙ্গে একেক ধরনের ‘মানব’ তৈরি করে থাকে। আমরা যে কথার কথা হিসেবে বলি, উনি বেশ সনাতনী ধারার লোক, উনি বেশ চলতি হাওয়ার পন্থী সেসব আদৌ কথার কথা নয়।
আধুনিকায়নের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের অন্দর-মহলেও আধুনিকায়ন ঢুকে পড়ে। চিন্তা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু মনের জানালা দিয়ে আধুনিকায়নের স্বপ্ন কুয়াশার মতো ঢুকতে থাকে। ঢাকার রাস্তায় হাঁটি, কিন্তু মনে মনে ঢাকা শহরকে দেখি না, আসলে হাঁটতে থাকি ম্যানহ্যাটানের ফুটপাতে। এদেশ এগুচ্ছে; তার বিলবোর্ড করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টি বা আইফেল টাওয়ারের কথা। গ্রাম-বাংলার তপ্ত দুপুরের রোদে কাজ থামিয়ে ক্ষেতের পাশেই গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়ছে যে বৃদ্ধ কৃষক তার মুখচ্ছবি আমাদের বিলবোর্ড থেকে হারিয়ে যায়। রণে-বনে- সংকটে আমরা পীর-মুর্শিদ বা পুণ্যধামে ছুটি না আর। নবযুগের পীর-আউলিয়া ড্যান মজীনারা আমাদের আশ্বস্ত করেন। কোন পথ ধরে এগুলে আমরা পাশ্চাত্যের গুডবুকে থাকব, জিএসপি সুবিধে বাতিল হবে না, বা পাব ‘মডারেট মুসলিম ডেমোক্রেসি’র খেতাব, আর কি করা গেলে ওবামা বা নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসবেন ঢাকায়, এমডিজিতে সাফল্যের করণে_ চাই কি শান্তির নোবেল_ এসব আমাদের রাষ্ট্রীয় তৎপরতার একটি প্রধান সাফল্য-সূচকে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ’ ধারণা অনুসরণ করে বলা যেতে পারে ‘ছোট আধুনিকতা’ [তৃতীয় বিশ্ব] বনাম ‘বড় আধুনিকতা’ [পশ্চাত্য] এই খেলাই চলছে এখন।
২. আধুনিকতার আদি প্রতিশ্রুতি
‘আধুনিকতার’ কোন একক সংজ্ঞা নেই। অর্থশাস্ত্রে আধুনিকায়ন [মডার্নাইজেশন] বলতে নগরায়ন, শিল্পায়ন প্রভৃতি ধারণা ব্যক্ত হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্বে [ইংরেজিতে_ সোশ্যাল থিওরি] আধুনিকতা বা মডার্নিটি আবার ‘পুঁজিবাদ’ ধারণার সমার্থক। উত্তর-আধুনিকেরা অবশ্য পরবর্তীতে দেখিয়েছেন যে, প্রথাগত সমাজতন্ত্রের ধারণাতেও আধুনিকতার মন্দ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পুঁজিবাদের মতো প্রথাগত সমাজতন্ত্রেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নির্মাণে, শিল্পায়নের পরিকল্পনায়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে, নগর-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রায় একই ধারার প্রযুক্তি-নির্ভর অবিবেচক মানসিকতা, একই ধরনের প্রবৃদ্ধি [গ্রোথ] মুখীনতাকে মানব-কল্যাণের উপরেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। স্তালিনের শাসনামলেই ‘আদি সমাজতান্ত্রিক পুঁজি সঞ্চায়নের’ মাধ্যমে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবৃদ্ধিশীল দেশে পরিণত হয়েছিল ১৯২৬-৩৬ পর্বে। এই অভিজ্ঞতা পরবর্র্তীতে ফেলদ্ম্যান-হ্যারড ডোমার প্রবৃদ্ধি-মডেলের উপত্তিগত ভিত্তি যুগিয়েছিলেন। এটা করতে গিয়ে যে অমানুষিক খেসারত দিতে হয়েছিল সেটা বড় বিবেচনা নয় এখানে। এর মধ্য দিয়ে প্রথাগত সমাজতন্ত্রে ক্রমশ স্থান করে নেয় যন্ত্র-মানব, যন্ত্রের রাজত্ব, বৃহত্তর-অর্থে ‘কলের নেশন’। ‘রক্তকরবী’র রাজা যেমন অনুভব করেছিলেন তারই সৃষ্ট যন্ত্র আর তার বশ্যতা মানছে না সেভাবেই একপর্যায়ে বিপর্যস্ত বোধ করেছিল প্রথাগত সমাজতন্ত্র। ক্রমশ প্রকৃতির প্রতি মেষপালকের মমতাময় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে জায়গা করে নিতে থাকে যন্ত্র-মানবের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। ‘আই-রোবট’ সিরিজের লেখক আইজাক আসিমভ যেসব রোবটিক্যাল প্রিন্সিপলের কথা বলে গেছেন_ যা নিয়ে একুশ শতকে আমাদের আরও ভাবতে হবে_ সেসব নিয়ম মানেনি কলের রাজত্বের নব্য শাসকেরা। এর ফলেই নিয়ম উনিশ-বিশ শতকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থাই ধারাবাহিকভাবে সংকটে পড়েছে।
এনলাইটেনমেন্টের তাত্তি্বকরা আধুনিকায়নের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই যুগ এখনও আমাদের দেখতে বাকি। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের একটি বড় অংশই সে কথা মনে করেছেন। টেকনোলজিক্যাল মেন, ওয়ান-ডাইমেনশনাল মেন, ডেথ অব মেন_ এসব ধারণার মধ্য দিয়ে সমালোচকেরা চেয়েছেন সভ্যতার নতুন পর্যায়। দেরিদাঁ যাকে সুন্দর করে বলেছেন একটি আপ্ত-বাক্যে_ ‘যে গণতন্ত্র আসতে বাকি’ [ডেমোক্রেসি-টু-কাম]। অর্থাৎ এখন গণতন্ত্রের নামে উন্নত বিশ্বে [এবং সারা বিশ্বে] যা চলছে তা প্রকৃত গণতন্ত্র নয়। আধুনিকতার মধ্যেই যারা বিকল্প সম্ভাবনা খোঁজেন সে রকম একজন জার্মান দার্শনিক হাবেরমাস_ তারও বক্তব্য এটাই। পাবলিক রিজন বা তর্ক-বিতর্ক-সমালোচনার মধ্য দিয়ে সিভিল সমাজ নতুন কোন পথ খুঁজে নেবে ইউরোপে যা পাশ্চাত্যের অসম্পূর্ণ গণতন্ত্র ও অসাম্যকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। বোদ্রিলার থেকে লিওতার পর্যন্ত ‘খাঁটি’ চরম উত্তর-আধুনিকতাবাদীরাও এতে হয়তো সায় দিতেও পারেন।
৩. ‘আধুনিকতা’ কি করতে চাইছে?
যে বিষয়ে সংজ্ঞা দেওয়াই কঠিন তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করাই এক ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব। আধুনিকতার সরলতম সংজ্ঞায় মৌল উপাদানকে [দাবিকে] চিহ্নিত করা যেতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া হচ্ছে আধুনিকতার প্রথম দাবিটি। সেটি হচ্ছে, সব ধরনের সমাজকেই একটি অভিন্ন ছাঁচে ঢালার চেষ্টা, বা সমসত্ত্বতার [হোমজেনিটি] দাবি। মনে করুন, আপনি গত এক মাসে বিভিন্ন মহাদেশের বেশক’টি দেশের বড় বড় শহরেই ঘুরে এলেন। প্রতিটা শহরেই আপনি থেকেছেন পাঁচতারা হোটেলে। প্রতিটা হোটেলেই যে রুমে আপনি ছিলেন তাতে ছিল একই ধারার টিভি, বাথরুমের অভিন্ন ফিটিংস, কার্পেটিং এবং দেয়ালে প্রায় একই ধারার আধুনিক চিত্রকর্ম। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে যে রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেলেন সেটিও [ধরা যাক] ছিল ম্যাকডোনাল্ডস বা কেএফসি। এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেলেন একই ধারার বিমানে করে, একই ধরনের সিটে বসে, একই ধরনের হলিউডি বা বলিউডি সিনেমা দেখতে দেখতে এবং প্রায় একই ধরনের স্ন্যাক ও পানীয় খেতে খেতে। এমনকি প্রায় একই ধরনের হাসি হেসে প্রায় একই ধরনের পোশাকের ও চেহারার বিমানবালা আপনাকে জানালো তার মাপা অভিবাদন। প্রায় একই চেহারার বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আপনি প্রায় একই রঙের ক্যাবে করে শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখানে সর্বত্র দেখেছেন একই ধরনের কোম্পানির বিজ্ঞাপন সংবলিত বিলবোর্ড। এত ‘সমসত্ত্বতার’ মধ্যে চলতে চলতে, বাস করতে করতে, একসময় আপনার হঠাৎ মনে হতেই পারে যে আপনি আসলে কোথাও যাননি, একই জায়গাতেই রয়ে গেছেন। আপনি আসলে টেরই পাচ্ছেন না কখন আপনি মেক্সিকো সিটিতে, কখন ন্যুয়র্কে, লন্ডনে, বার্লিনে, জোহানেসবার্গে, দুবাইয়ে, দিলি্লতে, ব্যাংককে বা সিডনিতে আছেন। এসব শহরের যে সার্কিটে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাতে করে স্থানের ও সময়ের কোনো বিশিষ্টতা খুঁজে পাচ্ছেন না আর [একমাত্র গায়ের রঙে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা ছাড়া]। কেননা, পোশাকে-আশাকেও সর্বত্র আপনি যাদের দেখছেন তারা প্রায় একই ধাঁচের জিনস, টপস, সানগ্গ্নাস পরে হালফিলের ল্যাপটপ বা আই-প্যাড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গল্পটা কল্পিত হলেও অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য নয়। আধুনিকতা নিয়ে ভাবতে গেলে আমরা এমনই এক সমসত্ত্ব সমাজকে [জগতকে] কল্পনা করি। এই হচ্ছে আধুনিকায়নের পয়লা নম্বর দাবি। পুঁজিবাদ সারা বিশ্বকেই তার নিজের ছাঁচে গড়ে-পিটে তুলবে তা সে আদিবাসী-অধ্যুষিত অরণ্যই হোক, কৃষক-সমাজই হোক, আর নোমাডিক বা বেদুইন পশুপালক গোত্রই হোক। সুদূর জাভা থেকে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, দূরবর্তী পাপুয়া নিউগিনি থেকে আন্দিস পর্বতমালা, ভারতবর্ষ থেকে সাহারা অঞ্চলবর্তী আফ্রিকা_ সর্বত্রই শিল্প-পুঁজি, বণিক-পুঁজি বহুজাতিক পুঁজি তার বাজারের সন্ধানে অনুপ্রবেশ করবে, বদলে দেবে প্রাগ-পুঁজিবাদী দৃশ্যপট এবং দেখাবে একটাই সিনেমা_ মেড ইন ইউএসএ বা মেড ইন ইউরোপ। সমসত্ত্বতার এই দাবিতে ক্ষুব্ধ উত্তর-আধুনিকেরা। তাদের বক্তব্য এর ফলে হ্রাস পাচ্ছে জীবনবৈচিত্র্য, সামাজিক বৈচিত্র্য, প্রতিভার বৈচিত্র্য। এই আধুনিকতা আসলে সৃষ্টিশীলতা বিনাশী, কেননা এটা ব্যক্তিক/আঞ্চলিক সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করছে। তাছাড়া সমসত্ত্ব ছকে ‘উন্নয়ন’ সম্ভব নয়, যেমন এক সাইজের জ্যাকেটে সবাইকে কাপড় পরানো চলে না। যদিও ওয়াশিংটন কনসেসাস সেটাই করতে চেয়েছিল গত দু’দশক ধরে। আধুনিক সরল সমসত্ত্বতার বিপরীতে উত্তর-আধুনিকেরা চেয়েছেন জটিলতর অসমসত্ত্বতা, বিভিন্ন কোরাস, ভিন্ন ভিন্ন পথে চলার নমনীয়তা।
আধুনিকতার দ্বিতীয় দাবিটি ক্ষমতা-সম্পর্কিত। এককেন্দ্রিক বা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতি আধুনিকতার পক্ষপাতিত্ব। এর সবচেয়ে কাছের উদাহরণ_ আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা। সমাজে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকলেও রাষ্ট্র্রের ক্ষমতা সমাজের আর সব ক্ষমতার উপরে। সবার উপরে রাষ্ট্র সত্য তাহার উপরে নাই_ এটি হচ্ছে আধুনিক চণ্ডীদাসের স্ল্নোগান। প্রথাগত সমাজতন্ত্রেও একই চেহারা। পার্টির বা এর পলিটব্যুরো সেখানে ক্ষমতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। তুলনায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভবন থাকলেও সেখানেও রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী-নির্ভর সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রাতীগ ক্ষমতার প্রায়োগ করে থাকে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর এক বিশ্বের ধারণা সারাবিশ্বে ক্ষমতার এককেন্দ্রিক প্রয়োগকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। বিশ্বব্যাংকে বিশ্বের প্রায় সব দেশই সদস্য। কিন্তু সেখানে এক দেশ এক ভোট প্রথা নেই। বিশ্বব্যাংকের তহবিলে যার হিস্যা যত বেশি তার তত বেশি ভোট। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে একাই প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভোটে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ সবই সমান, বলা হলেও আধুনিক গণতন্ত্রে কেউ কেউ ‘বেশি সমান’। এ ধরনের গণতন্ত্রে এক মানুষ-এক ভোট ব্যবস্থার পরিবর্তে কার্যত প্রবর্তিত হয় এক ডলার-এক ভোট ব্যবস্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা যার যত বেশি তার হাতে তত বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের পটভূমিতে স্টিগলিৎজ মহাশয় এই বিষয়টিকে নতুন করে সামনে এনেছেন।
আধুনিকতার এই দ্বিতীয় দাবিটিকেও মেনে নিতে পারেননি উত্তর-আধুনিকেরা। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ কালের পুঁজিবাদের সঙ্গে সেকালের পুঁজিবাদের পার্থক্য ঘটে গেছে গত কয়েক দশকে। সেকালের পুঁজিবাদে ক্ষমতার প্রয়োগ হতো এক-কেন্দ্র থেকে। কিন্তু এ কালের পুঁজিবাদে ক্ষমতা আর এক কেন্দ্রে সীমিত নেই; ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র ও উৎস ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে। এটি ছড়িয়ে আছে স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্যনিবাসে, জেলখানায়, পুলিশ ও সামরিক দপ্তরে, পরিবারের ভেতরে, বাজারের সিন্ডিকেটে, টেলিভিশনের চ্যানেলে, পত্রিকার সম্পাদকীয়তে, খেলার মাঠে অর্থাৎ ক্ষমতা প্রায় সর্বত্র বিরাজমান। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভুত্বশীল শ্রেণীর ক্ষমতার চর্চাকে পূর্ণ গণতন্ত্রায়ন করতে গেলে বা জনমানুষের স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূলে নিতে গেলে শুধু রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে বা রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রায়ন করলে চলবে না। সমাজের আর বাদবাকি যেসব প্রতিষ্ঠানের কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তার প্রতিটাতেই গণতন্ত্রায়ন সাধিত হতে হবে। মিশেল ফুকো যেমন দাবি করেছেন, ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রে থাকে না; এটা বহমান রয়েছে শিরায়-উপশিরায়-তন্তুতে_স্নায়ুকোষে-ডিএনএ-তে। উত্তর-আধুনিকেরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতার এই সর্বব্যাপী অস্তিত্বের কারণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলালেই ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটে না, এতে করে বড়জোর ক্ষমতার হাতবদল ঘটে মাত্র। এই সূত্রে তাঁরা প্রথাগত সমাজতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার আরও বোঝা হয়ে ‘গেড়ে বসাকে’ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। জারতন্ত্র সরিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলেও ক্ষমতার দাপট কমেনি। পার্টি ও রাষ্ট্রের একশ্রেণীর আমলাদের হাত দিয়ে ক্ষমতার চর্চা চলেছে। এর কারণ, সমাজের নানা স্তরে জারতন্ত্রের শেকড় রয়ে গিয়েছিল অথবা নতুন করে পার্টিতন্ত্র সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার ক্ষমতার শেকড় ছড়িয়েছিল। মার্কস কথিত ‘ফ্রি এসোসিয়েশন অব ফ্রি প্রোডিউসার্স’ আর করা যায়নি। এ তো গেল প্রথাগত সমাজতন্ত্রের কথা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতা চর্চার আরও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শেকড়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন ফুকো ও তার অনুসারীরা। যেমন ফুকোর একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে, ক্ষমতাসীনেরা টিকে থাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, সত্য-উদ্ভাবনের মাধ্যমে। বস্তুগত উৎপাদনের মতো ‘সত্য-উৎপাদন’ পুুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। এসব সত্য আপাত দৃষ্টিতে স্থান-কাল নিরপেক্ষ উদাহরণ মনে হলেও এসবের পেছনে কলকাঠি নাড়ছে ক্ষমতা-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। আবদুল মান্নান সৈয়দ যেমন লিখেছিলেন, ‘সত্যের মত বদমাশ’। এমনকি নিরীহতম গবেষণা-কাণ্ড যেটি তার মধ্য দিয়েও এমন সব সত্য উদ্ভাবন বা নির্মাণ করা হচ্ছে যার আসল লক্ষ্য_ মানবকে আরও বেশি করে শাস্ত্রের অধীনে আনা, এনে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, তাকে মুক্ত করা নয়। ফুকো যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস ঘেঁটে জানিয়েছেন, ‘স্বাভাবিক’ ও ‘অস্বাভাবিক’ ব্যবহারকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নতুন মনোবিদ্যায়। ব্যবহারের ‘স্বাভাবিকীকরণের’ [নর্মালাইজেশন] মাধ্যমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংক্ষুব্ধ শক্তিকে বশীভূত করা হয়েছে বিভিন্ন বিদ্যার, বিজ্ঞানের, রীতির, আচারের সমবেত প্রয়োগের মাধ্যমে। এর ফলে এক পর্যায়ে খাঁচার সব দরোজা খুলে দিলেও বনের পাখি আর উড়ে যেতে পারছে না_ স্বেচ্ছায় সে থেকে যাচ্ছে গৃহপালিত পাখি হিসেবেই।
উত্তর-আধুনিকেরা এই সত্য-উৎপাদনের তত্ত্ব ও তার ফল-পরিণামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক হিসেবে ফিরে যাচ্ছেন আন্তোনিও গ্রামসির সর্বেশ্বরতার [হেজিমনি] তত্ত্বে। আল থুসারের ‘আইডিওলজিক্যাল এপারেটাস অব স্টেট’ ধারণারও এটি কিছুটা অনুবর্তী। তবে গ্রামসি ও আল থুসার দুজনেই সত্য [বা ভাবাদর্শ] উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্র-ক্ষমতার বা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচ্ছন্ন প্ররোচণা হিসেবে দেখেছিলেন। উত্তর-আধুনিক তাত্তি্বকদের কাছে, সত্য-উৎপাদন কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন চক্রের সজ্ঞান ষড়যন্ত্রের পরিণাম নয়। রোগ-জীবাণুর মতো তত্ত্ব বা সত্য নিজেই ক্ষমতার ধারক-বাহক হয়ে উঠতে পারে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে_ তাতে রাষ্ট্রের বিশেষ দপ্তরের ষড়যন্ত্রের বা সালতামামির প্রয়োজন নেই। এর মধ্য দিয়ে উত্তর-আধুনিকেরা নিজস্ব মূল্যেই তত্ত্ব নির্মাণ, মতাদর্শ প্রচার, বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ_ জ্ঞানচর্চার যে কোন রূপকেই_ আরও বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে, জোরালো ভাবে, বিচারের দাবি জানিয়েছেন।
তবে একটি প্রশ্নে আধুনিকতাবাদী ও উত্তর-আধুনিকতাবাদী উভয়েই এক-অবস্থানে। উভয়েই মনে করেছেন যে একালের পুঁজিবাদে সবকিছুই পরিণত হয়েছে পণ্যে। শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানব-সৃষ্টির কোনো শাখাই আর মার্কস-কথিত পণ্যমোহবদ্ধতার [কমোডিটি ফেটিশিজম] বাইরে, থাকছে না। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সব কিছুই যদি পণ্য হয় [যেমন চে গুয়েভারার বিপ্লবী প্রতিকৃতির পোস্টার] তাহলে মানব-মুক্তি আসবে কোন পথে? যদি সমাজের সব খাতই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়ে থাকে তাহলে প্রতিরোধ দানা বাঁধবে কি করে? এর উত্তরে ফুকো বলেছিলেন, যেখানেই ক্ষমতা সেখানেই প্রতিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। মানুষের মধ্যে কোথাও স্বভূমির অস্তিত্ব থেকে যায় সমস্ত বন্দিদশার মধ্যেও। যেখানে পাখা মেলে মুক্তির বাসনা। ফুকো নিজেকে কখনো উত্তর-আধুনিক বলে দাবি করেননি। তবে ফুকো বা উত্তর-আধুনিকেরা ‘আধুনিকতার’ যে সমালোচনা নির্মাণ করেছিলেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে। তাঁরা প্রায় কেউই উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপের বাইরের তৃতীয় বিশ্বের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিতে পারেননি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে জোরেশোরে এগিয়ে আসে উত্তর-উপনিবেশিক সমাজের তাত্তি্বকেরা। উত্তর-উপনিবেশিকতাকে [পোস্ট কলোনিয়ালিটি] বিচারের মধ্যে এনে তারা পুঁজিবাদী আধুনিকতার আরেকটি চেহারা তুলে ধরেন। এই চেহারাটি মূলত ‘কপট, প্রতারক ও মায়াবী’ আধুনিকতার, যার মোদ্দা কথা হলো : হয় ছলে, নয় বলে, যে কোনো কৌশলে সাম্রাজ্য বিস্তার করো, অথবা প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম_ এমন শক্তিকে যে কোনো উপায়ে দুর্বল করে দাও। বাংলার উপনিবেশিক আমলের একটি উদাহরণ এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় টেনে আনছি। এর মধ্য দিয়ে উপনিবেশ ও উত্তর-উপনিবেশের পরিসরে আধুনিক ক্ষমতা-সম্পর্কের ‘কপট প্রতারক ও মায়াবী’ চরিত্রটি কিছুটা হলেও শনাক্ত করা সম্ভব হবে।
৪. আধুনিকতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ
উনিশ শতকের তিরিশের দশকের কথা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। উপনিবেশ ভারতের শিক্ষাদানের ভাষা, পাঠ্যসূচি ও সাহিত্য কীভাবে গড়ে তোলা উচিত তা নিয়ে জোর তর্ক চলছে ইংরেজদের মধ্যে। তর্কটা হচ্ছে ওরিয়েন্টালিস্ট ও এংলিসিস্টদের মধ্যে। কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সদস্যরা এ নিয়ে প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত। ১৮৩৫ সালে লিপিবদ্ধ এর কার্যবিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে, কমিটির অর্ধেক সদস্যরা ইংরেজিতে শিক্ষাদানের পক্ষে রায় দিয়েছেন। বাকি অর্ধেকের রায় নেটিভদের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষারীতির পক্ষে। আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় পাঠদান অব্যাহত থাকুক_ এটাই তারা চাইছেন। তরুণ জন স্টুয়ার্ট মিলও এই শেষোক্ত দলের পক্ষ হয়ে কলম ধরেছেন। এই বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছেন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক নিজেও। বিদগ্ধ টমাস বেবিংটন ম্যাকলে চান নেটিভদের মধ্যে এংলিসিস্ট সাহেবদের একটি দেশীয় শ্রেণী গড়ে তুলতে। তাঁর লক্ষ্য, উপনিবেশ ভারতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কেবল ইউরোপীয় সাহিত্যের পাঠদান করা। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এ পথেই কেবল শিক্ষার বিস্তার ঘটতে পারে উপনিবেশে। আলোকপ্রাপ্তি হতে পারে স্থানীয় অধিবাসীদের। এভাবেই বর্বরতার যুগ থেকে উত্তরণ ঘটতে পারে আধুনিকতায়। বিতর্কের এক পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকলে সাহেব যা বললেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের ইংরেজ শাসকদের জন্য ‘ম্যানিফেস্টো’ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোটা দাগে সেটা শোনালো এ রকম : ‘আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আসলে কোন ভাষা জানাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? অবশ্য সংস্কৃত বা আরবি কোনো ভাষাই আমার জানা নেই। তবে, এসব ভাষার কতটুকু অন্তর্নিহিত মূল্য তা যাচাইয়ের জন্য যা করার তার সবই আমি করেছি। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থগুলো আমি পড়েছি। যারা এসব ভাষায় কথা বলে থাকেন তাদের সঙ্গে আমি আলাপ-আলোচনা করেছি। যারা প্রাচ্যবিদ বলে পরিচিত, প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে আমি মান্য করি। এসব প্রাচ্যবিদের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত একজনকেও পাইনি যিনি অস্বীকার করেছেন যে, একটি ভালো ইউপরোপীয় গ্রন্থাগারের যে কোনো তাকও ভারতবর্ষ ও আরব ভূভাগের সমগ্র নেটিভ সাহিত্যের সমান মূল্যবান!’ ম্যাকলে সেদিন যা বললেন, তার একদশকের মধ্যে বাংলায় শুরু হলো ‘রেনেসাঁ’। ১৮৫০-এর দশকে রেলগাড়িও এলো এদেশে। এরপর থেকে গ্রাম হয়ে গেল অজপাড়া-গাঁ, আর শহর হয়ে পড়ল আধুনিকতার কেন্দ্র। সেদিনের নবজাগরণের নায়কেরা ম্যাকলের কথাতেই আস্থা আনলেন। তাঁদের সবারই স্বপ্ন ছিল, ম্যাকলে বর্ণিত ইউরোপীয় ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ওপর ভর করে ‘আধুনিক জাতি’ হিসেবে একদিন জগৎ সভায় তাঁদের সমাজ স্থান করে নেবে। ঔপনিবেশিক চিন্তার সঙ্গে আমাদের নাড়ির বন্ধনের সেখানেই সূত্রপাত। আধুনিকতার স্বপ্ন দেখার শুরু সে সময়েই। বিষয়টা তাহলে দাঁড়াচ্ছে_ আমাদের জীনের সমস্যা।
এর পরবর্তী একশ বছর ধরে ‘আধুনিক’ শব্দটা এতটাই প্রবলভাবে আক্রান্ত করেছিল আমাদের যে তা’ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ‘সভ্যতা’ বা সিভিলাইজেশনের নামান্তর। উনিশ-বিশ শতকের ভদ্রসম্প্রদায় বা ভদ্রলোক এসব শব্দবন্ধের মধ্যে যে ভদ্রতার ‘ধারণা’ মিশে ছিল তাকে ওই আধুনিকতার বাইরে আর কল্পনা করা যাচ্ছিল না। যুক্তিটা ছিল এ রকম : প্রাগ-আধুনিকেরা প্রাচীনপন্থি, রক্ষণশীল, পুরনো সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ জীব; যেন তারা প্রায় অসভ্য, আন-সিভিলাইজড। এর বিপরীতে আধুনিকেরা হচ্ছে প্রগতিপন্থি, চলতি হাওয়ার দল, বিজ্ঞানমনস্ক, জাত-পাত না-মানা বিদ্রোহী; যেন তারাই একমাত্র সভ্য, সিভিলাইজড। এ রকম দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল বাংলার বিদ্বৎসমাজ_ প্রথমে হিন্দুরা, পরে একপর্যায়ে এই বিভক্তি দেখা দিল কালক্রমে মুসলমান সমাজেও। অবশ্য কারও কারও মতিভ্রমও হলো_ একবার কেউ এ দলে নাম লেখালেন, আরেকবার অন্য দলে ভিড়ে গেলেন। যেমনটা হলো কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মশাররফ হোসেনের ক্ষেত্রে। কিন্তু আধুনিকতাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শিবিরবিভক্তির কয়েকটি বেদনাদায়ক ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অন্যত্র, যার প্রভাব বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য ভালো হয়নি।
প্রথমত, ইউরোপীয় ধারা মেনে চললে আধুনিক, নইলে তা রক্ষণশীল ও অনাধুনিক_ এ রকম একটি চটকজলদি সমীকরণ তাঁবু গাড়ল প্রথাগত জ্ঞানচর্চায়। এমনকি মনের ভুবনেও_ সেটা কিছুটা জ্ঞাতসারে, কিছুটা অজ্ঞাতসারে। প্রাগ-আধুনিক হয়েও তো সভ্য, ভদ্র ও বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায়। যেতে পারে। এ রকম সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া আর সহজে সম্ভব হলো না। শুধুমাত্র এই কারণেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়_ যিনি ধর্ম ও পরিবার চিন্তায় সনাতনীয় হলেও ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান এ দুই ধর্মের মধ্যে ব্যবহারিক, জ্ঞানগত ও আত্মিক যোগসূত্র স্থাপনে বিশ্বাসী ও উদগ্রীব_ তার সমসাময়িক বঙ্কিমের মতো তেমন কোনো গুরুত্ব পেলেন না বাংলার বিদ্বৎসমাজে। বঙ্কিমকে উপর্যুপরি ‘আনন্দমঠ’ ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’ লেখার পরও সে রকম কোনো অপযশ কুড়াতে হলো না তাঁর স্বধর্মীদের কাছ থেকে। অথচ, ভূদেব ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’-এর মতো মৌলিক গ্রন্থ লিখেও পেলেন না সামাজিক বিজ্ঞানীর যথাবিহীত সম্মান। অর্থশাস্ত্রে বঙ্কিমের তুলনায় তাঁর অধিকতর বুৎপত্তিও আড়ালেই থেকে গেল। এর কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর দেখা হয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতের এক পথিকৃৎ ‘আধুনিক চিন্তক’-এর ভূমিকায় [যে আধুনিকতার সংজ্ঞা আবার উপযোগবাদী মিল বেন্থাম দ্বারা নির্দিষ্ট]।
দ্বিতীয়ত, প্রাগ-আধুনিক মানেই প্রাচীনপন্থি ও রক্ষণশীল এ রকম মনে করার কারণে যা-কিছু ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের বাইরে, তাকেই অস্বীকার বা খাটো করে দেখার একটা প্রবণতা দেখা দিল। মহামতি কৌটিল্য যে কিসিঞ্জারের মতোই ‘আধুনিক’ হতে পারেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিস্তারে সে সম্ভাবনাকে আমলে নেওয়া হলো না। আকবর বাদশাহ ও আবুল ফজল মিলে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে নমুনা খাড়া করেছিলেন তা ইউরোপীয় ‘সেক্যুলার’ আদর্শের তুলনায় কোনো অংশে কম আদরণীয় অর্জন ছিল না_ সেটাও আমরা অনেককাল পর্যন্ত মনে রাখিনি। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে চেষ্টা করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য_ বিশ্ব সভ্যতার এ দুই ঐতিহ্যের মধ্যে সভ্যতার ‘সমকক্ষতা’ প্রতিষ্ঠা করতে। ইউরোপের মানবতন্ত্রের সাথে বাংলার আউল-বাউল-সহজিয়া ধারার ‘মনের মানুষ’-এর মানবতন্ত্রের মধ্যে ‘সমকক্ষতা’ প্রতিষ্ঠা করা ও তাঁর দর্শনচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এককথায়, তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে বাংলার আধুনিকতাকে সমকক্ষতার ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করতে। কিন্তু তার কথা আমরাও শুনতে চাইনি, আর ইউরোপীয় মনীষা শুনতে চাইলেও তা বুঝতে অপারগ থেকেছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো রবীন্দ্রনাথও যে মুক্ত-চিন্তক বা ‘ফ্রি-থিংকার’ হতে পারেন, সেভাবেও আমরা তাকে বিচার করতে পারি_ সেসব কোনো সম্ভাবনা আমাদের মনে জাগেনি। ১৮৩৫ সালের কার্যবিবরণীতে ম্যাকলে তাঁর ভাষণে যেমন বলেছিলেন, প্রাচ্যের আছে কেবল কিছু মহান কবি, কিন্তু তারা তো কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করে থাকেন মাত্র। জ্ঞানের রাজ্যে তাদের কোনো দক্ষতা নেই। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা সেভাবেই কমবেশি কবির শিরোপা পরিয়ে দিয়ে জ্ঞানচর্চার মূলক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রেখেছি।
প্রাগ-আধুনিককে খাটো করে দেখার কারণে তৃতীয় যে সমস্যা দেখা দিল তা হলো, ইউরোপীয় আধুনিকতাকে বাস্তবের চেয়ে অনেক বড়ো ও মহার্ঘ করে আমরা দেখতে শুরু করলাম। এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এখনও বিশ্বব্যাংক বা মার্কিন দূতাবাস বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিছু বললে আমরা ‘তা ঠিক, তা ঠিক’ করতে থাকি। উপনিবেশে ইউরোপ যেসব নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রযন্ত্র, তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা শুরু করল তাকেই আমরা নির্বিচারে মেনে নিতে শুরু করলাম ‘আধুনিক মানুষ’ হওয়ার সাধনায়। ইউরোপ যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ওপর গুরত্ব দিতে শুরু করল উনিশ শতকে, উপনিবেশে তারা গ্রহণ করল ভিন্ন নীতি। এ ক্ষেত্রে তারা নিল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতাবান করার নীতি। সেই পথ ধরে আমরাও ভাবতে শুরু করলাম যে, আধুনিক রাষ্ট্র মানে আসলে এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা। ইউরোপ উনিশ শতকের শেষ থেকে নিজের দেশে আস্তে আস্তে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, গণস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থা চালু করতে শুরু করল। কিন্তু উপনিবেশে সেসব ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠাই পেতে দিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতো ইউরোপীয় শাসকদের কেউ কেউ আদিতে চেয়েছিলেন কৃষিতে স্ব-আবাদি ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু কার্যত যা গড়ে উঠল তা হচ্ছে এক আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থা, যার মূল অভিপ্রায় ছিল এক অনুগত ও বাধ্যগত দেশীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করা। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আশ্রয়েই এ দেশে গড়ে উঠল এক জনবিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র যেটা আদৌ খোদ ইউরোপে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। এককথায়, ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকেই ‘আধুনিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত’ মনে করে আমরা না-পেলাম প্রাগ-আধুনিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ মনীষার ছায়া, না-পেলাম ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সেরা অন্তর্দৃষ্টি। এর বড় প্রমাণ, প্রত্যক্ষ উপনিবেশের অবসানের পরেও আমরা নিজেদের মতো করে উন্নয়ন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি ভাবতে ও গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলাম না। ‘ইউরোপ উদ্ভাবন করবে এবং আমরা কেবল তার প্রয়োগ করব’, অর্থাৎ আমরা চিরকালই থাকব হাত পেতে_ এই মানসিক ছক থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমাদের হলো না। আমরাও অনেক খাতে উদ্ভাবন করব এবং বাদবাকি বিশ্ব তা প্রয়োগ করবে_ এ রকম কোনো জ্ঞানভিত্তিক অভিমান আমাদের মধ্যে আজও এলো না। ফলে একজন দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ, একজন দ্বিতীয় সত্যেন বোস, একজন দ্বিতীয় মুহাম্মদ ইউনূস_ যারা সারা বিশ্বে বঙ্গ, বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশকে সৃষ্টিশীলতার মানদণ্ডে অতীতে ও সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠা করেছেন_ তারা শুধু ব্যতিক্রমী উদাহরণই হয়ে থাকলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কত কথা হচ্ছে এখন। বলা হচ্ছে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা। অথচ আজকের ঢাকা শহর যতই ‘আধুনিক’ বলে নিজেকে দাবি করুক না কেন, এখানে আজও প্রতিষ্ঠা পায় না অন্তত একটি দ্বিতল বা ত্রিতল বই-পত্রের ভবন, যেখানে থাকবে নানা দেশের ও শাস্ত্রের বই, যার নিকটতম তুলনা হতে পারে আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো বার্নস-এন্ড-নোবলস বা ওয়াটারস্টোনস। অর্থাৎ আধুনিকায়নের মন্ত্রটাও আমরা সঠিকভাবে আওড়াতে পারিনি।
আধুনিকতার মূল সমস্যাটা রামমোহন রায় বা দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠিকই কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় বা বৃহত্তর অর্থে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সে যা বলে, যা আদর্শ হিসেবে প্রচার করে, সেটা সে আসলে মেনে চলতে চায় না। অর্থাৎ নিজের খেলার নিয়ম সে নিজেই বারবার ভাঙে। এটা রামমোহনের বুঝতে দেরি হয়নি। রামমোহন যেমন ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে ম্যাকলের পক্ষে। তাঁর যুক্তি ছিল, উপনিষদ, ইসলাম ও ইউনিটেরিয়ান চার্চের মধ্যে রয়েছে একেশ্বরবাদী মতাদর্শের ঐক্য। ইংরেজরা যদি ইংরেজি স্কুল ও ইংরেজি মাধ্যমে বিদ্যাদান করতে চায়, তবে তাই হোক। কিন্তু রামমোহনের শর্ত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ করা চলবে না_ চাই সবার জন্যে ইংরেজি শিক্ষা, চাই বেশি বেশি করে স্কুল, গুণগত মানের স্কুল। রামমোহন অনুসারী দ্বারকানাথও চেয়েছিলেন, বাংলায় শুধু বণিক-পুঁজির নয়, শিল্প-পুঁজিরও বিকাশ হোক। তিনি নিজে ছিলেন ১৮৩০-৪০ দশকের সবচেয়ে প্রাগ্রসর ব্যবসায়ী_ প্রথম বৃহৎ বাঙালি বুর্জোয়া।
প্যারিসের এক হোটেলে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দ্বারকানাথ জানিয়েছিলেন, প্রথাগত ধর্মীয় আচার-বিচার তিনি মানেন না এবং প্রয়োজনে তিনি ইউরোপীয় যুক্তিবাদী আদর্শে ভারতীয় সনাতন ধর্ম-কর্মকে বদলে নিতেও রাজি। এ জন্যে তিনি পণ্ডিতবর্গকে মাইনে দিয়ে পুষছেনও। তারপরও একপর্যায়ে তাঁর সঙ্গে কিছুটা মতানৈক্য হয়েই গেল পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের। তার সমসাময়িকদের কেউ কেউ আবেগের আতিশয্যে ম্যাক্সমুলারকে ডাকতেন ‘মোক্ষমুলার’, যেন এই জার্মান পণ্ডিতের লেখা পড়লে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে। দ্বারকানাথ স্রেফ জানিয়ে দিলেন_ এবং গেয়েও শোনালেন_ ম্যাক্সমুলার ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের কিছুই বোঝেন না, কিন্তু তিনি ঠিকই পাশ্চত্যের রাগ-সঙ্গীত বোঝেন ও এর রস গ্রহণে পুরোপুরি সক্ষম। অর্থাৎ বিদ্যার্জনে বরং দ্বারকানাথ কিছুটা এগিয়েই ছিলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিকতা আত্মস্থ করেও আমাদের বাড়তি কিছু দেওয়ার এখনও বহুকিছু আছে. যেমন ম্যাক্সমুলারের মতো পণ্ডিতকেও শেখানোর মতো কিছু ছিল দ্বারকানাথের।
রামমোহন-দ্বারকানাথের যৌথভাবে নির্মিত আধুনিকতা-প্রকল্পের ফাঁদে অবশ্য পা দেয়নি সদাসতর্ক ঔপনিবেশিক শক্তি। ইংরেজি ভাষাকে জনগণের স্তরে ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী। বাংলায় ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা ছিল বরাবরই অতিসীমিত, এখনও তাই। তাছাড়া সাধারণভাবে এ দেশে স্কুলের প্রসারই ছিল সীমিত। অন্যদিকে বিদেশি রীতিনীতি মেনে কারবারি ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন এনে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে গতিশীল করতে চেয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ১৮৪৭-এর বিশ্ব স্টক মার্কেটের বিপর্যয়ের পর বাংলার শিল্পখাত আর সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত। বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তি মুখে বলেছে যে তারা চায় অবাধ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু কার্যত তারা শিল্পায়নকে আরও নিরুৎসাহিতই করেছে এই পর্বে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব জন স্টুয়ার্ট মিলের পাঠ্যবইয়ে বড় আকারে থাকলেও উপনিবেশে এর প্রয়োগ হয়েছিল অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে। আধুনিকতা ও পুঁজিবাদ ‘তার নিজের আদলে বিশ্বকে গড়ে নিতে চায়’_ এনলাইটেনমেন্টের এই মন্ত্রে পুঁজিবাদ নিজেই বিশ্বাস করেনি। পুঁজিবাদ বা আধুনিকতা ‘যা বলে সে আসলে তা না’। যখনই পাশ্চাত্যের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেছে, খেলার নিয়ম ভাঙা হয়েছে, অথবা নতুন নিয়মের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গ সূত্রে বলে রাখি, পুঁজিবাদের খেলায় ক্রমশ ‘সমকক্ষ’ হওয়ার সাধনায় নামা চীন এখন রামমোহন-দ্বারকানাথের সমস্যাটা নতুন করে বুঝতে পারছে। আধুনিকতা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিশ্বকে সেটা সে রক্ষা করেনি। আসলে সেরকম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সে পারে না, কেননা তা পুরোপুরি রক্ষা করতে গেলে ক্ষমতার চর্চা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর ক্ষমতা প্রয়োগই তো আধুনিকতার অপ্রকাশ্য লক্ষ্য। উত্তর-আধুনিকবাদী দার্শনিকদের এই সমালোচনা মানি না মানি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার নয়।

 বিনায়ক সেন
বিনায়ক সেন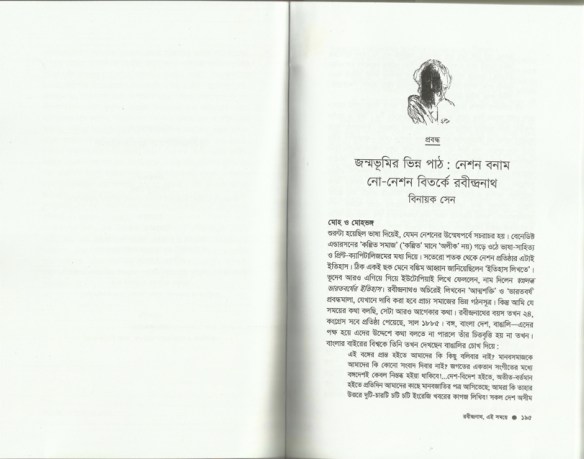

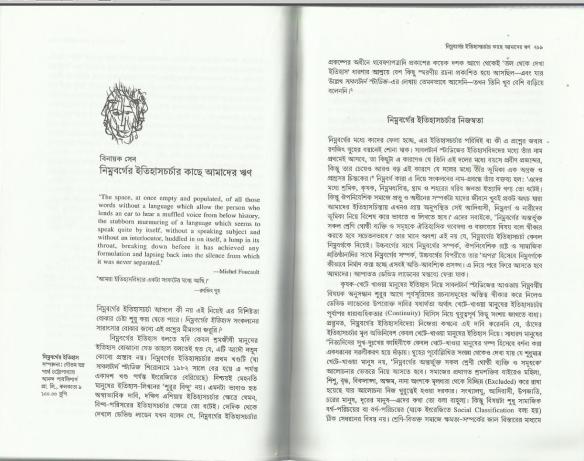
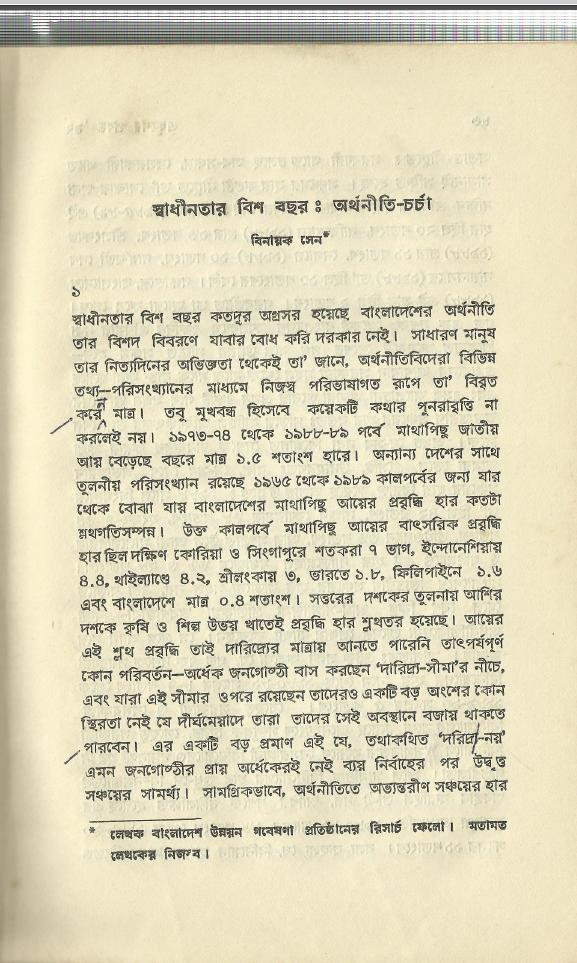

 বিনায়ক সেন
বিনায়ক সেন