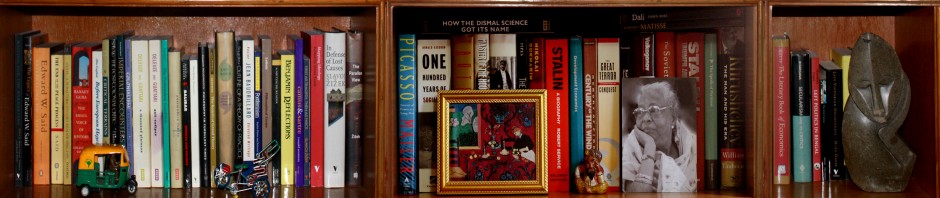পর্ব ::১৮
আমার দ্বিতীয় পছন্দ হলো, মহিউদ্দিন আলমগীরের ‘ফেমিন ইন সাউথ এশিয়া : পলিটিক্যাল ইকোনমি অব মাস স্টারভেশন’। এটি ১৯৮০ সালে প্রকাশিত। আলমগীর বইটি লেখেন যখন তিনি বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৯৭০-এর দশকে। আমার তৃতীয় পছন্দ হলো, ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মার্টিন র্যাভালিয়নের ‘মার্কেটস অ্যান্ড ফেমিনস্’। আমার তালিকার চতুর্থ অবস্থানে আছে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ১৯৭৯ সালের প্রকাশিত ‘পলিটিক্স অব ফুড অ্যান্ড ফেমিন ইন বাংলাদেশ’- এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, প্রথম তিনটির মত বই নয় যদিও, কিন্তু চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পেছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তথা মার্কিন হস্তক্ষেপের ভূমিকার বিরুদ্ধে উন্মোচনমূলক প্রথম প্রতিবাদ (ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি সাময়িকীতে প্রকাশিত)। সবশেষে উল্লেখ করব অধ্যাপক নূরুল ইসলামের ‘দ্য বার্থ অব এ নেশন : এন ইকোনমিস্ট’স টেল’ বইটির দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি। এর বাইরে অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ওসমানী তার একাধিক লেখায় চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, সেনের ‘এক্সচেঞ্জ এনটাইটেলমেন্টে’র তত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় দিক নিয়ে বিশদভাগে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, বাংলা ১১৭৬ সালের বা বাংলা ১৩৫০ সালের মন্বন্তর নিয়ে যেখানে গবেষণাপত্রের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে, ইংরেজি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ সে প্রেক্ষিতে- বিভিন্ন নিরিখের কাজের মধ্য দিয়েই- এক বহুল আলোচিত বিষয়।
এসব লেখা-পত্র থেকে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রভাবক ও কার্যকারণ সম্পর্কে যেসব প্রবণতা মোটা দাগে বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ। প্রথমত, উপর্যুপরি বন্যার তীব্র আঘাত। ব্রহ্মপুত্র সে বছর যেন ফুঁসে উঠেছিল। অন্যান্য নদ-নদীর পানিও অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ছিল। ১৯৭৪ সালের জুন মাসের শেষের বন্যায় আউশ ধানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ১৭ই জুলাই দেশের সব বড় নদীগুলোর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে, অর্থাৎ আউশ ফসল ওঠার মৌসুমেই বন্যার পানি ছড়িয়ে পড়ে ধানক্ষেতে-মাঠে। এই ক্ষতিটা সামাল দেওয়া যেত আমন ধানের আবাদের মাধ্যমে। কিন্তু আউশ ধান নষ্ট হওয়ার ১৫ দিনের মাথায়- অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই পানি আবার হুহু করে বাড়তে থাকে। যেসব জমিতে আমনের বীজতলা তৈরি হচ্ছিল সেগুলো ক্ষতির মুখে পড়ে যায়। ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম ও সিলেটের সাথে ঢাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বন্যার পানি বেড়ে ওঠার কারণে। ১১ই আগস্ট নাগাদ ঢাকার সাথে উত্তরবঙ্গের সমস্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আগস্টের মাঝামাঝি বন্যার পানি বাড়তে বাড়তে সে বছরের রেকর্ড-উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছে। এতে করে নতুন বোনা আমন ধানের একটা বড় অংশ ক্ষতির কবলে পড়ে। কিন্তু মূল আঘাতটা আসে সেপ্টেম্বরে। এ সময় বন্যার পানি ধীরে ধীরে জমার কথা। কিন্তু সে বছর ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আবারো বিপদসীমা অতিক্রম করে। এতে করে আগস্ট মাসের বন্যার পরে যতটুকু আমন ধান বেঁচেছিল সেটুকুও (রোপা আমনের অধিকাংশ) বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম উপর্যুপরি বন্যার আঘাতের পর সেপ্টেম্বরের শেষে এসে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়ার সরকারি ঘোষণা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সেদিন।
দ্বিতীয়ত, প্রায় ৬ হাজারের মতো লঙ্গরখানা খোলা না হলে আরো অনেক মৃত্যু আমাদের দেখতে হতো। সন্দেহ নেই। তবে আরো বেশি সংখ্যায় এবং দীর্ঘদিনের জন্য লঙ্গরখানা খোলার/চালু রাখার জন্য চাই প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মজুদ, আর সেই মজুদের সরকারি ক্ষমতা কমে গিয়েছিল সে বছর আন্তর্জাতিক তথা মার্কিন ষড়যন্ত্রে। ১৯৭৩ সাল থেকেই বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য ‘সাহায্য’ (ফুড এইড) হিসেবে দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মার্কিন সরকার। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে অবস্থাটা এত গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছে যে, বাংলাদেশ বাধ্য হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে খাদ্য সাহায্যের অনুরোধ জানাতে। রাশিয়া ছিল নিজেই আমেরিকা ও কানাডা থেকে খাদ্যশস্যের এক বড় আমদানিকারক। প্রায় ২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রাশিয়ার ক্রীত মজুদ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে প্রেরণের জন্যে এক জরুরি অনুরোধ জানানো হয়। রাশিয়া সেই ডাকে তখন সাড়াও দেয়। নইলে, ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসেই সেদিন এ দেশের পাবলিক রেশন প্রদানের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপ নীতির ফলে (নিক্সন-কিসিঞ্জার চক্র তখন রাষ্ট্র-ক্ষমতায়) সে দেশ থেকে খাদ্যশস্যের আমদানির ধারা চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের আগে থেকেই ছিল নিম্নাভিমুখী। এর ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে বাংলাদেশের মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল গড়ে মাসে ২ লাখ ৩২ হাজার টন, ১৯৭৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তা নেমে আসে গড়ে মাসে ৭৪ হাজার টনে মাত্র। অর্থাৎ, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস আগে থেকেই খাদ্যশস্যের আমদানি পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর একমাত্র বিকল্প হতে পারত আন্তর্জাতিক বাজারে গিয়ে সরাসরি খাদ্যশস্য কেনা। কিন্তু সেখানেও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে- ১৯৭২-৭৩ সালে যার দাম ছিল টনপ্রতি ১১৫ ডলার, ১৯৭৩-৭৪ সালে তার দাম গিয়ে দাঁড়ায় টনপ্রতি ১৯৯ ডলারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনার মত যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল না সরকারের হাতে সেদিন। ১৯৭৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যেখানে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে সেই রিজার্ভের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলারে। দুর্ভিক্ষ যখন চলছিল, সেই ৩য় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রিজার্ভের পরিমাণ আরও কমে যায়- সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন ৪০ মিলিয়ন ডলারে। বাড়তি খাদ্যশস্য সাহায্য পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সেদিন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ বাড়ানোর জন্যে। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বানচাল হয়ে যায় যখন কিউবায় পাট রপ্তানি করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ- এই অজুহাতে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা বন্ধ করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলার দাবি রাখে।
১৯৭৪ সালের ২৯শে মে (এরই মধ্যে তীব্র মৌসুমী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বিধ্বংসী বন্যা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। অকস্মাৎ ডেভিড বোস্টার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের কাছে জরুরি সাক্ষাৎকার চাইলেন। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় ৪০ লক্ষ পাটের ব্যাগ রপ্তানির পরিকল্পনা করছে, এ রকম খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে বলে বোস্টার জানতে পেরেছেন। এটা করা হলে মার্কিন খাদ্যশস্য ‘সাহায্যের’ নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ কোনো খাদ্য-সাহায্য পাবে না। ‘পাবলিক ল ৪৮০’ অনুযায়ী শত্রু দেশ ভিয়েতনাম ও কিউবার সাথে বাণিজ্য করা কোনো দেশ মার্কিন খাদ্য-সাহায্যের সুবিধে পাবে না। এটাই সে দেশের কংগ্রেসের বিধান। তখন বোস্টারকে জানানো হল যে, (ক) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের শোচনীয় পরিস্থিতি লাঘবের জন্যে হলেও এই পাট রপ্তানি করা দরকার, এবং (খ) চাইলে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে ‘অনুমতির অব্যাহতি’ (ওয়েভার) দিতে পারেন, বিশেষত যেখানে ‘নন-স্ট্র্যাটেজিক’ কৃষিপণ্যই কেবল রপ্তানি করা হচ্ছে দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে। তাতে মার্কিন পক্ষের অবস্থান নমনীয় হল না। রাষ্ট্রদূত বোস্টার সাফ জানিয়ে দিলেন, যদিও পাটের থলি হয়তো বা ‘নন-স্ট্র্যাটেজিক’ কৃষিপণ্য, তবুও প্রেসিডেন্টের কথিত ‘ওয়েভার’ মেলার কোনো সম্ভাবনাই নেই বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের উত্তরে হতবাকই হয়েছিল। কেননা, ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের পর থেকেই কিউবার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছিল এবং সে সম্পর্কে গোড়া থেকেই মার্কিন কূটনীতিবিদেরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। তদুপরি, প্রায় একই সময়ে মিসর যখন কিউবায় রপ্তানি করছিল, তখন তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। মিসর থেকে কিউবায় তুলা রপ্তানিতে সেদিন কোনো বাধা ওঠেনি; কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানিতে সেদিন প্রবল বাধা উঠেছিল। এই রহস্যের উত্তর খোঁজাও দুস্কর নয় : কিসিঞ্জারের কাছে আনোয়ার সাদাতের ‘মিসরকে’ হাতে রাখা জরুরি ছিল। আর বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া বাংলাদেশকে চাপের মুখে রেখে নতি-স্বীকার করানোর কিসিঞ্জারী নীতি পূর্বাপর তৎপর ছিল। এ কথা ক্রিস্টোফার হিচেনস তার ‘দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার’ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।
তৃতীয়ত, শুধু খাদ্যশস্যের সামগ্রিক মাথাপিছু প্রাপ্যতার বিষয়টিকে চুয়াত্তরের ‘দুর্ভিক্ষের ব্যাখ্যা’ হিসেবে নিলে সরলীকরণ করা হবে। প্রাপ্যতা একটি নির্ণায়ক, একমাত্র, এমনকি প্রধান নির্ণায়ক নাও হতে পারে। ১৯৭৪ সালের উপর্যুপরি বন্যায় প্রচুর ফসলহানির পরেও এটা বলা যেতে পারে। যেমন, ১৯৭৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার (উৎপাদন+আমদানি) পরিমাণ ছিল ১১.৫৭ মিলিয়ন টন, ১৯৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৩৬ মিলিয়ন টনে। মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার পরিমান (availability) ১৯৭৩ সালে ছিল দৈনিক ১৫.৩ আউন্স, যা ১৯৭৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় দৈনিক ১৫.৯ আউন্সে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেখলে দুর্ভিক্ষের বছরে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা এর আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি বৈ কম ছিল না। জেলা পর্যায়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিসংখ্যানও এ তথ্যকে বাড়তি সমর্থন দেয়। ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়ে ছিল প্রায় প্রতিটি জেলাতেই (কেবল বরিশাল ও পটুয়াখালী ছাড়া)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, তা হলো দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে উপদ্রুত তিনটি বৃহত্তর জেলায়- রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেটে খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে তো যায়ইনি বরং লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ তিনটি জেলায় মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্যতাও ছিল ১৯৭৩ সালের তুলনায় বেশি। এর থেকে অমর্ত্য সেন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ‘খাদ্যশস্যের সামগ্রিক প্রাপ্যতা ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষকে ব্যাখ্যা করতে সামান্যই সহায়ক হতে পারে।’ সেনের মতে, সে বছর উপর্যুপরি বন্যার কারণে ভিত্তহীন গ্রামীণ শ্রেণি তথা কৃষিমজুর ও স্বল্পবিত্ত বর্গাচাষিদের কর্মসংস্থানের পরিসর সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাস্তবে কমে গিয়েছিল। সেটাকে পুষিয়ে নিতে পারত পরীক্ষিত ‘পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম’ (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বা রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ইত্যাদি)। কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনি দুই কারণে : (ক) সরকারের কাছে ঐ সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বণ্টন করার মতো যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুদ ছিল না; (খ) ঐ সিস্টেমটি মূলত শহর এলাকার মধ্যবিত্ত মানুষদের রক্ষার জন্য রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারেই বেশি সচেষ্ট ছিল; (গ) ছয় হাজারের মতো লঙ্গরখানা চালু হলেও তা যথেষ্ট ছিল না ব্যাপক পরিসরে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য।
চতুর্থত, খাদ্যশস্যের বাজারে বেসরকারি খাতের মজুদদারি প্রবণতাও খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্যকে আরো বেশি করে উস্কে দিয়েছিল। মোটা চালের দামের ইনডেক্স ((Index of retail prices) যদি ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে হয় ১০০, তা আগস্ট মাসে বেড়ে হয় ১২১, সেপ্টেম্বর মাসে তা লাফ দিয়ে চড়ে যায় ১১৫-এ, আর অক্টোবর মাসে তা আরো বর্ধিত হয়ে পৌঁছায় ১৭৮-এ। কেবল মাত্র ডিসেম্বর মাসে তা আবার নেমে দাঁড়ায় ১৩৩-এ। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের উচ্চ ও অপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসকে অনিবার্য করে তুলেছিল।
[ক্রমশ]
Original in সমকাল