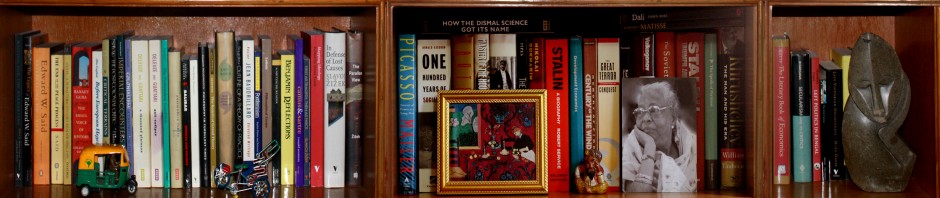পর্ব ::১৩
পূর্ব প্রকাশের পর
সুবিদিত যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেপাইদের জন্য ১৭৬৪ সালেই একটি ‘মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট’ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৭৮৫ সালে সরকারিভাবে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে আলাদা ‘মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট’-এর প্রবর্তন হয়। কিন্তু তার কার্যপরিধি সীমিত ছিল প্রশাসনিক কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেই। এদেশবাসীর জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত ছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর যখন কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে, তখন (১৮৬৯ সালে) সর্বপ্রথম ‘পাবলিক হেলথ্ কমিশনার’ পদের প্রবর্তন হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও জনসংখ্যার ‘ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স’ সংগ্রহ হওয়া শুরু হতে থাকে, যদিও এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় কেবল ১৯১৯ সালের পরেই। মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সাংবিধানিক সংস্কারের অধীনে প্রদেশগুলোর হাতে জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি বলতে চাইছি, শুধু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নয়; উনিশ শতকজুড়েই পর্যায়ক্রমে যে দুর্ভিক্ষগুলো ভারতবর্ষে (ও বাংলাদেশে) সংঘটিত হচ্ছিল, তাতে জনস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা বা বিধিমালা কার্যত ছিল না। বাংলার গ্রাম এলাকা এসব স্বাস্থ্যবিধির সম্পূর্ণ বাইরে থেকে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে রোগ-মহামারী প্রভৃতি উপসর্গে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বঙ্কিম প্রকারান্তরে জনস্বাস্থ্যের নিদারুণ অভাব বা অনুপস্থিতির কথাই পাঠককে (ও শাসকশ্রেণি) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।
তৃতীয়ত, হান্টারের বিবরণী থেকেও জানা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। ক্যানিবালিজমের উল্লেখ রয়েছে তার লেখায়। হান্টার লিখেছেন, ্তুঅষষ :যৎড়ঁময :যব ংঃরভষরহম ংঁসসবৎ ড়ভ ১৭৭০ :যব ঢ়বড়ঢ়ষব বিহঃ ড়হ ফুরহম. ঞযব যঁংনধহফ-সবহ ংড়ষফ :যবরৎ পধঃঃষব; :যবু ংড়ষফ :যবরৎ রসঢ়ষবসবহঃং ড়ভ ধমৎরপঁষঃঁৎব; :যবু ফবাড়ঁৎবফ :যবরৎ ংববফ-মৎধরহ; :যবু ংড়ষফ :যবরৎ ংড়হং ধহফ ফধঁমযঃবৎং, :রষষ হড় নুঁবৎ ড়ভ পযরষফৎবহ পড়ঁষফ নব ভড়ঁহফ;… রহ ঔঁহব ১৭৭০, :যব ৎবংরফবহঃ ধঃ :যব উঁৎনধৎ ধভভরৎসবফ :যধঃ :যব ষরারহম বিৎব ভববফরহম ড়হ :যব ফববফ.
বঙ্কিম এক পর্যায়ে হান্টারের অনুসরণ করে জন-দুর্গতির মর্মস্পশী বিবরণ দিয়েছেন! ‘লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তারপর কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগল, গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়।’
আনন্দমঠের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি সরসারি নর-মাংস ভক্ষণের দৃশ্যও প্রোথিত করেছেন। ধনী লোক মহেন্দ্র। কিন্তু তখন ‘ধনী নির্ধনের এক দর।’ মহেন্দ্র তার স্ত্রী কল্যাণীকে গৃহে রেখে তার শিশুকন্যার জন্য দুধ আনতে গেছেন। এরই মধ্যে তার গৃহে ঢুকে পড়েছে দস্যুর দল। ‘মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুস্ক। শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।’ তারা কল্যাণী ও তার শিশুকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর বঙ্কিমের প্রায় চাক্ষুষ বর্ণনাতেই শুনুন :
“তখন আর একজন বলিল, ‘রাখ, রও। রও যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে। তবে এই বুড়ার শুক্ন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব। এসো, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।’ আর একজন বলিল, ‘যাহা হয় পোড়া বাপু। আর ক্ষুধা সয় না।’ … অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।”
চতুর্থত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে শুধু অর্ধেক কৃষিজীবী জনগণের প্রাণনাশ ঘটে, তাই নয়। এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সারা বাংলায়। ডি-পপুলেশনের কারণে কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। হালচাষ করার মতো জনবলও ছিল না। বঙ্কিম লিখেছেন- ‘গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল অথবা জঙ্গলে পুড়িয়া গেল। দেশ জঙ্গলময় হইল।… চাষায় চাষ করিয়া টাকা পায় না, জমিদারের খাজনা দিতে পারে না, জমিদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। … কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়।’
এ রকম অরাজক পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ ব্যবস্থার পত্তন হয় ১৭৯৩ সালে। তার এক বছর আগে, ১৭৯২ সালে দারোগা ব্যবস্থার পত্তন হয় গ্রাম-এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। এ দেশের কৃষিতে ‘পুঁজিবাদী’ আদলের খামার-ব্যবস্থা নয়, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ-উত্তর অরাজক রাজস্ব পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে একটি স্থিতিশীল ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত করাই ছিল এর আশু লক্ষ্য।
৪. ১৮৭০-৮০ দশকের ‘উপোসি’ বাংলা
আগেই বলেছি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এসেছিল। তাতে করে সাময়িকভাবে হলেও কৃষিতে এক ধরনের স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছিল। মন্বন্তরের ফলে লোকশূন্য হয়ে জঙ্গলে পরিণত হওয়া জমি আবার ধীরে ধীরে আবাদযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কিন্তু ১৭৯৩ থেকে ১৮৯৩ এই একশো বছরে সাময়িকভাবে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থায় বাংলার কৃষকের আর্থিক আস্থার খুব সামান্যই উন্নতি হতে পেরে ছিল বস্তুত ১৮৫০ সালের পর থেকে কৃষকের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৬৮ সালের হান্টারের এনালস অব রুরাল বেঙ্গল-এর দুটি লেখা পরপর প্রকাশিত হয় যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি হচ্ছে, ১৮৭২ সালে লেখা বঙ্কিমের ‘বঙ্গদেশের কৃষক’; এবং আরেকটি হচ্ছে ১৮৭৫ সালের প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম বই ‘দ্য পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল’। [অবশ্য সত্যের খাতিরে বলা দরকার যে, এই তিনটি বইয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বেঙ্গল রায়তস দেয়ার রাইটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস’ শীর্ষক ১৮৬৪ সালের ‘ট্রিটিস’টি। অর্থনৈতিক চিন্তার ধ্রুপদী গ্রন্থ এটি।] কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে দেশের অবকাঠামোগত উন্নতি হচ্ছিল বটে, কিন্তু রায়ত বা চাষিদের জীবনে কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। অথচ বাংলার কৃষককুলই তো ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগ। আজকের যুগে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সময়ে ‘শতকরা ১ ভাগ বনাম শতকরা ৯৯ ভাগের’ বৈষম্য নিয়ে যে কথা আমরা শুনেছি, তারই পূর্বলেখ যেন পাই বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র দত্তের লেখায়। বঙ্কিম প্রবন্ধটিতে স্মরণীয় করে বলছেন : ‘ইংরাজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। … দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।’ দেশের গড় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু কৃষকের কাছে সেই শ্রীবৃদ্ধির সুফল পৌঁছায়নি। এরপর বঙ্কিম আসল কথাটা পাড়লেন: ‘আমরা দেখিলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।’ অকুপাই ওয়াল স্ট্রিটের আন্দোলনকারীরা জানলে খুশি হতেন যে তাহাদের আন্দোলনের দেড়শো বছর আগেই বাঙালি এক লেখক ৯৯ শতাংশের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটলে সেই জাতীয় ‘উন্নয়নকে’ প্রগতি বলে সাধুবাদ জানাতে অস্বীকার করেছিলেন।
বঙ্কিম যখন থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বিকেলে আড্ডা দিতে দিতে তারা দু’জনে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। বিশেষত তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন বাংলার কৃষকের ক্রম-অবনতিশীল অবস্থা নিয়ে। এ কারণেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্তের উভয়েরই কৃষকবিষয়ক লেখায় জমিদারবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের লেখার ওপরে সমসাময়িক ঘটনাবলিও প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৩ সালে পাবনা ও রংপুরের কৃষকদের বিদ্রোহ নতুন করে কৃষকদের প্রশ্নটিকে সামনে এনে দিয়েছিল। বঙ্কিম লিখেছিলেন, ‘জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালি কৃষকের শত্রু বাঙালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক, বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।’ সঞ্জীবচন্দ্র তার ‘বেঙ্গল রায়তস্’ গ্রন্থে রায়তের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : ‘লর্ড বেন্টিক বলেছেন রায়ত শব্দটির দ্বারা সমগ্র কৃষি জনগোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়ে থাকে। … তবে সাধারণ মতে ‘রায়ত’ এক নির্দিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীকেই নির্দেশ করে।’ যেমন জমিদার সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে; তালুকদার জমিদারের কাছ থেকে বড় আকারের জমি পেয়েছে; আর রায়ত জমিদারের কাছ থেকে ছোট আকারের জমি পেয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত তার বইটিতে দেখালেন যে, ১৮৫৯ সালের জমিদারি ব্যবস্থা সংস্কার-আইনে তিন ধরনের রায়তের অস্তিত্ব রেখে দেওয়া হয়েছে : (ক) যারা স্থায়ীভাবে জমিদারের জমি চাষাবাদের অধিকার পেয়েছে, অর্থাৎ যাদের জমিদাররা ইচ্ছা করলেই উচ্ছেদ করতে পারবে না; (খ) যারা কেবল ১২ বছরের জন্য চাষাবাদের অধিকার পেয়েছে (এর পরে তারা ওই জমি চাষ করতে পারবে কিনা তা জমিদারের ইচ্ছাধীন) এবং (গ) যাদের জন্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে রায়তী অধিকার নির্দিষ্ট করা নেই। এই শেষোক্ত ‘আন্ডার-রায়তরাই’ ছিল সংখ্যাধিক্যে; এদের যখন-তখন জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারত এবং এদের থেকে ইচ্ছামতো খাজনাও আদায় করা যেত। রমেশচন্দ্রের ‘দ্য পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল’ লেখার প্রধান প্রেরণা ছিল এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত অধিকারবিহীন রায়ত বা কৃষকদের জন্য ‘চিরস্থায়ী আবাদের’ অধিকার আদায় করা। অর্থাৎ, এদেরও প্রথম গ্রুপের তালিকাভুক্ত করায়। এর জন্যই তিনি নানাবিধ তর্কের জাল বিস্তার করেছিলেন বইটিতে। এক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যে, এই অধিকারহীন তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত রায়তেরাই বাংলার কৃষিতে পূর্বাপার চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাচ্ছে, এরাই পর্বান্তরে দুর্ভিক্ষের শিকার হচ্ছে বা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে থেকে যাচ্ছে।
১৮৭০-র দশকে শুধু যে পাবনা-রংপুরের কৃষকরা স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ করছিল তাই নয়, সে সময় এলাকা বিশেষ খাদ্যাভাবও দেখা দিচ্ছিল। এমনকি বাংলার ‘শস্যভাণ্ডার’ বলে পরিচিত পূর্ববঙ্গের খাদ্য-উৎপাদনে ‘উদ্বৃত্ত’ জেলাগুলোতেও ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছিল। ১৮৭০-র পর থেকেই বাংলা সামগ্রিকভাবে হয়ে ওঠে ‘উপোসি বাংলা’। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের লেখার কৃষকদের দুর্দশার যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে অবশ্য খাদ্যাভাব, মৌসুমি খাদ্য ঘাটতি ও অনাহারের থাকার বিশদ উল্লেখ নেই। ক্ষুধার বিস্তৃতির পেছনে যেমন ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত ‘কাঠামোগত’ কারণ, তেমনি এর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি জলবায়ু-পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন বন্যা ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব। শেষোক্ত প্রবণতাটি শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষ ও তার বাইরের বৃহত্তর এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতেই পরিদৃষ্ট হয়।
[ক্রমশ]
Original in সমকাল