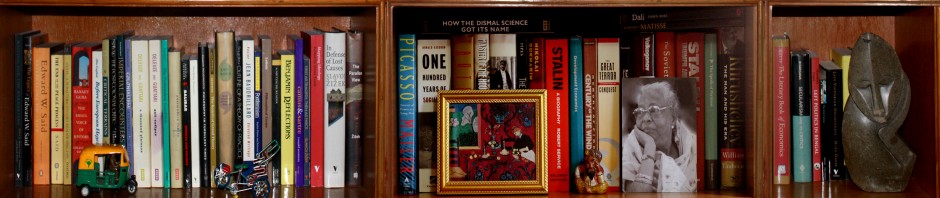পর্ব ::১০
[গত সংখ্যার পর]
মিল সর্বত্রই এই সমস্যাটা এড়িয়ে গেছেন এই বলে যে, বল প্রয়োগ না করার নীতি বা ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল হওয়ার নীতি ‘কেবলমাত্র সভ্য জাতিগণের’ জন্যই প্রয়োজ্য। বল প্রয়োগ বা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো উচিত কেবল অন্ধকারে আটকে থাকা বর্বর অসভ্য জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই। এ নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এখানে যেটা নতুন করে তোলা দরকার তা হলো, কে বর্বর ও অসভ্য- এটা নির্ধারণ করবে কে? নিশ্চয় সভ্য জাতিরই মহাত্মনেরা যারা আলোকিত মানুষ, বিদ্যা-বুদ্ধিতে এগিয়ে? এ ধরনের নিয়ম করার ক্ষেত্রে মিল অবশ্য কোনো নৈতিক সমস্যা দেখেননি। অন্যত্র এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, অপরিণত শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ লোকের ক্ষেত্রে কিসে তাদের ভালো, সেটা তাদের কাছে ছেড়ে দেওয়া চলে না। সে জন্য কিছুটা জবরদস্তি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে বৈকি। একই কথা খাটে বন্য জাতি বা স্যাভেজ, আধা-বর্বর ও বর্বর জাতি এবং জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। আফ্রিকার বেশির ভাগই প্রথমোক্ত গ্রুপে পড়ে। ভারতবর্ষ পড়ে মূলত বর্বর জাতির গ্রুপে (দু’একবার অবশ্য মিল আধা-বর্বর বা সেমি-বারবারাস অভিধাও ব্যবহার করেছেন ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে)। সভ্য ও বর্বর এবং বর্বরের মধ্যে বন্য, আধা-বর্বর ও বর্বর- এ রকম জনমিতিক শ্রেণিবিন্যাস করে একই ক্ষেত্রে ইউরোপ ও উপনিবেশের ক্ষেত্রে দুই ধরনের নীতির প্রয়োগকে মিল যুক্তিসিদ্ধ করে তুলেছেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে নিয়মের কল্পনা যেমন তাকে করতে হয়েছে, তেমনি তাকে নিয়মের ব্যত্যয়ের কল্পনাও তাকে করতে হয়েছে উপনিবেশ-সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে। যা আদিতে সৃষ্ট হয়েছিল ব্যত্যয়ের নীতি হিসেবে (‘ইউরোপে যা চলবে উপনিবেশে তা চলবে না’) উনিশ শতকের হিতবাদী লিবারেলদের লেখায়। তা-ই পরবর্তীকালে পুনর্জন্ম পেয়ে চলেছে তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে হালের লিবারেলদের উৎকণ্ঠাময় আলোচনায় (‘ইউরোপে যা চলবে বৈরী তৃতীয় বিশ্বে তা চলবে না’)।
মিলের অবস্থানে এই দ্বিত্বতা বঙ্কিমের চোখ এড়ায়নি। প্রবন্ধের শেষটায় তিনি মন্তব্য করেছেন- ‘পরিণামে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, মিল স্বস্বভাবানুবর্তিতা বিষয়ে যে কোন বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সভ্যতম জাতিগণেরই উপযোগী, এই কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য কিনা, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ হইতে পারে। আর মিলের মতই যে সর্ববাদী সম্মত, এ কথাও বলা যায় না; অন্য কি, লেখক নিজেই এই প্রবন্ধের সকল কথা আন্তরিক অবলম্বন করেন না। কিন্তু মিল অতি প্রধান ব্যক্তি, তাহার মত সর্বসাধারণের গোচর হইলে কোন প্রকার অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।’ গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে ‘কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স’জনিত কারণে বেশ কিছুটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর থেকে আঁচ করা যায়। তারপরও বলতে হয় যে, মিলের অসভ্য জাতির ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের তত্ত্বটি বঙ্কিম সুবিধামত কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রথমত, আর্যজাতি উত্থানের জন্য বাহুবলের (ও বাক্যবল) ব্যবহার দরকার হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাহুবলের জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার প্রেরণাও তিনি লাভ করেছিলেন মিল থেকে। সংগঠনের জন্য দরকার চরিত্র, আর চরিত্রের জন্য চাই উন্নত প্রশিক্ষণ, যার বিবরণী পাই ‘দেবী চৌধুরানী’তে।
বিবরণীটি চমকপ্রদ। ভবানী পাঠক প্রফুল্লের চরিত্র নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী বাহুবল-তত্ত্বের জন্য সংগঠন ও চরিত্র নির্মাণকে বঙ্কিম এভাবে দেখেছিলেন :’প্রথম বৎসরে তুলার তোষকে বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিশ, বিচালির বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত। প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।…প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।…এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।’
মিলের সাম্যচিন্তা বঙ্কিমকে প্রভাবিত করেছিল। ‘সাম্য’ প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রাকৃতিক বৈষম্য ও অপ্রাকৃত বৈষম্যের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে কেউ অধিকতর বলশালী, কেউ বেশি বুদ্ধিমান, কেউ অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, এসব সাম্যের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। এখানে প্রধান বিবেচনা হচ্ছে ‘অপ্রাকৃত বৈষম্য’, যার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণে-শূদ্রে বর্ণজনিত বৈষম্য, দেশি-বিদেশি শক্তির মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, অথবা ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার সম্পদজনিত বৈষম্য। এই শেষোক্ত অর্থগত বৈষম্যই সবচেয়ে গুরুতর। বঙ্কিম বলেছেন, ‘সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃত বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।’ পৃথিবীর যে দেশেই এই বৈষম্যের আধিক্য ঘটেছে সে দেশেই শ্রীবৃদ্ধির গতি শ্নথ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সের প্রসঙ্গ টেনে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন যে ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার কারণেই সেখানে সাম্যবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল :’পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সের দেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য, অপরিশুদ্ধ রাজশাসন-প্রণালীজনিত। রুশোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসন প্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানসশিষ্যরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।’
‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে দেশের কৃষি ব্যবস্থার যে চিত্র বঙ্কিম এঁকেছিলেন, সেখানেও কদর্য বৈষম্যের নিদারুণ ছাপ পাওয়া যায়। তিনিও কি নিজেকে সাম্যের প্রচারক হিসেবে, রুশোর মতোই সাম্যবাদী চিন্তক হিসেবে দেখেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে? সেই জন্যই কি ‘ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব’ সম্পর্কে মিলের মতের উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন :’যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার জন্য কোনো দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিয়াছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।’
প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথা যিনি বলতে পারেন, তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী কী করে হতে পারলেন? পরাণ মণ্ডল বলার সাথে সাথে তার কি হাসিম শেখ-এর কথাও মনে পড়ল না? অপ্রাকৃত বৈষম্য নিয়ে বলতে গিয়ে যখন ব্রাহ্মণ-শূদ্র বা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের প্রসঙ্গ তুললেন, তখন কি একবার তার মনে পড়ল না হিন্দু ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাথে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্যের কথা? শ্রেণি-প্রশ্নে যিনি এত তীক্ষষ্ট ও উদার অবস্থান গ্রহণ করেন (যার পরিচয় আমরা পেয়েছি ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ ও ‘সাম্য’ রচনায়) তার মন কেন আত্মসত্তার পরিচয় প্রশ্নে তথা আইডেনটিটির প্রশ্নে এসে এতটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে? ভারতবর্ষের জাতি বা মহাজাতি গড়ার প্রকল্পে নিয়োজিত হয়ে তিনি কেন বারবার হিন্দু-ইতিহাসের থেকেই প্রেরণা নিতে তৎপর হন? শুধু তা-ই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে দৃষ্টিকটূ রকমের অসহিষ্ণু মনে হয় তাকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করার ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক ও শ্রেণি-সমস্যা আলোচনার ক্ষেত্রে যিনি এত উদারনৈতিক, নারী-সমস্যা ও হিন্দু-সমাজের ভেতরকার জাত-পাতের সমস্যার আলোচনায় যিনি এতটাই মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির; মুসলমান প্রসঙ্গ এলে তিনি ততটাই অনমনীয়, অশোধনযোগ্যভাবে অসংবেদনশীল; তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শ্রেণি-রাজনীতিকে তাই ছাপিয়ে উঠে আইডেনটিটির রাজনীতি- বঙ্কিমের সত্তার দ্বিত্বতা বা দ্বিখণ্ডন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ফাটল বা দ্বিখণ্ডিত সত্তাকেই তুলে ধরে। এর ফল পরিণাম তো বঙ্কিমের মতো তীক্ষষ্টধী মানুষের কাছে অধরা থাকার কথা নয়। এর কিছু আভাস পাই বঙ্কিমের নিজের লেখাতেই। তাতে আমাদের মনোকষ্ট আরও বেড়ে যায়।
‘সীতারাম’ উপন্যাসকেই আমি এই সূত্রে বেছে নিতে চাই। তার আগে ‘আনন্দমঠ’ নিয়ে দু’একটি কথা বলা দরকার। আনন্দমঠে মুসলমান শাসনের অবসানের পর ইংরেজরাই ভারতবর্ষের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছিল। অর্থাৎ আনন্দমঠে হিন্দুর জয় হলো বটে, কিন্তু দেশে হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পেল না। এর থেকে বঙ্কিম-জীবনীকার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানেরা অত্যাচারী মুসলমান রাজশক্তিকে পরাভূত করেছে ঠিক- কিন্তু সেই হিন্দু সন্তান সম্প্রদায়কে দেশ শাসনের অধিকার’ দেওয়া হয়নি। ইংরেজ রাজত্বকে আবশ্যক বলে ভেবেছেন বঙ্কিম। কেননা, প্রচলিত হিন্দু সমাজে নানা অনাচার ঢুকে পড়েছে, যা তাড়ানোর জন্য হলেও ইংরেজকে মিত্র হিসাবে চাই তার :’ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। …তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা আর্য ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত আর্য ধর্ম- ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দু ধর্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে।’ এ জন্যই বঙ্কিম আনন্দমঠ রচনার প্রারম্ভেই ঠিক করে নিয়েছেন- ‘ইংরেজকে রাজা করিব।’ এই ব্যাখ্যা ঠিক হলে বলতে হয়, বঙ্কিম মিলের পূর্ব-কথিত ‘অপরিণত শৈশব’-এর কালতত্ত্ব এবং ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজের অধীনে থাকার ‘আবশ্যকীয় শিক্ষানবিশী পর্ব’র যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন। এর একটি সম্ভাব্য কারণ, শেষ জীবনে বঙ্কিম ক্রমশ হিন্দু ধর্মাশ্রিত আদর্শকে বড় করে দেখেছিলেন। ‘ধর্মতত্ত্ব’তে তিনি দেশপ্রেমকে ‘শ্রেষ্ঠ ধর্ম’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ‘ইউরোপ পুনঃদর্শন’ বইয়ে তপন রায় চৌধুরী বলেছেন. ‘তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শবাদে পরিবর্তনে-কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর আস্তিক্যবাদে উত্তরণ এবং পুরুষাণুক্রমিক ধর্মমতে প্রত্যাবর্তনের ফলে’ তিনি অন্তত একটি বিষয়ে ইউরোপের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তাকে মুসলমান সম্প্রদায়কে আরও দূরে সরিয়ে দিতে হয়েছিল।
অমিত্রসূদন আরও যুক্তি দেখিয়েছেন, যেহেতু মন্বন্তরের পটভূমিতে আনন্দমঠ রচিত এবং যেহেতু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে (১১৭৬-৭৮ বঙ্গাব্দকালে) অরাজক শাসন বিরাজ করছিল, এবং যেহেতু রাজকার্যে তখন পর্যন্ত মুসলমান শাসকদেরই ‘প্রধান’ দায়-দায়িত্ব ছিল, তাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল এবং সে কারণেই উপন্যাসটিতে মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য স্থানে স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিল- কল্পনা করা দুরূহ। বস্তুত বাংলায় তখন কোম্পানির অরাজক শাসনের বিস্তার হয়েছিল, যার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলমান রাজশক্তির একাংশের সাহায্য (বাংলার সুবেদার তখন রেজা খাঁ) নিয়েছিল কোম্পানির স্থানীয় প্রভুরা। বঙ্কিম লিখেছেন, ‘মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে।’ এখানে ঐতিহাসিক ত্রুটি আছে। মীরজাফর ১৭৬৫ সালেই মারা যান। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য হেস্টিংসকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে বঙ্কিম প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরেছেন :’এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। …তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত…বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।’ আসল ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতে, মুসলমান রাজন্যবর্গের হাতে নয়, আর দুর্ভিক্ষে এক-তৃতীয়াংশ বাংলার মানুষ যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন তার অন্তত :অর্ধেক ভাগই ছিল বাংলার দরিদ্র মুসলমান চাষিরা। বিদ্রোহীদের মধ্যে সন্ন্যাসী ও ফকির উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন।
[ক্রমশ]
Original in সমকাল