চলতি বাজেট জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত করবে
Author Archives: drbinayaksen
রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা
পর্ব : ০৫[পূর্বে প্রকাশের পর]

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাহলে কী করতে পারেন? তিনি বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে। নিজের ক্রিয়াকলাপের কর্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে। সে ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারবে না। নিম্নবর্গ কখনোই গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ। … আসলে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার মহলে যে-ভূমিকায় ‘সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ’ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল, সেটা হয় এক ধরনের র্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস কিংবা ‘হিস্ট্রি ফ্রম বিলো’– তল থেকে দেখা ইতিহাস। সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে এই ধরনের ইতিহাস লেখার খুব চল হয়েছিল। ক্রিস্টোফার হিল, এডওয়ার্ড টমসন, এরিক হব্সবম প্রভৃতি ইংরেজ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকের ধারা অনুসরণ করে অনেকেই তখন ইউরোপের পুঁজিবাদ আর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে যাওয়া বিস্মৃত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিন্নতর জীবনযাত্রার কথা লিখছিলেন। এই ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’ প্রধানত ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, মতাদর্শ, স্মৃতি খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। … ‘সাবল্টার্ন স্টাডিজ’-এর লেখকরাও যে ইউরোপের র্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসের কাজ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ তফাত ছিল। … ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে ‘তল থেকে দেখা’ ইতিহাসকে কিন্তু এ রকম কোনো ছকের ভেতরে বেঁধে রাখা কঠিন ছিল। ভারতে পুঁজিবাদী আধুনিকতার বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে গল্পের শেষটা অত নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়নি। বিশ্বের অন্যত্র যা ঘটেছে, ভারতে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এই ফর্মুলাটা যদি মাথায় চেপে বসে না থাকে, তাহলে ‘তল থেকে দেখা’ ভারতীয় ইতিহাসের লেখক সহজেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর গবেষণার উপাদান থেকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক প্রশ্ন তোলার সুযোগ খোলা রয়েছে। … লিবারেল জাতীয়তাবাদ এবং মার্ক্সবাদ– দুই ধরনের ইতিহাস রচনার প্রতিষ্ঠিত ছক সম্বন্ধেই ‘সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ’-এর লেখকদের মনে সংশয় ছিল। র্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসের চর্চায় নেমে তাঁরা তাঁদের বর্ণনাকে কোনো নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিণতি আধুনিক সমাজের কোনো নির্দিষ্ট ও পরিচিত ধারণার বাস্তবায়ন, এই কাহিনিসূত্রটি তাঁরা বারবারই অস্বীকার করতে লাগলেন তাঁদের লেখায়। তাই ‘তল থেকে দেখা’ ইতিহাস হিসেবেও ‘সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ’-এর লেখা বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল ইতিহাসচর্চার মহলে।” ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’ (History from Below) এবং ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ (Subaltern History) এই দুই ধারার মধ্যে তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছু পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। প্রথমত, এ দুইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে পটভূমিগত (Context) পার্থক্য। ‘তল দেখা ইতিহাস’ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল ইউরোপীয় বা উত্তর-আমেরিকার ‘আধুনিক’ অভিজ্ঞতার ওপরে। নিম্নবর্গের ইতিহাসের বিষয় হচ্ছে উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশ-উত্তর অভিজ্ঞতা। একের অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে মেলার কথা নয়: একটি যদি হয় সরলরেখা, অন্যটি তাহলে বক্ররেখা (crooked line)। ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামো আমাদেরকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করায়, যার সাথে ইউরোপ-আমেরিকার অভিজ্ঞতার কোনো তুলনাই হয় না। সেজন্যই কাছাকাছি শোনালেও ‘নিম্নবর্গের’ ইতিহাসচর্চা ও ‘তল থেকে দেখা’ ইতিহাসচর্চা ধারণাগতভাবে ভিন্ন হতে বাধ্য। এ দুই ধারার ইতিহাসচর্চার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য অভিনিবেশের বিষয়বস্তুর মধ্যে। ‘তল থেকে দেখা’ ও ‘মার্ক্সবাদী’ ইতিহাসচর্চা উভয়েরই মূল ঝোঁকটা শ্রেণিগত বিশ্লেষণের দিকে। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুধু শ্রেণি নয়, তার নজর পড়ে অন্যান্য শোষণ-বঞ্চনার প্রতিও। নারীদের একান্ত নিজস্ব সংগ্রাম নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি যখন পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা যুদ্ধ করেছে তখনও তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে আনার আলাদা গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। অধস্তনতার বেদনাকে যেমন আঁকতে হবে, তেমনি তুলে আনতে হবে তার স্ব-নিয়ন্ত্রণপ্রয়াসী (Agency) আচরণ। সেটা শুধু সুলতানা রাজিয়া বা ঝাঁসির রানীর ক্ষেত্রে নয়, ‘অশনি সংকেত’-এর অনঙ্গ-বৌ বা ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’র জয়গুনের ক্ষেত্রেও। ‘ইতিহাসের ক্ষুদ্র আওয়াজ’ (The Small Voice of History) প্রবন্ধে রণজিৎ গুহ বলেছেন যে পূর্বের ঐতিহাসিক বিবরণীগুলো যেমন ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক (statist), তেমনি ছিল পুরুষকেন্দ্রিক। নেতৃত্ব, পার্টি, সংগঠন শব্দগুলোই ছিল বড় বেশি পুরুষঘেঁষা। এসব গল্পে নারীদের কোনো স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ছিল না। নারীরা ছিল নিষ্ক্রিয় কর্তা, উদ্যমহীন ও ইতিহাসের বাসযাত্রায় চালকের আসন থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে বসা নীরব যাত্রীদের মতো। নিম্নবর্গের ইতিহাস এভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে নারীকে দেখবে না। রণজিৎ গুহ লিখেছেন : “In a new historical account this metaphysical view will clash with the idea that women were agents rather than instruments of the movement which was itself constituted by their participation. This will inevitably destroy the image of women as passive beneficiaries of a struggle for ‘equal rights’ waged by others on their behalf.” নারীদের ‘মুক্ত করতে গিয়ে’ নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক অপরাপর অধস্তন ও শোষিত ‘অপর জনগোষ্ঠীদের’ প্রতিও নজর দেবেন। এর মধ্যে প্রথমেই চলে আসে ‘নীচু জাত ও সম্প্রদায়ের’ প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষে এই জাতপাতের ফারাক এখনও তীব্র ও সজীব; ইতিহাসে এই ফারাক আরও বেশি তীব্র ও জীবন্ত। এমনকি ‘আধুনিক’ ভোটযুদ্ধ ও নির্বাচনী ইতিহাসে উঁচু জাত বনাম নীচু জাতের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মেরূকরণ কোনো শ্রেণি আলোচনা থেকে কম চিত্তাকর্ষক নয়। এরই সাথে যুক্ত করতে হয় স্বজাতি-ভিন্ন জাতি ব্যবধানের কথা। এককথায়, প্রতিটি বর্ণেরই নিজস্ব ব্যর্থতা ও উত্থানের কাহিনি রচনা করবে নিম্নবর্গের ইতিহাস। সব শেষে বলতে হবে আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, চেহারা-সুরতে ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংগ্রামের কথা। সংখ্যায় ক্ষুদ্র বলেই তাদেরকে আমাদের চোখে পড়ে না। প্রায় অদৃশ্য, পাহাড়ে-জঙ্গলে থাকা, আদিবাসী নৃগোষ্ঠীকে তো একেবারেই চোখে পড়ে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস এই শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষভাবে আলো ফেলবে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন : “I feel that women’s voice, once it is heard, will activate and make audible the other small voices as well … I want historiography to push the logic of its revision to a point where the very idea of instrumentality, the last refuge of elitism, will be interrogated and re-assessed not only with regard to women but all participants.” বর্ণ, জাত বা নারী এসব সামাজিক বর্গের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ‘শ্রেণি’ বিষয়টি নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। পার্থক্য এই যে, মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের চর্চায় শ্রেণির প্রতি যেমন একটা কেন্দ্রীয় মনোযোগ থাকে, সেরকমটা সাব–অল্টার্ন স্টাডিজের বেলায় নয়। তারা বরং উৎসাহী শ্রেণি/বর্ণ, শ্রেণি/জাত, শ্রেণি/নারী এই যুগলের মধ্যে আড়াআড়ি বিভক্তি (intersectionality)-কে ধরার জন্য। যেমন, ডোম সম্প্রদায় অর্থনৈতিক বিচারেও ‘দীনের হতে দীন’; সামাজিক বিচারেও ‘সবার অধম’; প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কলঙ্কচিহ্ন বয়ে বেড়াতে হয় তাদের সারাজীবন। কোন ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতিকে ‘অশুচি’ বা অপবিত্র জ্ঞান করা হয় ‘ভদ্রসমাজে’। তদুপরি তাদেরকে গণ্য করা হয় (বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসকদের বর্ণনায়) অপরাধপ্রবণ উপজাতি বা ‘ক্রিমিনাল ট্রাইব’ হিসেবে। অনেকটা ইউরোপের রোমা ‘জিপসি’ সম্প্রদায়ের মতো। এই ইন্টারসেকশনালিটিকে রণজিৎ গুহ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বের বরাত দিয়ে : ‘ডোম জন্মায় অড়হর খেতে, ছোটবেলা থেকেই সে চুরি করতে শেখে। জীবনের প্রথম থেকেই সে পতিতের মতো ঘুরে বেড়ায়। মাথার ওপর ছাদ ছাড়াই সে বাঁচে, থাকে না পরের দিনের অন্নের কোনো সংস্থান। পুলিশের তাড়নায় জীবনভর সে পালিয়ে বেড়ায় এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে। গ্রাম থেকে সে সদাই বহিষ্কৃত। … সে আছে হিন্দু ধর্মের নাগালের বাইরে। … সভ্যতার অগ্রগতি তাকে শুধু আরও অবনমনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে।’ উপরের বর্ণনায় আমরা ‘ইন্টারসেকশনালিটির’ প্রায় সবগুলো উপাদান পাই। এই অচ্ছুৎ মানুষদের ‘প্রান্তিকতাকে’ শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থান বিচার করে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। এই কথাটা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা জোরেশোরে বলবেন। দীপেশ চক্রবর্তীর প্রথম বই ‘রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি’-কে ইন্টারসেকশনালিটি ধারণার একটি আদি-প্রয়োগ হিসেবে দেখা চলে। শ্রমিক হলেই তা সবচেয়ে ‘প্রগতিশীল’ শ্রেণি এই ধারণা মার্ক্সীয় ধারায় একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস হিসেবে কাজ করে আসছে। তাই যদি হবে তাহলে শ্রমিক এলাকায় সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দাঙ্গা বাধে কী করে? মার্ক্সবাদীরা এ ক্ষেত্রে ‘ক্লাস-ফর-ইটসেলফ’ (সক্রিয় শ্রেণি) বনাম ‘ক্লাস-ইন-ইটসেলফ’ (নিষ্ক্রিয় শ্রেণি) বলে এই ধাঁধার মীমাংসা করার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাতে করে শ্রেণির মধ্যে ধর্মভেদ ও জাতপাতের সমস্যার সুরাহা হয় না। শিল্প-শ্রমিক শ্রেণি অন্যের শৃঙ্খল মোচন করতে এগিয়ে আসেনি, এমনকি নিজের শৃঙ্খলও মোচন করেনি– কিছু স্মরণীয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে। অর্থাৎ, সামাজিক মুক্তির বৃহত্তর পরিসরে ‘প্রলেতারিয়েত’ একটি বিমূর্ত রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে থেকে গেছে। এককথায়, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক শ্রমিক শ্রেণি সম্পর্কে পূর্বানুমানভিত্তিক কোনো মহিমান্বিত ধারণা অনুসরণ করে অগ্রসর হবেন না। এটা শুধু শ্রমিক শ্রেণি নয়, সব অর্থনৈতিক শ্রেণির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, মার্ক্সবাদী সাহিত্যের একটি প্রধান প্রবণতা ছিল কৃষক জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক শ্রেণির তুলনায় তুলনামূলক কম প্রগতিশীল বা অনগ্রসর সামাজিক শ্রেণি হিসেবে ভাবা। চীন-ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতার পরে এই প্রবণতা এখন কমে এসেছে, কিন্তু তার পরও আমাদের দেশে বিভিন্ন বাম দলের দলিলে-ঘোষণাপত্রে ‘মধ্যকৃষক হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র’ ধরনের আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষকদের দোষ যে কৃষক সর্বহারা নয়; জমির প্রতি তার ক্ষুধা পূর্বাপর– এমনকি ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। এককথায়, কৃষককে ঠিক বিশ্বাস করা চলে না জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে। অথচ আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা গেছে যে, কৃষকরাও শ্রমিকের চাইতে কম যায়নি আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে। ১৯৫২ সালের ছাত্র-আন্দোলনের ছাত্ররা ছিল কৃষকেরই সন্তান; ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সাধারণ মুক্তিসেনাদের অধিকাংশই ছিল গাঁওগেরামের কৃষক। ১৯৬৯ সালে আয়ুবশাহির পতনের পেছনে যেমন ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল চল্লিশের শেষার্ধে কৃষক-আদিবাসীদের তেভাগা-টংক-নানকার আন্দোলন; যা সাতচল্লিশের পর মুসলিম লীগ সরকারের ভিত কিছুটা হলেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কোন শ্রেণি কখন বিদ্রোহ করবে বা আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল হবে, সেটা আগে থেকে বলে দেওয়ার মতো গল্প অনুসারে পরিচালিত হয় না। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিদ্রোহ তো শুধু শ্রেণি-কাঠামো দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায় না– এ কথা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা বলবেন। এর চেয়েও বড় কথা, কোনো একটি আন্দোলনের নাম বা ব্যানার, তার আপাত রাজনৈতিক আদর্শ বা সংগঠনের পরিচিতি যা-ই হোক না কেন, তাতে অংশগ্রহণকারী সবাই একই আদর্শ বা সংগঠনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হন না। অংশগ্রহণকারী সবারই যার যার নিজস্ব কারণ থাকে– সেটা ব্যানার বা সংগঠনের আদর্শের সাথে মিলতেও পারে, না-ও পারে। এই যার যার ‘নিজস্ব কারণ’ বের করার দায়িত্ব নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের। একটি উদাহরণ দেব এ সূত্রে। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে নানা শ্রেণির মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। স্বৈরাচার-বিরোধিতা ছিল প্রকাশ্য রাজনৈতিক আদর্শ– ব্যানারে ব্যানারে সে কথাই লেখা ছিল। সেসময় পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর পিঠে লেখা ছিল ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’। আমরা কি হলফ করে জানি যে নূর হোসেন সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের জন্যই সেদিন সেই মিছিলে গিয়েছিলেন? আমার এখনও মনে পড়ে যেদিন এরশাদ পদত্যাগ করলেন, সেদিন ঢাকার তোপখানা রোডের মোড়ের কাছে একটি লোক বিড়বিড় করছিল– ‘আজ কেমন স্বাধীন স্বাধীন লাগছে!’ কেউ কি জানে কেন সে এই কথা বলেছিল? যেন একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি চারপাশে বিরাজ করছিল এবং এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে আমরা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু এটা আমার ইন্টারপ্রিটেশন; সেই লোকটি স্বাধীনতার অন্য কোনো অর্থ তৈরি করে থাকলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই কথাটিই বলার চেষ্টা করেছিলেন শামসুর রাহমান তাঁর ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় : ‘এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?/ এখানে তো নেই বোনাস ভাউচারের খেলা নেই’। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করেই এ কথা বলা, কিন্তু ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সেদিন যারা জড়ো হয়েছিল তাদের প্রাণ একসূত্রে বাঁধা ছিল না। কবিতাটির একটি বড় অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন : ‘এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের? এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিংবা নেই মায়া কোনো গোলটেবিলের, শাসনতন্ত্রের ভেলকিবাজি … আমি দূর পলাশতলীর হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক … আমি চটকলের শ্রমিক, আমি মৃত রমাকান্ত-কামারের নয়ন পুত্তলি, আমি মাটিলেপা উঠোনের উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী, আমি তাঁতি সঙ্গীহীন … আমি রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানি, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া, আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ, আমি নব্য কালের লেখক, আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী নিত্য করে আসা-যাওয়া …’ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-চর্চায় সব আন্দোলন-সংগ্রামকেই ‘একসূত্রে বাঁধা’ হিসেবে দেখা হয়। সেসব আন্দোলন-সংগ্রামে যোগদানের আপন আপন কারণ খুঁজে বের করার তাগিদ নেই সেখানে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক সেই ঐক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখবেন; সমগ্রের মধ্যে ভগ্নাংশকে দেখবেন; প্রতিটি কণ্ঠস্বরকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে শনাক্ত করবেন। এই মর্মে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (আরেকজন দিকপাল সাব-অল্টার্ন ঐতিহাসিক) লিখেছেন: ‘ভগ্নাংশের সমর্থনে : দাঙ্গা নিয়ে কী লেখা যায়?’ পার্থ চ্যাটার্জী লিখেছেন আরও স্পষ্ট করে : ‘নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্রাগমেন্টস’; এর মর্মার্থ হলো– জাতি-রাষ্ট্রের নানা অংশ, গোষ্ঠী, শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার তারা আলাদা ধারা হিসেবেই শেষাবধি থেকে গেছে। একটি জাতিতে তারা মিলতে পারে নাই। ‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে’– সেই মহামিলন রাজনৈতিক ভাষণে-দাবিতে-সংবিধানে শুধু থেকে গেছে; বাস্তবে তা হয় নাই। কেন হয় নাই সে প্রশ্নের সওয়াল-জবাব নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা করবেন। অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের বিশেষ মনোযোগ কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্বুদ্ধ? সেটা কি বস্তুবাদী নাকি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি? হিউম্যানিজম নাকি পপুলিজম? মার্ক্সবাদ নাকি ‘ডিসিডেন্ট লেফট’? নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার পেছনে কোন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে, সেটা জানা জরুরি বৈকি। এ বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তী এক জায়গায় লিখেছেন : ‘১৮৯৭ সালে বোম্বাইয়ের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ সরকারের প্লেগ-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তার ইতিহাস আজ কেন লিখব? নিছক নিম্নবর্গের বিরোধিতার ইতিহাস লিখতে চাই বলে? সেটা তো পপুলিজম। মানুষ হাজারো বাধার মধ্যেও তার সংগ্রামী সত্তাকে জিইয়ে রাখে, এই কথাটার পুনঃপ্রচার করতে চাই বলে? সেটা তো হিউম্যানিজম। এর বাইরেও তো একটি ইতিহাস আছে …’ এর বাইরের ইতিহাস– যাকে ‘অন্য ইতিহাস’ বলেছি এই অধ্যায়ের শুরুতে– তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী। ব্যাখ্যাটি স্পষ্টতই মার্ক্সের ‘রাষ্ট্রের ক্রম-বিলুপ্তি’ (withering away of the state) তত্ত্বের দ্বারা অন্তত আংশিকভাবে প্রভাবিত। হয়তো এই চিন্তার মধ্যে ‘এনার্কিস্ট’ ধ্যান-ধারণাও কাজ করেছে। দীপেশ লিখেছেন : ‘রাষ্ট্রের ভিত্তি– লেনিন যেমন বলেছিলেন– সংগঠিত হিংসায়। হিংসার মাধ্যমেই তার জন্ম। নিজেকে বৈধ প্রমাণ করতে তাঁর কতগুলো ‘কল্যাণকর’ মতাদর্শের সাহায্য নিতে হয়। আবার এগুলোই তাঁর হাতে অস্ত্রবিশেষ। অথচ গান্ধীবাদীভাবেই ভাবুন বা মার্ক্সবাদীভাবেই ভাবুন, শেষ বিচারে মানুষের মুক্তি রাষ্ট্রের অবলুপ্তিতে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে, তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার চরিত্র বোঝা দরকার। এবং তেমনি বোঝা প্রয়োজন ইতিহাসে রাষ্ট্র-বিরোধিতার সূত্রগুলো কোথায়, কারণ একদিন আবার মানুষের মুক্তির কাহিনির সূত্রপাত সেইসব জায়গা থেকে করতে হবে।’ নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্রমেই মহাপরাক্রমশালী হয়ে ওঠা ভূমিকার বিরোধিতা একটি বড় দিক রণজিৎ গুহ ও তাঁর অনুপ্রাণিত সাব-অল্টার্ন স্কুলের ঐতিহাসিকদের দর্শনে। তার মানে এই নয় যে রণজিৎ গুহ প্রথাগত মার্ক্সবাদের যুক্তি বিন্যাসের মধ্যেই আটকে থাকতে চেয়েছিলেন। ‘বামপন্থি’ তিনি (এবং তাঁর সহযোগীরা) অবশ্যই, তবে তাঁরা ভিন্নমতাবলম্বী বাম বা ‘ডিসিডেন্ট লেফট’ গোত্রের। রণজিৎ নিজে একসময় কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন চল্লিশের দশকে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে। সেসময় তিনি চীনসহ নানা পূর্ব ইউরোপীয় দেশে সিপিআইয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রতিনিধি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্বচক্ষে দেখেছেন নতুন সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণের প্রচেষ্টা এসব দেশে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে সিপিআইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর থেকে অফিসিয়াল পার্টি লাইনের বাইরের লোক ছিলেন তিনি– বামপন্থিদের মধ্যে অনেকটাই অপাঙ্ক্তেয়। সুতরাং ডিসিডেন্ট লেফট-ই বলব তাঁকে এবং তাঁর অনুপ্রাণিত অন্য ইতিহাসের সহযোগীদের। যদিও তাঁদের ‘ডিসিডেন্ট’ হয়ে ওঠা ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কাকতালীয়ভাবে বলি, রণজিতের প্রায় একই সময়ে মিশেল ফুকোও ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আগ্রাসন তাঁর ওপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বামপন্থি বলয়ে থাকলেও আর কখনোই পার্টির বলয়ে তিনি ফিরে যাননি। এ রকম ঘটেছিল ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত আগ্রাসনের পরেও। জাঁক দেরিদা ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির বলয় থেকে এই সময়ে বেরিয়ে আসেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সাল এই কুড়ি বছর রণজিৎ গুহের একান্ত নিরিবিলি গবেষণার জীবন। ফরাসি জানেন তিনি, ফলে ইংরেজিতে বার হবার আগেই ক্লদ-লেভি স্ট্রস, রোলা বার্থ, মিশেল ফুকো, জাঁক দেরিদা প্রমুখের লেখার সাথে পরিচিত ছিলেন। মার্ক্সবাদের অনুশীলন তো পূর্বাপর ছিলই। সাথে সাথে সংস্কৃত ভাষাটাও রপ্ত করেছিলেন তরুণ বয়সেই (রণজিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবপ্রসাদ গুহ ছিলেন পালি ভাষার ওপরে একজন ‘অথরিটি’)। সাথে ছিল সাহিত্য পাঠের বিপুল প্রস্তুতি। এসবই তাঁকে সাহায্য করেছিল নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার প্রকল্প সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গড়ে তুলতে।
[ক্রমশ]
রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা
পর্ব : ০৪ [পূর্বে প্রকাশের পর]

তপন রায়চৌধুরী গুনে দেখিয়েছেন যে বরিশালের কিছু এলাকায় জমিদার ও প্রকৃত কৃষক-প্রজার মাঝে ৩২-স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকে। প্রাগ-ব্রিটিশ পর্বে পুরোনো জমিদার-পুরোনো রায়তের মধ্যে (ফ্রান্সিসের ভাষায়) ‘স্বাভাবিক স্বার্থ ও সম্পর্কের যে পারস্পরিক বন্ধন ছিল’ তা প্রায় সর্বাংশে ধসে পড়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর নতুন পরিস্থিতিতে। কেন এমন হলো সে প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর– ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও ইউরোপের পুঁজিবাদ গোড়া থেকেই ভিন্ন নিয়ম মেনে অগ্রসর হচ্ছিল। একেই পার্থ চ্যাটার্জী পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন– ‘কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স’। মেট্টোপলির জন্য যে নিয়ম খাটে, কলোনির জন্য সে নিয়ম খাটে না। উপনিবেশের পরিস্থিতিতে অবাধ ধনতন্ত্রের যৌক্তিক নিয়ম কার্যকর করা যায় না। সেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাও সহজে চালু করা যায় না। রাজশক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ আর সব বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। সেখানে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়েও কৃষকের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থেaর মধ্যে স্থান পায় না। অন্তত বহুকাল পর্যন্ত পায়নি। যতদিন পর্যন্ত কৃষকেরা নিজেরাই তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলেছে, অথবা কখনও কখনও নীরবেই প্রতিবাদ করেছে প্রতিদিনের নিঃশব্দ প্রতিরোধে। রণজিৎ গুহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লেখার প্রায় কুড়ি বছর বাদে এ নিয়ে বিস্তৃত লিখবেন। কৃষক-বিদ্রোহ (বিদ্রোহ করা ছাড়া তার আর কী উপায় থাকছে তখন) এই প্রথম বড় আকারে স্থান পাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায়।
৩. অন্য ইতিহাসের নির্মাণ
‘এ রুল অব প্রপার্টি ফর বেঙ্গল’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় ১৯৮২ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অমর্ত্য সেন বলেন যে ‘Ranajit Guha is, arguably, the most creative Indian historian of this century’– সম্ভবত বিশ শতকের ‘সবচেয়ে সৃষ্টিশীল’ ঐতিহাসিক এই উপমহাদেশ থেকে। এই ভূমিকায় অমর্ত্য সেন ‘রুল অব প্রপার্টি’ পর্যায়ের সাথে পরবর্তী কালের ‘সাব-অলটার্ন স্টাডিজ’ পর্যায়ের যৌক্তিক যোগসূত্র খুঁজে বার করেন। উচ্চবর্গের ইতিহাসের সাথে নিম্নবর্গের ইতিহাসের যোগসূত্রটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে এভাবে (উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক)। অমর্ত্য সেন বলছেন:
“Since we often tend to see people in fairly formulaic terms, some would no doubt expect to find in A Rule of Property for Bengal a reflection of the ‘subaltern approach’, with its overarching interest in the role of the non-elite–the so-called subalterns. As I shall presently argue, those looking for such an approach need not be entirely disappointed. There are elements that link A Rule of Property and the Subaltern Studies…
What, then, are these connections? To examine them, it is useful to recapitulate briefly Guha’s motivating concern in initiating the ‘subaltern studies’ :
The historiography of Indian nationalism has for a long time been dominated by elitism–colonialist elitism and bourgeois-nationalist elitism… Both these varieties of elitism share the prejudice that the making of the Indian nation and the development of the consciousness–nationalism–which informed this process were exclusively or predominantly elite achievements.
While A Rule of Property is virtually all about elites–their ideas, their commitments, their hopes, their doubts–it is a view of a well-meaning but ultimately fumbling elite, botching things up at the highest level. In this sense it is not a ‘pro-elite’ book. A Rule of Property brings out the difficulties and the ultimate inadequacy of economic reforms initiated by the elite and influenced by the finest elitist thinking.”
এটা বলার পর অর্মত্য সেন লিখেছেন যে রণজিতের উচ্চবর্গের ব্যর্থতার আলোচনা ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধের আলোচনার মধ্যে একটি গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে গুহ দেখেন যে এই ইতিহাস কেবল অর্থনৈতিক তত্ত্ব, শ্রেণি-তত্ত্ব বা সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ তত্ত্বের নিরিখে বিচার করা যাচ্ছে না। এর সাথে জড়িয়ে গেছে ঔপনিবেশিক (ও আধুনিক) ক্ষমতা-কাঠামোর মৌলিক প্রভাব। এজন্যই ‘শিব গড়তে বাঁদর’ হয়ে যাচ্ছে। ফরাসি বিপ্লবের সামন্তবাদবিরোধী বিশ্বজনীন সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের ধ্যান-ধারণাগুলো দূরবর্তী উপনিবেশে এসে– তা সে ঢাকার বুড়িগঙ্গাই হোক, আর কলকাতার হুগলি নদীই হোক– সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চেহারা নিচ্ছে। সুস্থ নির্মাণের পরিকল্পনাও একটি অসুস্থ/বিকৃত নির্মাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
Guha explains the botched job in the following terms: “…a typically bourgeois form of knowledge was bent backwards to adjust itself to the relations of power in a ‘semi-feudal society.’ Through the relevance of ‘power relations’ we get into a territory in which the subaltern studies have taken great interest.”
‘রুল অব প্রপার্টিস’ বইয়ে ফ্রান্সিস সাহেব ও অন্যদের আলোচনা করতে গিয়ে রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন যে কী করে একটা আপাতদৃষ্টিতে ‘ভালো’ বুর্জোয়া আইডিয়া ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে এসে নিজেরই বিরুদ্ধে গিয়ে আধা-সামন্তবাদী ক্ষমতার সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এই অর্থে বইটি কোনো এলিটকেন্দ্রিক আলোচনার বই নয়: এটি এলিট বা উচ্চবর্গের জ্ঞানমার্গ (Episteme) ও তার রাজনীতিরই নিকট সমালোচনা। এবং এই সূত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনার দরকার ছিল নিম্নবর্গের আলোচনা শুরু করার জন্য। কেননা, উচ্চবর্গের রাজনীতির ব্যর্থতাই নিম্নবর্গকে ইতিহাসের প্রান্তস্থল থেকে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে। রণজিৎ উচ্চবর্গের ব্যর্থতার আলোচনা করতে গিয়েই একপর্যায়ে নিম্নবর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ার তাগিদ অনুভব করেছেন।
এই পর্যায়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কী নয় সে বিষয়টি আগেভাগে পরিষ্কার করা ভালো। রণজিৎ গুহ তার পূর্বে উদ্ধৃত অংশে দুই ধরনের ইতিহাসচর্চার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে– ঔপনিবেশিক এলিটকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার ধারা। যেন ম্যাকলে সাহেব এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে কথা ভাবলেন বা জন স্টুয়ার্ট মিল কোম্পানির নীতি নিয়ে যে বিবৃতি দিলেন তার সুবাদেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অথবা ঔপনিবেশিক ভারতের বড়লাট হয়ে কোন নির্দিষ্ট পর্বে যে বিশেষ ইংরেজ রাজকর্মচারী এ দেশ শাসন করতে এলেন তার ওপরেই যেন নির্ভর করছে এ দেশের ইতিহাসের ধারা। অপর ইতিহাসচর্চার ধারাটিও খুবই প্রচলিত: সেটি হচ্ছে (বুর্জোয়া) জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা। এই মতে, দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী যবে থেকে সাহেব-সুবোদের বেশ ছেড়ে কৃষকের বেশ ধরলেন– যবে থেকে তিনি ‘মহাত্মা’ হলেন– তখন থেকেই গণজাগরণ দেখা দিল এ ভূখণ্ডে। অথবা সাহেব-সুবোদের মতো বেশধারী জিন্নাহ যবে থেকে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন এবং মুসলিম কৃষক জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ অংশ যখন থেকে তাঁকেই তাদের নেতা বলে মানতে শুরু করল, তখন থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে আসল গণজোয়ার আসতে শুরু করল। নেহরু ‘ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া’ লিখলেন এবং জেলে বসে তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ব-ইতিহাস নিয়ে ইংরেজিতে যেসব চিঠিপত্র লিখে গেলেন, তা পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বৈশ্বিক পরিসরে পেশ করল। ইংরেজ গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে সুভাষ বসুর মহা-নিষ্ক্রমণ, পরবর্তী সময়ে তাঁর জার্মানি ও জাপান যাত্রা, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন– এগুলো ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মহাপথপরিক্রমা। বাংলাদেশেও ৬ দফা থেকে স্বাধীনতার পর্যায়ে উত্তরণ ঘটল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। এসব মিথ্যে নয়, ইতিহাসে ব্যক্তি বা নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করার নয়, কিন্তু এসবই জাতীয়তাবাদী আখ্যানের অংশ, ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা। কিন্তু তার বাইরেও অন্য ইতিহাস রয়ে গেছে।
অন্য ইতিহাস বলতে সচরাচর আমরা বুঝি ‘মার্ক্সবাদী’ ইতিহাসচর্চার ধারা, যেটি স্পষ্টতই ঔপনিবেশিক এবং ‘জাতীয়তাবাদী’ ইতিহাসচর্চা থেকে আলাদা। মার্ক্সবাদী ঘরানার মধ্যে নানা উপধারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেটা এখানে প্রশ্ন হিসেবে পাঠকদের মধ্যে দেখা দেবে তা হলো– এসবের মধ্যে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার স্থান কোথায়? মার্ক্সীয় ধারার থেকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ কতটা ও কোথায় পৃথক? ‘তল থেকে দেখা ইতিহাস’– এই ধারার সাথেই বা এর সম্পর্ক কী রকম?
সবচেয়ে সরল বা মোটাদাগের প্রভেদটা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে (যদিও আমরা অচিরেই দেখব যে মূল পার্থক্যটা সেখানে নয়)। ঔপনিবেশিক এলিটকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার ধারায় মূল আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে ঔপনিবেশিক (ইংরেজ) প্রভুদের জীবনচর্চা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নীতিমালা, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বাদানুবাদ ইত্যাদিকে ঘিরে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ‘নায়ক’ হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, তাঁদের জীবন ও কর্মতৎপরতা– যার মধ্য দিয়ে একটি জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ধীরে ধীরে। মার্ক্সীয় ইতিহাসচর্চার মূলে রয়েছে তাঁর ‘শ্রেণিগত’ দৃষ্টিকোণ– ‘পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের পরিণতি’ এই ঘোষণায় আস্থা রেখে। আধুনিক সমাজে পুঁজির মালিক ও শিল্প-প্রলেতারিয়েত হচ্ছে দুই যুধ্যমান পক্ষ। সম্পত্তির ওপরে কার অধিকার তা নিয়ে যুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ মার্ক্সীয় ইতিহাসচর্চায় শোষক ও শোষিতের মুখের চেহারাটি স্পষ্ট; সহজেই তাদের শনাক্ত করা যায়। অন্তত সেটাই এই ঘরানার ইতিহাসবিদদের প্রধান দাবি : সমস্ত শোষণের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থের টানাপোড়েন। এবং এই অর্থনৈতিক শোষণ যারা চালাচ্ছে এবং যাদের ওপরে চালাচ্ছে, সেটি উন্মোচন করতে পারলেই ইতিহাসের রথের ঘোড়া যে পথ বেয়ে চলেছে সেই পথকে বোঝা সম্ভব হবে।
এইসবের প্রেক্ষিতে সাব-অলটার্ন স্টাডিজের অবস্থান কোথায়? ‘নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে সাব-অলটার্ন ঐতিহাসিক মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকের তুলনায় বেশি অনিশ্চয়তায় ভুগবেন। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বাইরে ইতিহাসের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর খুঁজে বেড়াবেন। ইতিহাসের কর্তা হিসেবে তিনি স্পষ্ট করে কোনো নায়ককে দেখতে পাবেন না। না ঔপনিবেশিক ‘প্রভু’, না জাতীয়তাবাদী ‘লিডার’, না দলিত-শোষিত শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ‘নেতা’– কেউ তাঁর চোখে পূর্বনির্ধারিতভাবে নায়কের আসনে সমাসীন নন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা আসলে ‘বিরোধী বা ক্রিটিকাল ইতিহাস রচনা’। পুরো উদ্ধৃতিটি আমি এখানে তুলে ধরতে চাই:
“প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনার পদ্ধতি আছে, থাকবে। উচ্চবর্গের আধিপত্যও আছে, থাকবে। অন্তত ইতিহাস লিখে সে-আধিপত্যের অবসান ঘটানো যাবে না। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাহলে কী করতে পারেন? তিনি বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে।
[ক্রমশ]
রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা
পর্ব : ০৩ [পূর্বে প্রকাশের পর]
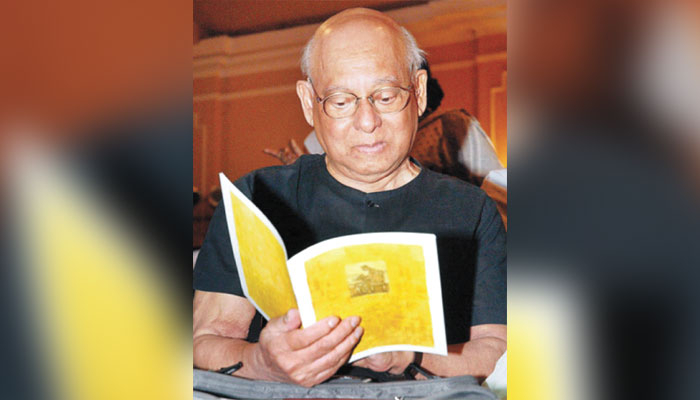
এমনকি সেরকম হবারও কোনো প্রয়োজন নেই, না রায়তের নিজস্বার্থে না সরকারের স্বার্থে।’ রণজিৎ একে যথার্থভাবেই ‘সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত’ বলেছেন এবং এই পয়েন্টে এসে ফিলিপ ফ্রান্সিসকে আমরা আর চিনতে পারি না।
ফ্রান্সিসের তৃতীয় অসুবিধে ছিল যে উপনিবেশের স্থানীয় ক্ষমতা-কাঠামো আমলে না নিয়ে এডাম স্মিথের ‘লেসে-ফেয়ার’ নীতির ওপরে তিনি বেশি করে নির্ভর করেছেন। আবার জমিদারকে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার দিলেও তিনি রায়তকেও পক্ষে রাখতে চেয়েছেন, তবে নিতান্তই পরোক্ষভাবে। প্রজার সঙ্গে জমিদার কী রকম বন্দোবস্তের চুক্তি করবে তা একান্তইভাবেই জমিদারের এখতিয়ার এ কথা কয়েকবার বলার পর তিনি অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন যে চুক্তির বিষয়টা দু’পক্ষের ওপরে ছেড়ে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। ফ্রান্সিস মনে করেছেন যে সরকারি হস্তক্ষেপ না ঘটলে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্পর্ক একটা স্বেচ্ছাচুক্তির আকার ধারণ করবে: ‘দু’পক্ষকেই যদি এভাবে নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সহজেই এমন একটা চুক্তিতে আসবে যাতে উভয়েরই সুবিধা।’ জমিদার ও রায়ত– এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের চেয়ে আপসেরই সম্ভাবনা দেখেছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে ১৭৬৯-১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী গ্রামবাংলার অবস্থাকে তিনি সাক্ষী মেনেছেন। যুক্তিটি কৌতূহুলোদ্দীপক:
‘এ দেশের বর্তমান অবস্থায় জমিদারের চেয়ে রায়তেরই সুবিধা হবে বেশি। এতখানি জমি যেখানে পতিত পড়ে আছে এবং আবাদ করার লোক যখন এত কম, তখন চাষিকে সাধাসাধি করতে হবে।’
এ কথা ফ্রান্সিস লিখতে পারলেন কী করে? নিকট ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের প্রভাব কেটে গেলে জমির ওপর কৃষিজীবী লোকসংখ্যার চাপ আবারও বেড়ে যাবে। ফলে জমিদার রায়তের মধ্যে দরকষাকষির সুবিধা-অসুবিধার এই হিসাব পাল্টে যেতে পারে। চাষের শর্ত উত্তরোত্তর জমিদারের পক্ষে ও রায়তের বিপক্ষে চলে যেতে পারে সেই চিত্রটা ফ্রান্সিস তার হিসাবে রাখেননি। ধনিক-চাষি যেমন ক্ষেতমজুরের শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসেবে খরিদ করে, স্বত্বাধিকারী জমিদার তেমনিভাবে স্বত্বহীন রায়তের কাছ থেকে শ্রমশক্তি কিনবে। এ ক্ষেত্রে কোনো জোরাজুরি নেই, দু’পক্ষের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে অলিখিত স্বেচ্ছাচুক্তির ভিত্তিতে, যার মূলে রয়েছে ‘লেবার-মার্কেটের চাহিদা-জোগানের অমোঘ নিয়ম’। দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রান্সিস বাংলার কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের কল্পনা করেছেন জমিদারকে জমির মালিকানা দিয়ে আর স্বত্ববিহীন রায়তকে তার মালিকানার অধিকার কেড়ে নিয়ে সেই জমির চাষাবাদে শ্রম দিতে বাধ্য করে। রণজিৎ গুহ অনুমান করেছেন যে অর্থশাস্ত্রের ফিজিওক্রেটিক স্কুলের প্রভাবের কারণেই ফ্রান্সিস জমিদার ও রায়তের মধ্যে ওরকম শ্রম কেনা-বেচার একটি ‘স্বাধীন চুক্তি’ কল্পনা করতে পেরেছিলেন যেটা কেবল ধনতান্ত্রিক কৃষিতেই ঘটে থাকে।
প্রশ্ন উঠতে পারে, লেবার মার্কেটের চাহিদা-জোগানের ‘অমোঘ নিয়মে’ জমিদার-রায়তের মধ্যে জমির ব্যবহার নিয়ে একধরনের বন্দোবস্ত নাহয় হলো, কিন্তু জমিদার সেই চুক্তি যদি না মানে? সেক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের যুক্তি ছিল জমিদার ও রায়তের মধ্যকার বন্দোবস্তের শর্ত লেখা থাকবে ‘পাট্টা’ নামক দলিলে, এবং শর্তসংবলিত সেই পাট্টাকেই ‘আইনসংগত চুক্তিপত্র’ বলে গণ্য করা হবে। ৫ নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখে ফ্রান্সিস তার লাটসভার বিবৃতিতে বললেন যে, “পাট্টাই হচ্ছে জমিদারের সঙ্গে রায়তের ‘স্বেচ্ছাচুক্তির সাক্ষ্য ও গ্যারান্টি’ এবং গভর্নমেন্টের উচিত ‘তাদের এই পারস্পরিক চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা’ অবলম্বন করা।” কিন্তু বাস্তবে ১৭৯৩ সালের আইনে চাষিদের এ রকম অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জমিদার শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতার নির্ভরযোগ্য সামাজিক শক্তি হিসেবে সমর্থন দেওয়ার রাজনৈতিক যুক্তিই তখন প্রধান বিবেচনা হিসেবে কাজ করেছিল।
শুধু কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রবর্তন নয়, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এর রাজস্ব-তাৎপর্য নিয়েও ভেবেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রথম দিকে ব্রিটিশরাজের খাজনা আদায় বাড়লেও আখেরে তা কমে যাবে এটা বুঝতে পারা কঠিন কিছু নয়। প্রথমত, খাজনা চিরকালের জন্য বাঁধা (যা চলতি মূল্যে স্থিরীকৃত এবং যার প্রকৃত মূল্য মূল্যস্ফীতির সাথে কমতে বাধ্য); দ্বিতীয়ত, জমিদার চাষাবাদে অনীহা দেখালে জমির উৎপাদনশীলতা (land productivity) বাড়ার সম্ভাবনা কম; তৃতীয়ত, রায়তের ওপরে নানা কায়দায় বাড়তি শোষণ এই উৎপাদনশীলতাকে আরও কমিয়ে নিয়ে আসবে। এ কারণেই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে জমিদারি বন্দোবস্ত থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিসরে দেখলে– রাজস্ব আদায় কমই হয়েছে। তুলনামূলকভাবে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৮৫০-এর পরে প্রবর্তিত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকার ‘রায়তওয়ারী’ বন্দোবস্ত থেকে। শেষোক্ত ব্যবস্থায় জমির মালিক করা হয়েছিল খোদ কৃষককেই– কোনো ওপর থেকে বসানো জমিদারকে নয়। এর ফলে ব্রিটিশরাজের রাজস্বগত আয়ই বেশি হয়েছিল তা-ই নয়, রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক উন্নয়নও বাংলার তুলনায় বেগবান হয়েছিল। অভিজিৎ ব্যানার্জীদের লেখা থেকে সেটা আজ সুপ্রমাণিত। ফ্রান্সিস কেন এই লাইনে যুক্তি দেননি তখন?
ফ্রান্সিস রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের যুক্তিতে না হেঁটে ‘আসন্ন সর্বনাশকে’ প্রথমে মোকাবিলা করতে চাইলেন। তার চোখে আসন্ন সর্বনাশ ছিল– আগেই বলেছি– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অমিত রাজস্বক্ষুধা। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তার পয়লা নম্বর নালিশ ছিল ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা :
‘এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবৃত্তিকে অচল অটলভাবে অনুসরণ করার ফলেই এ দেশের সর্বনাশ ঘটেছে, এবং সত্যিই যে কোনো অর্থনৈতিক লাভ এতে হয় না সে কথাও অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।’
ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির পেছনে ছিল খাজনার হার বাড়ানো। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের যুক্তি অধুনাকালের ‘সাপ্লাই-সাইডার্স’ মতবাদের অনুসারীদের মতো। করের হার কমিয়ে মোট কর-রাজস্ব বাড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাজনার হার খুব চড়া ধরে তার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাবার নীতি বর্জন করে তার বদলে স্বল্প হারে খাজনার পরিমাণ একেবারেই অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত– এই ছিল ফ্রান্সিসের প্রস্তাব। এই প্রসঙ্গে তার মতামত যে সরাসরি মঁতাস্ক্যুর কাছে ঋণী তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন:
“রাজস্ব সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ও সরল নীতিটি আমি মঁতাস্ক্যুর এই সূত্রের ভিত্তিতে রচনা করেছি: ‘জনসাধারণ কতখানি দিতে পারে তা নয়, কতটা তাদের দেওয়া উচিত, তারই ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা কর্তব্য’– অর্থাৎ কতটা দিতে পারছে তা নয়, কতটা তারা সর্বদাই দিয়ে যেতে পারে তারই ভিত্তিতে।”
এক কথায় ‘সরকারের মূল শাসনব্যবস্থাটিকে চালু রাখার জন্য যতটুকু না হলে নয় তারই ভিত্তিতে হিসাব করে’ রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত।
এক পর্যায়ে রাজস্ব-হ্রাসের প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিস মোগল আমলের নজির টেনে নিজের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। মঁতাস্ক্যু বলেছিলেন যে মোগল শাসকেরা বিজিত দেশের রাজস্বের হার ও পরিমাণ অনড়ভাবে বেঁধে দিত বলেই তাদের শাসন এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। ২২ জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের পরিকল্পনায় ফ্রান্সিস এই মত উল্লেখ করে বলেন: ‘মুসলিম বিজেতারা সুপরিমিত রাজস্ব আদায় করতেন, এবং আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যেও কোনো জটিলতা ছিল না; এই কারণে তারা অতি সহজেই আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য কায়েম রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।’
স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এমন একটি কর-রাজস্ব ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে করের হারকে সহনীয় রাখা হবে, কর আদায়ের ব্যবস্থায় জটিলতা থাকবে না, এবং সুপরিমিতভাবে কর-রাজস্ব আদায় করা হবে। এতে করে দীর্ঘ মেয়াদে শাসনকার্যের স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। এই একই ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি জমির ওপরে সমস্ত প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ কর (tax) রদ করে শুধু খাজনাকেই (Rent) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে করভার কৃষকদের ওপর থেকে কমে যায়, আর তারা যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে নিতে পারে। কৃষকদের দিয়ে বেগার খাটানোর প্রথা, যেমন তাদের দিয়ে রাস্তা বাঁধার কাজে বেগার খাটানোর (corvee) প্রথা যেটা ফ্রান্সে একদা চালু ছিল, সেসব ‘সব রকম আবওয়াব ও মাথটের উচ্ছেদ’ করার তিনি প্রস্তাব করেন। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের চোখের সামনে ছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। ১৭৭৬ সালের ২২ জানুয়ারিতে তিনি বলেছেন:
‘দেশের লোক এত গরিব হয়ে পড়েছে এবং আগের তুলনায় এত কম জমিতে এখন চাষের কাজ হয় যে স্বভাবতই যেটুকু জমিতে চাষের কাজ চালু থাকে তার ওপরে করের ভার ক্রমেই বেড়ে যায়।’
ফ্রান্সিসের আলোচনার মাধ্যমে রণজিৎ গুহ কী বার্তা দিতে চাইলেন? প্রথমত, ফ্রান্সিস ছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ধনতন্ত্রের পন্থি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষিপণ্য চলাচলের ওপরে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার অবসান। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থাকে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বহির্বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত প্রকার অভ্যন্তরীণ শুল্ক উচ্ছেদ করতে। আমরা দেখেছি একটু আগেই যে সমস্ত প্রকার পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে ভূসম্পত্তির ওপরে একটিমাত্র কর বসিয়ে খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে আদায় করার প্রস্তাব। সাধারণভাবে মোগল রাজশক্তির অনুসরণে তিনি চেয়েছিলেন খাজনার অপেক্ষাকৃত পরিমিত ও অপরিবর্তনীয় হার। তিনি চেয়েছিলেন ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা; জমিদার ও রায়তের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে দরকষাকষির সম্পর্ক; এবং সেই সুবাদে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষের নিরসন, এবং ব্রিটিশরাজের আয় ও রাজনৈতিক সমর্থনের যুগপৎ সম্প্রসারণ।
দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে লাটসভায় যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা ছিল তখনকার বিচারে প্রাগ্রসর। সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক। কিন্তু ফ্রান্সিসের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর প্রস্তাব কলোনিয়াল পরিবেশে পড়ে বিপরীতধর্মী চেহারা নিল। অবাধ প্রতিযোগিতার ধার দিয়েও গেল না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা মেট্রোপলিতে অবস্থানরত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। উদাহরণত, ফ্রান্সিস চেয়েছিলেন কোম্পানির ‘সাপ্লাই ব্যবসা’ করার জন্য খোলা টেন্ডারে কোনোরকম বৈষম্য না রেখে সমস্ত দেশি ব্যবসায়ীকেই কনট্র্যাক্ট নেবার সুযোগ দেওয়া হোক। এতে করে কলকাতায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে এবং আখেরে কোম্পানিরই লাভ হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের অবাধ বাণিজ্যের প্রশস্তি কোম্পানির কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থা পূর্বাপর বজায় রইল। ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা পেল বটে, কিন্তু ফ্রান্সিস যাদের ভেবে জমিদারদের কাছে ভূমির অধিকার দিতে চাইলেন তারা মূলত এই সংস্কারের বাইরে থাকল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলভোগী হলো এক শহুরে নব্য-ধনী সম্প্রদায়, যারা ছিল কোম্পানিরই সাথে জড়িত ব্যবসায়ী-আমলা-মুৎসুদ্দী। এরাই নতুন জমিদার ও নতুন তালুকদার হয়ে রাজত্ব করবে পরবর্তী দেড়শ বছর ধরে। ফ্রান্সিস যাদের মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখলেন ধনবাদী বিকাশের যুক্তিতে, তারা কালক্রমে জমি কর্ষণের অধিকারও হারাল। ফ্রান্সিসের উদ্ভাবিত জমিদার-রায়তের ‘স্বেচ্ছা-চুক্তির’ সম্ভাবনা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল।
[ক্রমশ]
তপন রায়চৌধুরী গুনে দেখিয়েছেন যে বরিশালের কিছু এলাকায় জমিদার ও প্রকৃত কৃষক-প্রজার মাঝে ৩২-স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকে। প্রাগ-ব্রিটিশ পর্বে পুরোনো জমিদার-পুরোনো রায়তের মধ্যে (ফ্রান্সিসের ভাষায়) ‘স্বাভাবিক স্বার্থ ও সম্পর্কের যে পারস্পরিক বন্ধন ছিল’ তা প্রায় সর্বাংশে ধসে পড়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর নতুন পরিস্থিতিতে। কেন এমন হলো সে প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর– ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও ইউরোপের পুঁজিবাদ গোড়া থেকেই ভিন্ন নিয়ম মেনে অগ্রসর হচ্ছিল। একেই পার্থ চ্যাটার্জী পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন– ‘কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স’। মেট্টোপলির জন্য যে নিয়ম খাটে, কলোনির জন্য সে নিয়ম খাটে না। উপনিবেশের পরিস্থিতিতে অবাধ ধনতন্ত্রের যৌক্তিক নিয়ম কার্যকর করা যায় না। সেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাও সহজে চালু করা যায় না। রাজশক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ আর সব বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। সেখানে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়েও কৃষকের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থেaর মধ্যে স্থান পায় না। অন্তত বহুকাল পর্যন্ত পায়নি। যতদিন পর্যন্ত কৃষকেরা নিজেরাই তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলেছে, অথবা কখনও কখনও নীরবেই প্রতিবাদ করেছে প্রতিদিনের নিঃশব্দ প্রতিরোধে। রণজিৎ গুহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লেখার প্রায় কুড়ি বছর বাদে এ নিয়ে বিস্তৃত লিখবেন। কৃষক-বিদ্রোহ (বিদ্রোহ করা ছাড়া তার আর কী উপায় থাকছে তখন) এই প্রথম বড় আকারে স্থান পাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায়।
রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা
পর্ব : ০২ [পূর্বে প্রকাশের পর]

আসলে ফ্রান্সিসের অসুবিধে ছিল তিনটি। ফ্রান্সিসের চোখে মূল অ্যাডভারসেরি বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খোদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অ্যাডাম স্মিথের মতো তিনিও মনে করতেন যে কোম্পানির নীতিমালা অবাধ বাণিজ্য তত্ত্বের পরিপন্থি। কোম্পানির সঙ্গে ফ্রান্সিস বা স্মিথের এই সংঘর্ষের মধ্যে উদীয়মান ‘লিবারেল গভর্নমেন্টালিটির’ সঙ্গে গেড়ে-বসা ‘কলোনিয়াল গভর্নমেন্টালিটির’ সংঘর্ষ ধরা পড়েছে। কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বাংলার একচ্ছত্র ‘দেওয়ানী’ লাভের পর চারদিকে খাজনা আদায়ের যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল– যেটি চলে প্রায় এক দশক অবধি– তাতে করে বাংলাদেশের কৃষকের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এই অতিরিক্ত শোষণেরই পরিণতি ১৭৭০ সালের মহা-মন্বন্তর; যার ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণহানি ঘটে। খোদ ইংল্যান্ডে এই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রান্সিস, তার বন্ধু এডমান্ড বার্ক এবং অন্য সহযোগীরা তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে সরাসরি এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেন। তাদের যুক্তি– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করছে বলেই এই নির্বিচার শাসন চলতে পারছে। এর ফলে শুধু বাংলায় অপরিসীম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে তা-ই নয়, ব্রিটিশ স্বার্থেরও আখেরে ক্ষতি হচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী হেস্টিংস নিজে। বঙ্কিম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–
‘১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই। সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল– লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল … অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে-কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহির জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।’
বঙ্কিমের বর্ণনায় শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা ছিল না, অধিকন্তু ছিল সাধারণ মানুষ যখন উপবাসে কষ্ট পাচ্ছে, তখন রাজশক্তি (প্রকারান্তরে ব্রিটিশ শাসন) ‘রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায়’ বুঝে নিচ্ছে; যখন অনাবৃষ্টিতে সামান্যই ফলন হয়েছে, তখন রাজশক্তি সিপাহিদের তথা সামরিক বাহিনীর জন্য সেই ফসল কিনে রাখছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে; এমনকি যখন লোকজন দুই বেলা করে উপবাস করছে, তখনও ‘রাজস্ব আদায়’ বন্ধ হয়নি। যাতে কোম্পানির মোট রাজস্ব আদায়ে যাতে টান না পড়ে সেজন্য উপবাসের বছরে রাজস্বের মাত্রা ‘শতকরা দশ টাকা’ হারে বৃদ্ধি করা হলো। স্পষ্টতই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ওয়ারেন হোস্টিংসের আমলে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও অপশাসনের ওপরে, যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখভোগকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।
ফ্রান্সিসের প্রথম অসুবিধে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে কার্যত ‘ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজমের’ সাথে এক কাতারে মেলানো। প্রাগ-ব্রিটিশ পর্বের মোগল সাম্রাজ্যে জমিতে ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। সব জমির মালিক ছিলেন ‘এশিয়াটিক’ মোগল-সম্রাট। রাজশক্তির রাজকর্মচারীরা জমির ইজারাদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে কর-রাজস্ব আদায় করতেন। ফ্রান্সিসের যুক্তি ছিল যে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল-সম্রাটের ‘স্থান গ্রহণ’ করেছে, অর্থাৎ নিজেকে সব জমির মালিক ঘোষণা করেছে। এবং জমির ইজারাদারদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো কর-রাজস্ব আদায় করছে। এই ইঙ্গিতটাই বঙ্কিমের পূর্বে-উদ্ধৃত লেখায় দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানির শাসন ও মোগল শাসন– এই দুইয়েরই মধ্যে জমিতে ব্যক্তিমালিকানা অনুপস্থিত এই সমীকরণ টেনে ফ্রান্সিস পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে বাড়তি যুক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন। এই যুক্তিতেই ফ্রান্সিস ওয়ারেন হেস্টিংসের ‘ইজারাদারি ব্যবস্থার’ বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। সামন্ততন্ত্রে তা সে মোগল শাসনেই হোক, আর ষোড়শ লুইয়ের ফ্রান্সেই হোক, ইজারাদারি ব্যবস্থায় সকল জমিকে ‘রাষ্ট্রের সম্পত্তি’ হিসেবে দেখা হয় ও জমিদারকে কেবল ‘রাষ্ট্রের কর্মচারী’ বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, ফ্রান্সিসের পরিকল্পনায় জমি হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং জমিদার হবে উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পত্তির মালিক। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সিসের অভিযোগ ছিল যে তার আমলে নিলাম ডেকে সর্বোচ্চ খরিদ্দারের কাছে অল্প ও অনিশ্চিত মেয়াদে ভূমি ইজারা দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়েছে। এতে করে ইজারাদারি (লিজ) পদ্ধতিতে (১) ‘মালিকানার শাশ্বত অধিকারকে’ অস্বীকার করা হয়েছে; (২) ‘রাজস্বের দাবি অত্যন্ত উঁচু হারে’ বেঁধে রাখা হয়েছে; এবং (৩) এই হারও যখন-তখন বদলে যেতে পারে, অর্থাৎ ইজারাদারি ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার ‘স্ট্যাবিলিটি’ নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে এর পরও ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ১৭৬৫-উত্তর বাংলাদেশে, তার কারণ তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভুল পাঠ করেছেন। যেখানে ওয়ারেন হেস্টিংসের কোম্পানি জমিতে সামন্ত মোগল যুগের ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, সেখানে ফ্রান্সিস চাইছেন ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা। এ দুই আইডিয়ার সংঘাত আসলে উপনিবেশের জমিনে নব্য-সামন্তবাদের সাথে পুঁজিবাদের লড়াই। রণজিৎ গুহ স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এই মর্মে:
“ফ্রান্সিস বলেছেন যে ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোম্পানি ‘মালিকের কাজ’ করেছে, কারণ রাজশক্তিই জমির মালিক এই ভুল ধারণা থেকেই উক্ত ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। এই নীতি অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে যারা সম্পত্তির আইনসংগত মালিক তাদের অধিকার হরণ করে ‘সব ক্ষেত্রেই বিদেশিদের কাছে জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে’; বিদেশি বলতে তিনি কলকাতার বেনেদের নাম করেছেন, কারণ তারা গ্রামবাংলার লোক নয়, অথচ স্বনামে বা শ্বেতাঙ্গদের হয়ে বেনামিতে তারাই জমি বেশি ইজারা নিত।”
ফ্রান্সিসের প্রথম অসুবিধেটা তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমি-নীতিকে তিনি পছন্দ করছেন না ব্যক্তিমালিকানার প্রতি স্বীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে। কিন্তু একই সাথে তিনি এ-ও বুঝতে পারছেন যে কোম্পানিকে ছাড়া এই মুহূর্তে উপনিবেশের সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। ১৭৭৬ সালে ২২ জানুয়ারি ফ্রান্সিস বাংলার লাটপরিষদে যখন হেস্টিংসের ইজারাদারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন, তখন জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঐ বছরের ৪ জুলাই আমেরিকা তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ তখন কোম্পানির ওপর নির্ভর করা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষ সামরিকভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। এক পর্যায়ে ইয়র্কটাউনের যুদ্ধে পরাস্ত জেনারেল কর্নওয়ালিসকে ‘লর্ড’ উপাধি দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। এই হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অপসারণের কোনো পথ সেদিন জানা ছিল না ফ্রান্সিসের। তিনি শুধু আশা করেছিলেন যে কোম্পানির ইজারাদারি পলিসির সমালোচনার ফলে কৃষিতে ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে সমর্থন জোরালো হবে; কোম্পানি তার জমি বা কৃষি-সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবর্তন করবে; এবং এক পর্যায়ে কোম্পানির একাধিপত্যের ওপরেও ব্রিটিশ সরকারের তীক্ষ্ম নজরদারি স্থাপিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি দেখলেন যে ইজারাদারি ব্যবস্থার সুফল পেয়েছে গ্রামবাংলার বাইরের লোকজন, যারা মূলত কোম্পানির এ দেশীয় কর্মচারী এবং যারা কলকাতায় থেকে ‘স্বনামে বা শ্বেতাঙ্গদের হয়ে বেনামিতে’ জমি ইজারা নিয়ে আসছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা ফুলে-ফেঁপে উঠছিল ১৭৬৫-১৭৯৩ কালপর্বে। এদেরকেই বলা হতো তৎকালের ‘নব্য-ধনী’, যারা প্রাগ-ব্রিটিশ পর্বের (পড়ন্ত) জমিদার শ্রেণি থেকে ভিন্ন চরিত্রের। এক নতুন সামাজিক বর্গ হিসেবে এরা সেই সময়ে আবির্ভূত হয়। বাংলায় কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তনের সময় আদিতে যে ৬৯৩ জন বৃহৎ জমিদারি স্বত্ব লাভ করেছিলেন, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন প্রাক্তন-ইজারাদার তথা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কৃষি-ব্যবসার সাথে জড়িত নব্য-ধনী গোষ্ঠী। এদের কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গদের সাথে মিলে রপ্তানি বাণিজ্যেও জড়িত ছিলেন। এরাই ছিল বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের মূল রাজনৈতিক ভিত্তি। ফলে ১৭৯৩ সালের ভূমি-নীতি বাংলায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সূত্রপাত না করে পর্যবসিত হয়েছিল মার্কস-কথিত ‘ভূমি সংস্কারের এক ক্যারিক্যাচারে’।
ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় অসুবিধে ছিল কৃষিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্নটিকে তিনি শুধু জমিদারের সাথে সম্পর্কিত করে ভেবেছিলেন। রায়তের কাছে চাষযোগ্য জমিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেননি। আমি রায়তকে জমির মালিকানা-স্বত্ব দেওয়ার কথা তুলছি না (যদিও সেটাও একটা ইস্যু এখানে)। আমি বলছি বর্গা-চাষি হিসেবে রায়তকে জমি ‘ব্যবহারের’ চিরস্থায়ী অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে। হতে পারে যে তিনি হয়তো শুধু কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের ‘প্রুসিয়ার পথই’ মানস-কল্পনায় রেখেছেন। যার মোদ্দা কথা হলো, জমিদার-জোতদার বা বৃহৎ ভূস্বামীও জমিতে বিনিয়োগ করতে করতে একসময় পুঁজিবাদী ধনিক কৃষকে রূপান্তরিত হতে পারে। রণজিৎ অবশ্য লিখেছেন এক্ষেত্রে ফ্রান্সিস শুধু জমিদারের কথা নয়, রায়তের কথাও ভেবেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে সেটা ছিল নিতান্তই একটি অর্ধ-চিন্তিত প্রকল্প। যেমন, ১৭৭৫ সালে লর্ড নর্থকে তিনি লিখেছিলেন ‘জমিদার, তালুকদার, এমনকি রায়তেরও সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করা উচিত।’ এর থেকে ধারণা হতে পারে, জমিদারকে চিরস্থায়ী ব্যক্তিমালিকানা স্বত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তিনি বুঝি রায়ত বা প্রজাদেরকেও (tenants) রক্ষা করতে চান এক ধরনের বর্গা-নিরাপত্তা বা tenurial security দানের মাধ্যমে। কেননা, তিনি তো জানতেন যে জমিদারি স্বত্ব দিলেও এই পুরাতন জমিদার শ্রেণি জমির দেখভাল করতে পারবে না: ‘আমি শুনেছি এবং বিশ্বাসও করি যে তরুণ জমিদার সন্তানদের অধিকাংশই জড়বুদ্ধি মূর্খ। … কিন্তু উপায় কী, জমিদারি বা ইজারাদারি একটা বেছে নিতেই হবে।’ তাহলে সমাধান কী এখানে? ফ্রান্সিস একটা অনন্য সমাধান দিতে পারতেন। জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা-স্বত্ব দেওয়া হলে হোক, কিন্তু সাথে সাথে তাদের জমি যারা চাষ করবে তাদেরকেও চিরকালের বা দীর্ঘকালের জন্য ঐ জমি চাষ করার অধিকার দেওয়া হোক, যাতে করে ‘রায়ত চিরদিনের বা দীর্ঘকালের মতো জমির অধিকার ভোগ করতে পারে’– অর্থাৎ রায়তের সঙ্গেও জমির মালিকানায় না হোক, জমির ব্যবহার নিয়ে চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেত। কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে ফ্রান্সিস সে পথে হাঁটলেন না। জমিদারকেই জমির প্রকৃত মালিক হতে হবে, রায়তকে নয়– এই যুক্তিতে অনড় রইলেন। কোনো দ্বিধা-সংশয় না রেখে স্পষ্টই তিনি রায় দিলেন: ‘এ কথা আদৌ সত্য নয় যে রায়তই জমির স্বত্বাধিকারী।
[ক্রমশ]
এমনকি সেরকম হবারও কোনো প্রয়োজন নেই, না রায়তের নিজস্বার্থে না সরকারের স্বার্থে।’ রণজিৎ একে যথার্থভাবেই ‘সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত’ বলেছেন এবং এই পয়েন্টে এসে ফিলিপ ফ্রান্সিসকে আমরা আর চিনতে পারি না।
ফ্রান্সিসের তৃতীয় অসুবিধে ছিল যে উপনিবেশের স্থানীয় ক্ষমতা-কাঠামো আমলে না নিয়ে এডাম স্মিথের ‘লেসে-ফেয়ার’ নীতির ওপরে তিনি বেশি করে নির্ভর করেছেন। আবার জমিদারকে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার দিলেও তিনি রায়তকেও পক্ষে রাখতে চেয়েছেন, তবে নিতান্তই পরোক্ষভাবে। প্রজার সঙ্গে জমিদার কী রকম বন্দোবস্তের চুক্তি করবে তা একান্তইভাবেই জমিদারের এখতিয়ার এ কথা কয়েকবার বলার পর তিনি অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন যে চুক্তির বিষয়টা দু’পক্ষের ওপরে ছেড়ে দিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। ফ্রান্সিস মনে করেছেন যে সরকারি হস্তক্ষেপ না ঘটলে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্পর্ক একটা স্বেচ্ছাচুক্তির আকার ধারণ করবে: ‘দু’পক্ষকেই যদি এভাবে নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা সহজেই এমন একটা চুক্তিতে আসবে যাতে উভয়েরই সুবিধা।’ জমিদার ও রায়ত– এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের চেয়ে আপসেরই সম্ভাবনা দেখেছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে ১৭৬৯-১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী গ্রামবাংলার অবস্থাকে তিনি সাক্ষী মেনেছেন। যুক্তিটি কৌতূহুলোদ্দীপক:
‘এ দেশের বর্তমান অবস্থায় জমিদারের চেয়ে রায়তেরই সুবিধা হবে বেশি। এতখানি জমি যেখানে পতিত পড়ে আছে এবং আবাদ করার লোক যখন এত কম, তখন চাষিকে সাধাসাধি করতে হবে।’
এ কথা ফ্রান্সিস লিখতে পারলেন কী করে? নিকট ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের প্রভাব কেটে গেলে জমির ওপর কৃষিজীবী লোকসংখ্যার চাপ আবারও বেড়ে যাবে। ফলে জমিদার রায়তের মধ্যে দরকষাকষির সুবিধা-অসুবিধার এই হিসাব পাল্টে যেতে পারে। চাষের শর্ত উত্তরোত্তর জমিদারের পক্ষে ও রায়তের বিপক্ষে চলে যেতে পারে সেই চিত্রটা ফ্রান্সিস তার হিসাবে রাখেননি। ধনিক-চাষি যেমন ক্ষেতমজুরের শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসেবে খরিদ করে, স্বত্বাধিকারী জমিদার তেমনিভাবে স্বত্বহীন রায়তের কাছ থেকে শ্রমশক্তি কিনবে। এ ক্ষেত্রে কোনো জোরাজুরি নেই, দু’পক্ষের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে অলিখিত স্বেচ্ছাচুক্তির ভিত্তিতে, যার মূলে রয়েছে ‘লেবার-মার্কেটের চাহিদা-জোগানের অমোঘ নিয়ম’। দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রান্সিস বাংলার কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের কল্পনা করেছেন জমিদারকে জমির মালিকানা দিয়ে আর স্বত্ববিহীন রায়তকে তার মালিকানার অধিকার কেড়ে নিয়ে সেই জমির চাষাবাদে শ্রম দিতে বাধ্য করে। রণজিৎ গুহ অনুমান করেছেন যে অর্থশাস্ত্রের ফিজিওক্রেটিক স্কুলের প্রভাবের কারণেই ফ্রান্সিস জমিদার ও রায়তের মধ্যে ওরকম শ্রম কেনা-বেচার একটি ‘স্বাধীন চুক্তি’ কল্পনা করতে পেরেছিলেন যেটা কেবল ধনতান্ত্রিক কৃষিতেই ঘটে থাকে।
প্রশ্ন উঠতে পারে, লেবার মার্কেটের চাহিদা-জোগানের ‘অমোঘ নিয়মে’ জমিদার-রায়তের মধ্যে জমির ব্যবহার নিয়ে একধরনের বন্দোবস্ত নাহয় হলো, কিন্তু জমিদার সেই চুক্তি যদি না মানে? সেক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের যুক্তি ছিল জমিদার ও রায়তের মধ্যকার বন্দোবস্তের শর্ত লেখা থাকবে ‘পাট্টা’ নামক দলিলে, এবং শর্তসংবলিত সেই পাট্টাকেই ‘আইনসংগত চুক্তিপত্র’ বলে গণ্য করা হবে। ৫ নভেম্বর ১৭৭৬ তারিখে ফ্রান্সিস তার লাটসভার বিবৃতিতে বললেন যে, “পাট্টাই হচ্ছে জমিদারের সঙ্গে রায়তের ‘স্বেচ্ছাচুক্তির সাক্ষ্য ও গ্যারান্টি’ এবং গভর্নমেন্টের উচিত ‘তাদের এই পারস্পরিক চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা’ অবলম্বন করা।” কিন্তু বাস্তবে ১৭৯৩ সালের আইনে চাষিদের এ রকম অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জমিদার শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতার নির্ভরযোগ্য সামাজিক শক্তি হিসেবে সমর্থন দেওয়ার রাজনৈতিক যুক্তিই তখন প্রধান বিবেচনা হিসেবে কাজ করেছিল।
শুধু কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রবর্তন নয়, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এর রাজস্ব-তাৎপর্য নিয়েও ভেবেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রথম দিকে ব্রিটিশরাজের খাজনা আদায় বাড়লেও আখেরে তা কমে যাবে এটা বুঝতে পারা কঠিন কিছু নয়। প্রথমত, খাজনা চিরকালের জন্য বাঁধা (যা চলতি মূল্যে স্থিরীকৃত এবং যার প্রকৃত মূল্য মূল্যস্ফীতির সাথে কমতে বাধ্য); দ্বিতীয়ত, জমিদার চাষাবাদে অনীহা দেখালে জমির উৎপাদনশীলতা (land productivity) বাড়ার সম্ভাবনা কম; তৃতীয়ত, রায়তের ওপরে নানা কায়দায় বাড়তি শোষণ এই উৎপাদনশীলতাকে আরও কমিয়ে নিয়ে আসবে। এ কারণেই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে জমিদারি বন্দোবস্ত থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিসরে দেখলে– রাজস্ব আদায় কমই হয়েছে। তুলনামূলকভাবে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৮৫০-এর পরে প্রবর্তিত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এলাকার ‘রায়তওয়ারী’ বন্দোবস্ত থেকে। শেষোক্ত ব্যবস্থায় জমির মালিক করা হয়েছিল খোদ কৃষককেই– কোনো ওপর থেকে বসানো জমিদারকে নয়। এর ফলে ব্রিটিশরাজের রাজস্বগত আয়ই বেশি হয়েছিল তা-ই নয়, রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক উন্নয়নও বাংলার তুলনায় বেগবান হয়েছিল। অভিজিৎ ব্যানার্জীদের লেখা থেকে সেটা আজ সুপ্রমাণিত। ফ্রান্সিস কেন এই লাইনে যুক্তি দেননি তখন?
ফ্রান্সিস রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের যুক্তিতে না হেঁটে ‘আসন্ন সর্বনাশকে’ প্রথমে মোকাবিলা করতে চাইলেন। তার চোখে আসন্ন সর্বনাশ ছিল– আগেই বলেছি– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অমিত রাজস্বক্ষুধা। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তার পয়লা নম্বর নালিশ ছিল ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা :
‘এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবৃত্তিকে অচল অটলভাবে অনুসরণ করার ফলেই এ দেশের সর্বনাশ ঘটেছে, এবং সত্যিই যে কোনো অর্থনৈতিক লাভ এতে হয় না সে কথাও অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।’
ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির পেছনে ছিল খাজনার হার বাড়ানো। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের যুক্তি অধুনাকালের ‘সাপ্লাই-সাইডার্স’ মতবাদের অনুসারীদের মতো। করের হার কমিয়ে মোট কর-রাজস্ব বাড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাজনার হার খুব চড়া ধরে তার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাবার নীতি বর্জন করে তার বদলে স্বল্প হারে খাজনার পরিমাণ একেবারেই অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত– এই ছিল ফ্রান্সিসের প্রস্তাব। এই প্রসঙ্গে তার মতামত যে সরাসরি মঁতাস্ক্যুর কাছে ঋণী তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন:
“রাজস্ব সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ও সরল নীতিটি আমি মঁতাস্ক্যুর এই সূত্রের ভিত্তিতে রচনা করেছি: ‘জনসাধারণ কতখানি দিতে পারে তা নয়, কতটা তাদের দেওয়া উচিত, তারই ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা কর্তব্য’– অর্থাৎ কতটা দিতে পারছে তা নয়, কতটা তারা সর্বদাই দিয়ে যেতে পারে তারই ভিত্তিতে।”
এক কথায় ‘সরকারের মূল শাসনব্যবস্থাটিকে চালু রাখার জন্য যতটুকু না হলে নয় তারই ভিত্তিতে হিসাব করে’ রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত।
এক পর্যায়ে রাজস্ব-হ্রাসের প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিস মোগল আমলের নজির টেনে নিজের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। মঁতাস্ক্যু বলেছিলেন যে মোগল শাসকেরা বিজিত দেশের রাজস্বের হার ও পরিমাণ অনড়ভাবে বেঁধে দিত বলেই তাদের শাসন এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। ২২ জানুয়ারি ১৭৭৬ তারিখের পরিকল্পনায় ফ্রান্সিস এই মত উল্লেখ করে বলেন: ‘মুসলিম বিজেতারা সুপরিমিত রাজস্ব আদায় করতেন, এবং আদায়ের ব্যবস্থার মধ্যেও কোনো জটিলতা ছিল না; এই কারণে তারা অতি সহজেই আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য কায়েম রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।’
স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এমন একটি কর-রাজস্ব ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে করের হারকে সহনীয় রাখা হবে, কর আদায়ের ব্যবস্থায় জটিলতা থাকবে না, এবং সুপরিমিতভাবে কর-রাজস্ব আদায় করা হবে। এতে করে দীর্ঘ মেয়াদে শাসনকার্যের স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। এই একই ধারণার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি জমির ওপরে সমস্ত প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ কর (tax) রদ করে শুধু খাজনাকেই (Rent) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে করভার কৃষকদের ওপর থেকে কমে যায়, আর তারা যাতে নির্বিঘ্নে তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে নিতে পারে। কৃষকদের দিয়ে বেগার খাটানোর প্রথা, যেমন তাদের দিয়ে রাস্তা বাঁধার কাজে বেগার খাটানোর (corvee) প্রথা যেটা ফ্রান্সে একদা চালু ছিল, সেসব ‘সব রকম আবওয়াব ও মাথটের উচ্ছেদ’ করার তিনি প্রস্তাব করেন। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সিসের চোখের সামনে ছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক। ১৭৭৬ সালের ২২ জানুয়ারিতে তিনি বলেছেন:
‘দেশের লোক এত গরিব হয়ে পড়েছে এবং আগের তুলনায় এত কম জমিতে এখন চাষের কাজ হয় যে স্বভাবতই যেটুকু জমিতে চাষের কাজ চালু থাকে তার ওপরে করের ভার ক্রমেই বেড়ে যায়।’
ফ্রান্সিসের আলোচনার মাধ্যমে রণজিৎ গুহ কী বার্তা দিতে চাইলেন? প্রথমত, ফ্রান্সিস ছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ধনতন্ত্রের পন্থি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষিপণ্য চলাচলের ওপরে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার অবসান। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থাকে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বহির্বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত প্রকার অভ্যন্তরীণ শুল্ক উচ্ছেদ করতে। আমরা দেখেছি একটু আগেই যে সমস্ত প্রকার পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে ভূসম্পত্তির ওপরে একটিমাত্র কর বসিয়ে খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে আদায় করার প্রস্তাব। সাধারণভাবে মোগল রাজশক্তির অনুসরণে তিনি চেয়েছিলেন খাজনার অপেক্ষাকৃত পরিমিত ও অপরিবর্তনীয় হার। তিনি চেয়েছিলেন ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা; জমিদার ও রায়তের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে দরকষাকষির সম্পর্ক; এবং সেই সুবাদে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষের নিরসন, এবং ব্রিটিশরাজের আয় ও রাজনৈতিক সমর্থনের যুগপৎ সম্প্রসারণ।
দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে লাটসভায় যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা ছিল তখনকার বিচারে প্রাগ্রসর। সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক। কিন্তু ফ্রান্সিসের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর প্রস্তাব কলোনিয়াল পরিবেশে পড়ে বিপরীতধর্মী চেহারা নিল। অবাধ প্রতিযোগিতার ধার দিয়েও গেল না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা মেট্রোপলিতে অবস্থানরত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। উদাহরণত, ফ্রান্সিস চেয়েছিলেন কোম্পানির ‘সাপ্লাই ব্যবসা’ করার জন্য খোলা টেন্ডারে কোনোরকম বৈষম্য না রেখে সমস্ত দেশি ব্যবসায়ীকেই কনট্র্যাক্ট নেবার সুযোগ দেওয়া হোক। এতে করে কলকাতায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গড়ে উঠবে এবং আখেরে কোম্পানিরই লাভ হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসের অবাধ বাণিজ্যের প্রশস্তি কোম্পানির কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থা পূর্বাপর বজায় রইল। ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা পেল বটে, কিন্তু ফ্রান্সিস যাদের ভেবে জমিদারদের কাছে ভূমির অধিকার দিতে চাইলেন তারা মূলত এই সংস্কারের বাইরে থাকল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলভোগী হলো এক শহুরে নব্য-ধনী সম্প্রদায়, যারা ছিল কোম্পানিরই সাথে জড়িত ব্যবসায়ী-আমলা-মুৎসুদ্দী। এরাই নতুন জমিদার ও নতুন তালুকদার হয়ে রাজত্ব করবে পরবর্তী দেড়শ বছর ধরে। ফ্রান্সিস যাদের মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখলেন ধনবাদী বিকাশের যুক্তিতে, তারা কালক্রমে জমি কর্ষণের অধিকারও হারাল। ফ্রান্সিসের উদ্ভাবিত জমিদার-রায়তের ‘স্বেচ্ছা-চুক্তির’ সম্ভাবনা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। তপন রায়চৌধুরী গুনে দেখিয়েছেন যে বরিশালের কিছু এলাকায় জমিদার ও প্রকৃত কৃষক-প্রজার মাঝে ৩২-স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল উনিশ শতকে। প্রাগ-ব্রিটিশ পর্বে পুরোনো জমিদার-পুরোনো রায়তের মধ্যে (ফ্রান্সিসের ভাষায়) ‘স্বাভাবিক স্বার্থ ও সম্পর্কের যে পারস্পরিক বন্ধন ছিল’ তা প্রায় সর্বাংশে ধসে পড়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উত্তর নতুন পরিস্থিতিতে। কেন এমন হলো সে প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর– ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও ইউরোপের পুঁজিবাদ গোড়া থেকেই ভিন্ন নিয়ম মেনে অগ্রসর হচ্ছিল। একেই পার্থ চ্যাটার্জী পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন– ‘কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স’। মেট্টোপলির জন্য যে নিয়ম খাটে, কলোনির জন্য সে নিয়ম খাটে না। উপনিবেশের পরিস্থিতিতে অবাধ ধনতন্ত্রের যৌক্তিক নিয়ম কার্যকর করা যায় না। সেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাও সহজে চালু করা যায় না। রাজশক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ আর সব বিবেচনাকে ছাড়িয়ে যায়। সেখানে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়েও কৃষকের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থেaর মধ্যে স্থান পায় না। অন্তত বহুকাল পর্যন্ত পায়নি। যতদিন পর্যন্ত কৃষকেরা নিজেরাই তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলেছে, অথবা কখনও কখনও নীরবেই প্রতিবাদ করেছে প্রতিদিনের নিঃশব্দ প্রতিরোধে। রণজিৎ গুহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লেখার প্রায় কুড়ি বছর বাদে এ নিয়ে বিস্তৃত লিখবেন। কৃষক-বিদ্রোহ (বিদ্রোহ করা ছাড়া তার আর কী উপায় থাকছে তখন) এই প্রথম বড় আকারে স্থান পাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায়।
রণজিৎ গুহ ও নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর ইতিহাস-চর্চা
পর্ব : ০১

১। প্রান্তবর্তী মানুষ
রণজিৎ গুহকে নিয়ে তাঁর প্রায় শতায়ু জীবনের অবসানের পর পত্রপত্রিকায় লেখালিখি অব্যাহত রয়েছে। জীবদ্দশাতে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। তার পেছনে একটি কারণ ছিল যে তিনি নিজেকে কিছুটা সচেতনভাবেই যেন প্রান্তবর্তী করে রেখে দিয়েছিলেন। মেইনস্ট্রিম বনাম বিকল্প ইতিহাস-চর্চার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তিনি হয়তো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন আরও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেটা না করে তিনি নিজেকে রেখে দিয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স বা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অপেক্ষাকৃত নির্জন অবস্থানে। এটা হয়তো ছিল তাঁর সচেতন সিদ্ধান্ত। নিরিবিলি ধ্যানকেন্দ্রী দূরত্বে বসে অবলোকন করা সহজ মেইনস্ট্রিমের ইতিহাস-চর্চার গতি-প্রকৃতি। যেমন করে আদিবাসীরা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে অবলোকন করে ঔপনিবেশিক সেনাদলকে।
‘পলিটিকস অব নোলেজের’ কথাই যদি বলি, তবে সে রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রান্তবর্তী মানুষদের পক্ষে লড়াইয়ে পুরোধা যোদ্ধা ছিলেন রণজিৎ গুহ। একাধারে এই যুদ্ধের পরিকল্পক, সংগঠক, নির্দেশদাতা ও যোদ্ধা।
রণজিতের জন্ম হয়েছিল বরিশালের সিদ্ধকাঠিতে, মৃত্যু ভিয়েনায়। শেষের দশ-পনেরো বছর তাঁর খুব কাছের দু’তিনজন আত্মার আত্মীয় সাব-অলটার্ন স্টাডিজের সাথে যুক্ত গবেষক ছাড়া প্রায় কারও সাথেই যোগাযোগ রাখতেন না তিনি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেশ চক্রবর্তী; হয়তো আরও কেউ কেউ। শুনেছি পরিবার-স্বজনদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তার কারণ জানা নেই, তবে কিছুটা যোগাযোগ বোধ করি একমাত্র তাঁর ছোট ভাইয়ের মেয়ে দেবারতির সাথে থেকে থাকবে। এর কারণ শুধু অনুমানই করা চলে। কলকাতার বনেদি মধ্যবিত্তের মধ্যে আধা-সামন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব নানাভাবেই উঁকি-ঝুঁকি দিত এমনকি সত্তর-আশির দশকেও। ডোমেস্টিসিটির ঘেরাটোপে বদ্ধ হয়ে ছটপট করত অনেক প্রাণ– তারা সেকালের মতো অন্তঃপুরবাসিনী না হলেও তাদের গতিবিধি খড়ির গণ্ডিতে বাঁধা। ঘরের কাজ ও বাইরের কাজ উভয় দিকই তাদের সামলাতে হতো। এসব আচার রণজিতের ভালো লাগেনি, এমনকি এ নিয়ে তাঁর মাকেও অনুযোগ করতে দ্বিধা করেননি। একবার রণজিৎ তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী মেখ্টিল্ডকে নিয়ে ক্যানবেরা থেকে কলকাতায় এলেন। উদ্দেশ্য মায়ের সাথে পরিচয় করানো। এ নিয়ে রণজিতের ভাইঝি দেবারতি পরবর্তী সময়ে লিখেছে:
“That visit of Jethu and Jethima was my first introduction to the idea of ‘personal is political’. During that visit, I often saw Jethu getting angry with his mother, as she made my mother had her meal at the very end after serving everyone else. The goodies, the bigger fish, the bigger glass of milk- all were for the family’s men, while most of the household chores were done by my Ma (mother) alone, day in and day out.”
দেবারতি এ-ও দাবি করেছে যে, এইসব আধা-সামন্তবাদী নিগ্রহ ক্রমাগত অবলোকনের কারণেই রণজিৎ একপর্যায়ে কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবার বা শ্রেণির ওপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন : ‘Jethu blamed it on the patriarchal.’ এমনকি একপর্যায়ে, দেবারতির মা যখন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন, রণজিৎ ‘broke all his ties with his mother and never visited her again.’ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পেছনে ছিল সামন্তবাদী মানসিকতার প্রতি তীব্র বিরুদ্ধাচরণ– তা সে ঘরেই হোক বা বাইরেই হোক। ইতিহাস-চর্চা করতে গিয়ে যিনি সবসময়ে ‘পলিটিকস অব নোলেজ’ নিয়ে সজাগ থেকেছেন, ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনেও তিনি এ বিষয়ে– বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে– বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে ‘এক্সট্রিম’ মনে হতে পারে, কিন্তু এক অর্থে তিনি চরমপন্থিই ছিলেন বিশুদ্ধতম অর্থে। রণজিৎ কথাটার মধ্যেই ‘রণ’ লুকিয়ে আছে। যুদ্ধে জয়ী হলেন কিনা, সেটা মহাকালই বলবে। কিন্তু আজীবন যুদ্ধরত ছিলেন, সেটা তাঁর পরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। সেজন্যই মেইনস্টিম ইতিহাস-চর্চার বিপক্ষে ক্রমাগত অবস্থান নিতে পেরেছিলেন এবং নিজেকে তার জন্য তৈরি করতে পেরেছিলেন। এবং এই প্রস্তুতি পর্বে তাঁকে চলতে হয়েছিল প্রায় একাই। আমি সেই ষাট-সত্তর দশকের কথা বলছি যখন পর্যন্ত তাঁর ধারে-পিঠে তরুণ সঙ্গীরা একে একে জমায়েত হতে শুরু করেনি। তরুণ বিদগ্ধ অনুসারীগণ– যাদের তুলনায় রণজিৎ ছিলেন প্রায় দুই দশকের বেশি বয়সী– সমবেতভাবে একটি সংগঠনের শক্তি বা মহিমা এনে দিয়েছিল কলকাতার নিস্তরঙ্গ জীবনে। রণজিতের দীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটেছিল সাব-অলটার্ন স্টাডিজের ঘোষণার মাধ্যমে। মধ্যযুগের ওপরে গবেষক ও ইতিহাসবিদ আব্দুল মোমিন চৌধুরী যেমন বলেছিলেন, রণজিৎ গুহের সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে একঝাঁক নতুন ইতিহাসবিদের সৃষ্টি। পার্থ চ্যাটার্জি, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শাহিদ আমীন, জ্ঞান পান্ডে– ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজতত্ত্ব-দর্শন-সাহিত্য বিবিধ ক্ষেত্রে বিচরণ তাঁদের। কিন্তু এর শুরুটা হয়েছিল রণজিৎ গুহকে দিয়ে। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা দিয়ে যার সূত্রপাত।
২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছায়া
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানে চিরকালের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের পত্তন হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। ওরকম একটি সুদূরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণজিৎ গুহের এতটা উৎসাহ কেন– তা নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেননা আমরা তো জানি যে, এই দীর্ঘ সময়ে এই ব্যবস্থার ভালো-মন্দ নিয়ে লেখা তো কম হয়নি, এমনকি পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত খতিয়ান নিলেও। রণজিৎ গুহ এর একটি সমকালীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হলো ফ্লুড কমিশনের রিপোর্ট। তখন চারদিকে একটা রব উঠল যে জমিদারি ব্যবস্থা অচিরেই উঠে যাচ্ছে বা এর বড় আকারের সংস্কার হতে যাচ্ছে। কলকাতা বা ঢাকার (হিন্দু) মধ্যবিত্ত সমাজ– যারা এই ব্যবস্থার ছায়ায় এতকাল লালিত-পালিত হয়েছে– তারা আকস্মিক ভয়ে যেন কুঁকড়ে গেল। রণজিৎ গুহ এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন:
‘আমার বাবা ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। জীবিকার প্রয়োজনে অনেক বই পড়তেন ও কিনতেন। একদিন দেখি ফ্লুড কমিশনের রিপোর্ট ছয় খণ্ড এসে গেছে। শুনেছিলাম যে তাতে নাকি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি ছাপা হয়েছে। কৃষকসভা যে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত গণ-সংগঠন তা জানা ছিল। তাই কলেজ কামিয়ে রিপোর্টটা নিয়ে বসে গেলাম। সেই পড়ার ফলেই গ্রাম-সমাজে ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আমার বালকবয়সের কৌতূহল প্রথম যৌবনে রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় রূপায়িত হয় এবং কালক্রমে আমাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করে।
তবে ভূমিস্বত্ব নিয়ে যে আলোচনা ও বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল মহামন্দা ও মহাযুদ্ধের যুগে, তার সঙ্গে, আপাতদৃষ্টিতে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে লেখা আমার রচনার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না– না বিষয়বস্তুতে, না দৃষ্টিভঙ্গিতে। জমিদারি প্রথার তৎকালীন সংকট ও তা সমাধানের উপায় কী, তা আমার জিজ্ঞাসা নয়। আমার প্রশ্নও সেই সংকটকে ছুঁয়েছে, তবে সরলে নয় তির্যকে: অর্থাৎ সাম্প্রতিকে নয়– অতীতে দেড়শ বছরের ব্যবধানে, প্রত্যক্ষের প্রতীয়মানতায় নয়– ধারণায়, লক্ষণে নয়– কারণে। কেন, এদিক থেকে, আমার ইতিহাস-চিন্তা উন্মার্গগামী হলো? উত্তরে আমি কেবল এটুকু বলতে পারি যে, অপরিসর গ্রাম্য পরিবেশে কিছু অসংগতির আভাসে যেমন বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম প্রথম বয়সে, তেমনি আবার যৌবনে আরও বড় মাপের আরেকটু জটিল অসংগতি-প্যারাডক্স আমার সংশয়-প্রবণতাকে উত্তেজিত করে।
আমি তখন এমএ ক্লাসে এক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের কাছে ইংরেজ রাজত্বে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়া নিচ্ছি। সেই সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল প্রবক্তা ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে লাট কাউন্সিলে ওয়ারেন হেস্টিংসের মতানৈক্যের বিবরণ পড়ে আমার যেন মনে হচ্ছিল যে, রাজস্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বার্থে বাংলার কৃষিতে এক প্রকার ধনতন্ত্রের প্রবর্তন করাই ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্য। অথচ ফ্লুড কমিশনের রিপোর্টে সংকলিত বিবৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেই বন্দোবস্তের জোরেই জমিদারি প্রথা গ্রাম-সমাজে আধাসামন্ত শোষণ ও সংস্কৃতিকে এতকাল কায়েম রাখতে পেরেছে। তাহলে কি বুঝতে হবে যে মূল পরিকল্পনাটিতেই এমন কিছু স্ববিরোধিতা ছিল, যা তার ধারণারই মর্মস্থ এবং যার ফলে তত্ত্বে ও প্রয়োগে সামঞ্জস্য ঘটতে পারেনি? ভাবি, এই অসংগতি কি আমারই মিথ্যা অনুমান, নাকি ছিটেফোঁটা ঐতিহাসিক সত্য তাতে থাকলেও থাকতে পারে?
কী করে সেই সংশয়ের নিরসন হয় জানি না, অথচ তা মন থেকে সরাতেও পারি না। তাই মরিয়া হয়ে অধ্যাপক মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞেস করে বসলুম, আর তিনিও সোজাসুজি উত্তর দিলেন– থাক, এখন ওসব থাক, আগে পরীক্ষাটা ভালো করে দাও, তারপরে দেখা যাবে। তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার সাফল্য কামনা করেন বলেই সেই রকম উপদেশ দিলেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা যে বাগ মানে না। নানা বই উল্টোই, উত্তর খুঁজি। মাঝে মাঝে দু-এক ঝলক আলো এসে পড়ে এখান থেকে ওখান থেকে, মনে হয় যা ভাবছি তা হয়তো অবান্তর নয়। কিন্তু এমন কোনো তথ্য মিলছে না যে তার ওপর নির্ভর করে সঠিক কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়।’
এই ধাঁধার কারণটি কী? এলিয়ট বলেছিলেন– ‘Between the idea and reality/Falls the Shadow’ ev ‘Between the conception and creation/Falls the Shadow’. এই ধাঁধা কি সে রকমই কিছু: ‘ভেবেছিলাম এক, আর হলো আরেক। শিব গড়তে বাঁদর গড়া?’ আপাতদৃষ্টিতে যেটি কেবল ‘আইডিয়ার ইতিহাস’, রণজিৎ গুহের হাতে পড়ে তা অন্য এক টুইস্ট পেল। প্রথম পর্যায়ের ধাঁধা ছিল এরকম। ব্রিটিশরা তো এ দেশে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন করতে চেয়েছিল এবং তারা আশা করেছিল যে, এটি করা হলে জমিতে বিনিয়োগের প্রতি জমির মালিকের আগ্রহ বাড়বে এবং কালক্রমে একটি পুঁজিবাদী খামার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যেমনটা হয়েছিল ইউরোপে, কিন্তু তা না হয়ে এক ধরনের ‘সামন্তবাদী’ বা ‘আধা-সামন্তবাদী’ ব্যবস্থার জন্ম হলো কেন পুঁজিবাদের পরিবর্তে?
১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন যাঁরা চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি তো জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক ছিলেন। রণজিৎ তাঁকে অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথের সাথে অনেক ক্ষেত্রে তুলনা করেছেন প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার মানদণ্ডে। তাহলে তিনি কেন বুঝতে পারছিলেন না যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে যে-ব্যবস্থা বাংলার কৃষিতে পত্তন হতে যাচ্ছে, তা কৃষককুলের সর্বনাশ বয়ে আনবে (কতটা সর্বনাশ সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদেশের কৃষক’-এর পাঠক মাত্রেই জানেন)।
[ক্রমশ]
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ৭টি বৈশিষ্ট্য
[পূর্বে প্রকাশিতের পর] [শেষ পর্ব]

জবাবে শেখ মুজিব বললেন: শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতীক্ষায় তোমরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে চাও, করো। কিন্তু আমি সে পথেই যাব না। যে দেশে শ্রমিকের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং কৃষকের সংগঠন ও চেতনার স্তর নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, সে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রত্যাশায় কালক্ষেপ করতে আমি রাজি নই।
এক, প্রথমে পাকিস্তান থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ নির্মূল করব। দুই, এ দেশে আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। তিন, সভ্য জগতে কোনো রাষ্ট্রই ধর্মের ওপর ভিত্তি করে চলতে পারে না। রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। চার, এমন কতকগুলো অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া উত্থাপন করতে যাচ্ছি যাতে শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও মেহনতি মানুষ সকল সম্পদের মালিক হয়; রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্বে সেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলাম: উপরিউক্ত চারটি দফা যদি আদায়ই হয়, তবে সে তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে না, হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ধরনের একটা কিছু। কিন্তু মেহনতি মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য ও কর্মসূচি দিতে হবে। উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রে শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত জনগণের অবস্থান কীরূপ দাঁড়াবে সে প্রশ্নেরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাব থাকতে হবে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচিতে।
জবাবে মুজিব বললেন: ‘ধীরে ধীরে যেতে হবে, ধাপে ধাপে যেতে হবে। শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত মানুষের জন্যই তো আমাদের সংগ্রাম। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন এবং তার কর্মসূচি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে যে পারা যাবে না সে সম্পর্কে আমি সজাগ, আমি নিশ্চিত।’
এই ম্যানিফেস্টো-ধারার বিবৃতিকে নিছক ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেসির’ তথা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ‘ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিজম’-এর অনুবর্তী বললে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ধারণাটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করা হবে। আবার একে প্রথাগত সোভিয়েত-চীনের ধারার সমাজতন্ত্র বললেও অন্যায় করা হবে। উভয় বিচারই তথ্যনিষ্ঠ হবে না। এখানেই তার ‘গণতন্ত্রের হাত ধরে চলা সমাজতন্ত্রের’ বিশেষত্ব। কতিপয় গোষ্ঠীর কাছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যাক এটা যেমন তিনি চান না, তেমনি চান না কোনো একনায়কত্বের শাসন।
বর্তমান নিবন্ধ থেকে কয়েকটি প্রবণতা বেরিয়ে এসেছে– যা নিয়ে আরও কাজ করা দরকার– তা এই পর্যায়ে দাখিল করব।
১. উন্নত ধনতন্ত্রের বেশ কিছু দেশে যে ধরনের ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’ পাই, বা প্রথাগত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে অতীতে (এবং বর্তমানে কোন কোন দেশে) যে ধরনের ‘স্টেট সোশ্যালিজম’ দেখতে হয়েছে, তার বাইরে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর নিকটবৃত্তের প্রগতিশীল সহকর্মীদের। এ দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতাই তাঁদেরকে নতুন পথ খুঁজতে বাধ্য করেছিল।
২. এই নতুন পথের নাম ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’। বাহাত্তরের সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’ (Preamble) অংশেই একে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল ‘গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের’ পথ হিসেবে। এই সংজ্ঞা বাহাত্তরের গণপরিষদের সংবিধান আলোচনার সময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নিকট সহকর্মীরা বহুবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ‘প্রস্তাবনা’ অংশে উল্লিখিত উদ্ধৃতি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে সবচেয়ে যথাযথ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে ধারণ করে:
‘আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা‒ যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।’
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বহুদিন থেকে। এ বিষয়ে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কমিটমেন্ট ছিল। এ নিয়ে প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৬৪ সালের পুনরুজ্জীবিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টোতে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচির’ ঘোষণায় সমাজতন্ত্রের প্রতি কমিটমেন্ট সুষ্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। এই পূর্ব-ইতিহাস জানলে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতন্ত্রের দাবি সাহসের সাথে উল্লিখিত হয়েছিল। নির্বাচনের মুখে কিছুটা বাড়তি ঝুঁকি নিয়েই শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও সমাজতন্ত্রের ধারায় সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি তোলার জন্য অসম্ভব সৎসাহস থাকা দরকার। বিশেষত পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিরূপ পরিস্থিতিতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথাই বলা হয়েছিল:
‘আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।’
এই নির্বাচনী ইশতেহারেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল ‘জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলিসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা,’ তবে এ ক্ষেত্রে ‘বেসরকারি পর্যায়ে নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুবিধে’ রাখা হয়েছিল ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য। এ ছাড়া বলা হয়েছিল ‘জমিদারি, জায়গিরদারি, সরদারি প্রথার বিলুপ্তি সাধনের কথা’। পরিষ্কারভাবে অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছিল ‘সব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করার কথা’ এবং সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকের মতোই যাতে ‘সমান অধিকার ভোগ’ করে এই প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ ছিল। অনেকের চোখেই এটি ছিল পাকিস্তানের দুই অংশ জুড়ে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তরফে প্রায় নিশ্চিতভাবেই অতিরিক্ত নির্বাচনী ঝুঁকি নেওয়া, বিশেষত পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিতে। কিন্তু সমানাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পূর্বাপর অবিচল।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার তথা সমাজতন্ত্রের প্রতি এই অঙ্গীকার আরও গভীর হয়। মুজিবনগরে বাংলাদেশ পরিষদের সদস্যবর্গের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, ‘অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমরা বহুপূর্বেই গ্রহণ করেছি। এ প্রশ্নে কারও মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত মালিকানা হ্রাস করতেই হবে। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক মালিকানা অর্জন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হতে হবে।’
৪. এই পর্যায়ে অবশ্য এটাও বলা দরকার যে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণাটির ‘দুই অংশই’ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৭ জুনের ভাষণে স্পষ্ট করে এ কথা বলেছিলেন, ‘আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।’ এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুসারী–যিনি ‘লিবার্টি প্রিন্সিপালকে’ প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং যিনি ভেবেছিলেন ব্যক্তিস্বার্থকে বাদ দিলে প্রগতির চাকা রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
মোট কথা, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার স্বাধীনতার পরে হঠাৎ করে বা কেবল বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নকালে গড়ে ওঠেনি। দেশি-বিদেশি পারিপার্শ্বিক শক্তির চাপে বা প্রভাবে এটি উদ্ভূত হয়নি। সংবিধানের চার স্তম্ভও তেমনি নিছক স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উদ্ভাবন নয়। এর পেছনে ছিল দীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পরম্পরা, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৫. ধারাবাহিকভাবে গড়ে ওঠা এবং ক্রমাগতভাবে উচ্চারিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পেছনে প্রেরণা এসেছিল বিভিন্ন সূত্র থেকে। নিশ্চিতভাবেই আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট একটি পরোক্ষ প্রভাব রেখেছিল ইউরোপের– বিশেষত উন্নত ধনবাদী দেশসমূহের– ‘সোশ্যাল স্টেট’, ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’, ‘সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’ প্রভৃতি ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে। পরোক্ষ প্রভাব রেখেছিল প্রথাগত সমাজতান্ত্রিক দেশের তখনকার দিনের অগ্রগতিও। ১৯১৭ সালের পর থেকেই সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল উন্নত ধনবাদী দেশসমূহের তরফে কম্পিটিটিভ ‘সোশ্যাল পলিসি’ গ্রহণের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিম ইউরোপের উন্নত ধনবাদী নানা দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ধারা এবং রাশিয়া, চীনসহ পূর্ব ইউরোপের নানা সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রাথমিক উন্নয়ন সাফল্য এই দুটি দিকই তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন মুজিবের এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অনেক আগে থাকতেই। এ ক্ষেত্রে পঠন-পাঠনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা তো ছিলই; কাজে এসেছিল প্রত্যক্ষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও। প্রায় সত্তর ছুঁইছুঁই রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ১৯৫২ সালে তরুণ শেখ মুজিবের নয়াচীন ভ্রমণ, যেখানে তিনি প্রথমবারের মতো অনুভব করলেন রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থাকলে কত অনায়াসে সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘সুযোগের সমতা’ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক প্রয়োজনকে নিশ্চিত করা যায়। যদিও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মুজিব প্রশংসার পাশাপাশি নয়াচীনের সমালোচনাও করেছেন‒ বিশেষত মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের অভাব ঘটছে এই আশঙ্কা করে। যে রকম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্ট্যালিনের রাশিয়ায় একনায়কের ছায়া দেখতে পেয়ে।
৬. বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ওপরে পরোক্ষ প্রভাব এসেছিল বাঙালির ‘সমাজতান্ত্রিক’ ঐতিহ্য ও সাম্যচিন্তার সূত্রেও। রাজনীতি-সচেতন ও সংস্কৃতিমনা শেখ মুজিব ও তাঁর নিকটবৃত্তের সহকর্মীরা বাঙালির ‘প্রগতিশীল’ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ছিলেন এই ঐতিহ্যের দুটি প্রধান স্তম্ভ। ‘সাম্যের’ বঙ্কিম থেকে ‘লাঙলের’ সাম্যবাদী নজরুল; ‘রাশিয়ার চিঠি’ ও ‘সভ্যতার সংকটের’ রবীন্দ্রনাথ থেকে ‘সুলতানার স্বপ্নের’ বেগম রোকেয়া; ‘রায়তের কথার’ প্রমথ চৌধুরী থেকে ‘শাশ্বত বঙ্গের’ কাজী আব্দুল ওদুদ বাঙালির প্রগতিশীল চিন্তার প্রবাহে একেকটি মাইলস্টোন। এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। এদের যাপিত জীবন ও লেখনীর মধ্য থেকে একটি সমৃদ্ধ উদারনৈতিক সামাজিক ন্যায়বিচারমুখীন ‘সমাজতান্ত্রিক’ সমাজের আদর্শ ক্রমশ স্পষ্ট অবয়ব নিয়েছিল, যা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নিকটবৃত্তের মানসভুবনকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে থাকবে। বিশেষত এদের প্রায় সকলের লেখনীর মধ্যেই ছিল চোখে পড়ার মতো সামন্তবিরোধী ভাবধারা, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এর ফলে কৃষি ও কৃষকের সমস্যা এবং সক্রিয় জোট নিরপেক্ষতার নীতি স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সম্মুখসারির ইস্যু হিসেবে চলে আসে।
এর সাথে যুক্ত করতে হয় চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট দশকের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। সেসব দেশ-কাঁপানো ঘটনাবলি যার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ; সাতচল্লিশের দেশভাগ; পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক নীতি; পঞ্চাশের দশকের নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-শান্তি আন্দোলন; ‘বাইশ পরিবারের’ সৃষ্টি; রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ; পূর্ব বাংলার দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন; জাতিগত ও আঞ্চলিক বৈষম্য; অগণতান্ত্রিক আচরণ ও গণবিরোধী নীতি-পদক্ষেপ ইত্যাদি ছিল জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া তত্ত্বের কিছু জরুরি উপকরণ। এসবই মুজিবকে সমৃদ্ধ করেছে– পূর্বনির্ধারিতভাবে নির্দিষ্ট করেছে বাহাত্তর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভ। এসব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের বিবরণ ছাড়া বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ বা আদলকে শুধু অর্থনৈতিক যুক্তির নিরিখে ঠিক স্পষ্ট করে চেনা যায় না।
৭. বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্যকে বর্তমান প্রবন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: (ক) বিভিন্ন ধরনের মালিকানার সহাবস্থান বা ‘মিশ্র অর্থনীতি’; (খ) অর্থনৈতিক বাস্তবতাবাদ বা ইকোনমিক প্র্যাগমেটিজম; (গ) একচেটিয়া (মনোপলি) পুঁজির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান; (ঘ) ‘সুযোগের সমতা (ইকুয়ালিটি অব অপরচ্যুনিটি) ও ‘ফলাফলের সমতা’ (‘ইকুয়ালিটি অব আউটকাম’); (ঙ) নানামাত্রিক শোষণের অবসান; (চ) তীক্ষ্ণ জোটনিরপেক্ষতা বা ‘র্যাডিক্যাল নন-এলাইনমেন্ট’; এবং (ছ) ক্রমান্বয়বাদীতা বা গ্র্যাজুয়ালিজম। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের দাবি করে। সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এরা এমন কতগুলো দিক তুলে ধরেছে; যা প্রথাগত সমাজতন্ত্রের মধ্যে নেই, অথবা থাকলেও নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে উপস্থিত।
‘মিশ্র অর্থনৈতিক’ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে বিভিন্ন মালিকানা-সম্পর্কের একত্রে উপস্থিতি ও তার গুরুত্ব। এর অর্থ, যা কিছু সামাজিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান ও গরিবমুখী বণ্টনের জন্য ফলদায়ী হবে সেই মালিকানা-সম্পর্ককেই জনকল্যাণের স্বার্থে স্বীকার করে নেওয়া হবে ‘পরিকল্পনা’ গ্রহণের সময়ে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে বা মালিকানায় থাকবে জাতীয় স্বার্থের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত সকল খাত; যা সরাসরিভাবে সামষ্টিক কল্যাণের বা ‘পাবলিক গুড’-এর বণ্টনের সাথে জড়িত। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিপণন-নির্ভর ‘সমবায়ী মালিকানাকে’ উৎসাহিত করা হবে। ব্যক্তিমালিকানাকে যথাবিহিতভাবে বিকশিত হতে দেওয়া হবে, অনেক ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকারও দেওয়া যাবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পুঁজিপতি শ্রেণিকে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার বা প্রভাব-বিস্তার করার মতো অবস্থানে যেতে দেওয়া হবে না।
ইকোনমিক প্র্যাগমেটিজমের নীতি বলছে যা কিছু জনকল্যাণের জন্য উপকারী, সেই নীতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ‘পরিকল্পনা’, ‘বাজার’ এবং ‘সামাজিক উদ্যোগের’ মধ্যে তুলনামূলক ঝোঁক কেমন দাঁড়াবে সেটি ঠিক করবে অর্থনৈতিক প্রয়োজন, প্রশাসনিক সামর্থ্য এবং সেই সময়ের অর্থনৈতিক বিশ্ববাস্তবতা। অর্থাৎ কোনো পূর্বনির্ধারিত ডগমা বা আইডিওলজি নয়, বাস্তবে কোন নীতি কতটা ফলপ্রসূ সেই নিরিখে নীতিমালা নেওয়া হবে বা বদলানো হবে। দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং সব পেশার ও জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত মানব-উন্নয়ন নিশ্চিত করাই হবে প্রধান লক্ষ্য। এ ছাড়া যথাসম্ভব গরিববান্ধব প্রবৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টনের জন্য বাস্তবোচিত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত-বিরোধিতা হবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনোমতেই অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতে কতিপয় ব্যবসা-গোষ্ঠীর একচেটিয়া রাজ বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঘনীভবন/কেন্দ্রীভবন হতে দেওয়া যাবে না। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র তার জাতীয়করণ নীতি, কর-রাজস্ব নীতি, মুদ্রা ও আর্থিক নীতি পরিচালিত করবে। বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্য খাতে অনাদায়ী মন্দ ও খেলাপি ঋণের একটি বড় অংশ জড়ো হয়ে থাকলে সেসব উদ্যোগকে ‘মিশ্র মালিকানায়’ নিয়ে আসা সম্ভব। খেলাপি ঋণের সমপরিমাণ মূল্যের শেয়ার সরকারি মালিকানায় ন্যস্ত করা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নতিতে সকল প্রকার প্রণোদনা ও উৎসাহ দেওয়া হবে সকল শ্রেণির উদ্যোক্তাদের জন্য।
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে শুধু ‘সুযোগের সমতার’ বিধান করলেই চলবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে আরও সমতামুখীন হচ্ছে কিনা সমাজ-অর্থনীতি, সেটিও দেখতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত আয়-বণ্টন নীতি গ্রহণ করতে হবে; সামাজিক নিরাপত্তা সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে; সবার জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বাস্তবায়ন করতে হবে; সকলের জন্য ‘গ্রহণযোগ্য’ পেনশন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; সবার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; মানবপুঁজি বিকাশের মাধ্যমে উন্নত পেশা বাছাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং সেই সুবাদে আয়-বৈষম্য বিশেষত ইন্টার-জেনারেশনাল ইনইকুয়ালিটি কমিয়ে আনতে হবে। একই সাথে সমাজের নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসমূহ যাতে কালক্রমে উচ্চ আয়ের মানুষের সাথে এবং অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমপর্যায়ে যেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-পদক্ষেপ নেবে রাষ্ট্র। এর জন্য চাই প্রগতিশীল আয়কর ও সম্পদকর এবং ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ’ পাওয়ার ব্যবস্থা– সর্বস্তরের পেশা ও শ্রেণির মানুষের জন্য। অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে নারীদের ‘অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন’ ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ঘরে-বাইরে নারী-পুরুষের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য দূরীভূত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ছকে কোনো ছাড় নেই।
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্র ও তার বিদেশ নীতি পরিচালিত হবে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে। এই নীতি সবার সাথে বন্ধুত্বের নীতিতে বিশ্বাসী, তবে সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদবিরোধী। এটি কোনো বহিঃশক্তির অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। এক কথায়, বিদেশ নীতি র্যাডিক্যাল ধারার জোটনিরপেক্ষতার অবস্থানকে অনুসরণ করবে, যেমনটা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সময়ে।
সবশেষে, বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কাছের ও দূরের লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় বিধান করবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কৌশলে কোনো পূর্বনির্ধারিত ছক বা মডেল নেই। এ ক্ষেত্রে কাছের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের আশু চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা আর দূরের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, যেখানে প্রাথমিক ও মৌলিক প্রয়োজনই শুধু পূরণ হবে না, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ বৈষয়িক ও আত্মিক উভয়বিধ বিকাশকে লালন করা হবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, সে লক্ষ্যের দিকে রাতারাতি যাওয়া সম্ভব হবে না। যেতে হবে পর্যায়ক্রমে, স্টেপ-বাই-স্টেপ, প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে অতিক্রম করে, অর্থাৎ গ্র্যাজুয়ালি। কেউ বলবেন, নিও-লিবারেল গভর্নমেন্টালিটি বা বাজার অর্থনীতির যুগে এসবই স্বপ্ন, কিন্তু এটি একটি সুন্দর ও সাহসী স্বপ্ন, যার পেছনে ছোটা চলে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নিকটবৃত্তের সহকর্মীরা ১৯৭১ সালে এই স্বপ্নই দেখেছিলেন। আজকের বাংলাদেশেও এর তাৎপর্য অস্বীকার করার নয়।
[বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত]
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ৭টি বৈশিষ্ট্য
অধ্যায়:: ১৬ [চলমান] [পূর্বে প্রকাশিতের পর]

১৬.৬। র্যাডিক্যাল নন-এলাইনমেন্ট
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রগতিশীল বিদেশনীতি। এটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের একটি তুলনামূলকভাবে অনালোচিত দিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী অবস্থান আরও মনোযোগের দাবি রাখে। ‘এ ক্ষেত্রে কারও সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব’ বললে পুরোটা বলা হয় না। এ জন্য বোঝা দরকার বঙ্গবন্ধুর ‘র্যাডিক্যাল নন-এলাইনমেন্ট’-এর মতো প্রাগ্রসর অবস্থানকে। এটিকে শুধু স্বাধীনতা-উত্তর বাস্তবতায় গৃহীত এক কুশলী বৈদেশিক নীতি-পদক্ষেপ হিসেবে দেখলে খাটো করা হবে। এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান বঙ্গবন্ধুর মনে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছিল। এর স্পষ্ট প্রতিফলন প্রথম লক্ষ্য করা যায় ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থে। সেখানে শেখ মুজিব গিয়েছিলেন ‘পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স’ শীর্ষক শান্তি-সম্মেলনে অংশ নিতে। তরুণ মুজিব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:
“অনেকে বলতে পারেন কম্যুনিস্টদের শান্তি সম্মেলনে আপনারা যোগদান করবেন কেন? আপনারা তো কম্যুনিস্ট না। কথাটা সত্য যে আমরা কম্যুনিস্ট না। তথাপি দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের শান্তি সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক, যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, ‘আমরা শান্তি চাই’। কারণ, যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে– যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কাঁচামাল চালান দিতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস জোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে।”
১৯৫২ সালে লেখা এটি, অথচ ২০২২-২৩ সালের ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে এর প্রাসঙ্গিকতা আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়ে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ:
১। ১৯৪৯ সালের ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টোতে’ বলা হয়েছিল:
‘পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করার সমস্ত প্রচেষ্টায় পাকিস্তানকে অংশীদার হইতে হইবে এবং শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সর্বব্যাপী বিজয় অভিযানকে জয়যুক্ত করিবার জন্য অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ও জনকল্যাণকর আন্দোলন ও কর্মধারায় সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা করিতে হইবে। দুনিয়ার সমস্ত জালিমদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মজলুমদিগকে মুক্ত করাই হইবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।’
২। নয়াচীন ভ্রমণের এক বছর পরে ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের ‘সাংগঠনিক রিপোর্টে’ (শেখ মুজিব কর্তৃক উত্থাপিত) বলা হয়েছিল:
‘তাই আওয়ামী লীগ … সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী জোটের সাথে সম্পর্কহীন সক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ এই নীতির অনুকূলে শান্তি আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। … শান্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়া আওয়ামী মুসলিম লীগ যুগ যুগব্যাপী মানুষের প্রতিভা ও সাধনার প্রতিভূ মানবসভ্যতা রক্ষার জন্য বিশ্বধ্বংসী রণপাগল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ আজ নীতিগতভাবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির মহান নেতা।’
৩। ১৯৬৪ সালের পুনরুজ্জীবিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে প্রথমবারের মতো শেখ মুজিব উচ্চারণ করেন দলের বিদেশনীতি:
‘সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হিংসা কারও বিরুদ্ধে নহে (Friendship to all, Malice to none) আওয়ামী লীগ বৈদেশিক সম্পর্কে এই নীতিতে বিশ্বাস করে। বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ সহযোগিতা প্রদান করিবে। বৈদেশিক সম্পর্ক অনড় (static) থাকিতে পারে না। উহা সচল ও পরিবর্তন সাপেক্ষ (Dynamic) এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তববাদে বিশ্বাসী। তবে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীননীতি গ্রহণে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী।’
৪। ১৯৬৭ সালে গৃহীত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ‘নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণা অর্থাৎ (ম্যানিফেস্টো)’তে বলা হয়েছিল:
‘আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং একনায়কত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের প্রতি আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থন থাকিবে।’
৫। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল:
“পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনোমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না এজন্য আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হয়। আমরা ইতোমধ্যে ‘সিয়াটো’, ‘সেন্টো’ ও অন্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে, সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।”
৬। বাহাত্তরের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল: রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়-অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।’
এ-ই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ‘র্যাডিক্যাল নন-এলাইনমেন্ট’-এর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
১৬.৭। গ্র্যাজুয়ালিজম
বঙ্গবন্ধু তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আরেকটি মৌল বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সেটির এককথায় নাম– ধাপে ধাপে চলা, পর্যায়ক্রমতা (ইংরেজিতে Gradualism)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠার পথ এক দীর্ঘ অভিযাত্রার পথ। এখানে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কারণে নানামুখী কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কখনও বাঁয়ে, কখনও ডানে সরে এসে; কখনও দু’কদম পিছিয়ে গিয়ে, কখনও দ্রুত পথ অতিক্রম করে চলতে হয়। এজন্য ‘বিশুদ্ধপন্থি’ হলে চলে না। একেই মাইকেল হ্যারিংটন (১৯৮৯) অভিহিত করেছিলেন ‘ভিশনারি গ্র্যাজুয়ালিজম’ বলে।
এজন্যই খোন্দকার মো. ইলিয়াসকে (পূর্বে-উদ্ধৃত কথোপকথনে) মুজিব বলেছিলেন, ‘ধীরে ধীরে যেতে হবে, ধাপে ধাপে যেতে হবে’ এ দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে। এই যাত্রাপথে পরিকল্পনা ও বাজার-অর্থনীতি উভয়কেই আশ্রয় করতে হয়; ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সামষ্টিক জমায়েত উভয়কেই উৎসাহিত করতে হয়; স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা উভয়কেই বিবেচনায় নিতে হয়। সমাজের aspiration এবং custom-culture কে হিসেবে নিতে হয়। এর বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা দলিলের প্রথম অধ্যায়ে। যেখানে দেশের উন্নয়নের ধারা বেগবান করার জন্য ‘দূরের’ সাম্যবাদী লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ‘কাছের’ উন্নয়ন-সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি আমি এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় তুলে ধরছি। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা দলিলের মধ্যে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত আলোচিত হয়েছিল।
প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার দলিলে যথার্থই বলা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য দরকার বিদ্যমান পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন: ‘Without this assessment a country may adopt a programme which is unrealistic, either too ambitious or too modest’। বলা হয়েছিল, গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলোকে আগে শনাক্ত করতে হবে। যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বা প্রাগ-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ, সেটা একলহমায় করা যাবে না: ‘Depending upon the objective conditions of the society, this may have to be done in stages’। দলিলে যথার্থই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল উৎপাদন-বৃদ্ধির ওপরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিতে কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য সচল করাই হচ্ছে আশু কর্তব্য: ‘In an underdeveloped economy such as Bangladesh, the socialist transformation of the economy must accompany the growth of productive forces. It has to be clearly understood that anything which hampers increase in productivity or growth of productive forces and dissipates the meagre resources of the country in unproductive activities and unnecessary consumption is in contradiction with the basic principles of socialism.’
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতাকে বেগবান করে ‘productive forces’ কে আগে বিকশিত করে এবং পরে ‘production relations’-এর পরিবর্তনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভবত এই ছিল পরিকল্পনাবিদদের মত। পরিকল্পনা দলিলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য আরও যে ফ্যাক্টরের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে ‘সমাজতন্ত্র গড়ার ক্যাডার’ গড়ে তোলা। পরবর্তীকালে বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণার সময় বঙ্গবন্ধু এই দিকটির প্রতি বিশেষ জোর দেন। পরিকল্পনা দলিলে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল, সমাজের মূল্যবোধ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে ব্যাপকভাবে না দাঁড়ালে কখনোই উত্তরণ সফল হবে না: ‘As long as the broad masses are unable to accept the norms of behaviour necessary for a radical transformation of society, no amount of socialist policy adopted by the government can usher in socialism.’ আর সমাজের মূল্যবোধ শুধু সরকারি আমলাদের কাজের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় না। এখানে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা প্রশিক্ষিত আত্মনিবেদিত ‘ক্যাডার’ হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এনজিও লিটারেচারের পরিভাষায় এই ক্যাডাররা সমাজ-পরিবর্তনের ‘এনিমেটার’ বা ‘catalytic agent’ হিসেবে কাজ করতে পারে। এটা বলে পরিকল্পনা দলিলে মন্তব্য করা হয় যে, কাজটা সহজ নয় আদৌ: ‘Before socialism becomes a reality, the task is to educate the public about the need for social change. The cadres are the instruments through which the task is carried out. We must, however, be aware of the fact that a cadre is as likely to degenerate as any one else.’
কেন এসব সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছিল পরিকল্পনা দলিলে সেদিন? স্পষ্টতই, দলিল-প্রণেতারা কোনো কল্পলোকে বিচরণ করতে চাননি এবং মাঠ-পর্যায়ের বাস্তবতাকে পরিকল্পনার মধ্যে বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। সমস্যা হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ‘আত্মোৎসর্গ’ করার আহ্বান শুধু সাময়িক কালের জন্য কাজ করে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতকে আগেই উদ্ধৃত করেছি যেখানে তিনি বলছেন স্বার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলে অর্থনীতির চাকা একপর্যায়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মানব-চরিত্রের স্বার্থপরতার দিক এবং সমাজ-কল্যাণে ব্রতী পরার্থপরতার দিক উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধন করেই ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম যে-কথা দিয়ে তাঁর পরিকল্পনা দলিলের ভূমিকা শেষ করেছিলেন তা আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে: ‘Development is a slow and painful process. It means present sacrifice for future gains. It is specially painful for a country at a very low level of living such as Bangladesh where an increasing and significant reliance is to be placed on domestic resources for development. We can make the sacrifice, which is so essential for development, socially tolerable only if it is equitably shared by all.’ এটা বলেই তিনি সতর্ক করলেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের: ‘The room for flexibility is so small, the ability of the socio-economic system to withstand the effects of mistakes and waste is so severely limited that in the use of scarce resources as well as in experimenting with new institutions, great caution and extreme care need to be exercised.’
কৃষিপ্রধান দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার সমস্যা বঙ্গবন্ধু গভীরভাবেই জানতেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কী ধরনের অর্থনীতি সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের ভেতরেই নানা মত চালু ছিল। সেই অস্পষ্ট আদলের সমাজতন্ত্রে কীভাবে পৌঁছানো যাবে সেটারও কোনো রেডিমেড ব্লুপ্রিন্ট তার হাতে ছিল না সেদিন। তার চারপাশের বুদ্ধিজীবীরাও সেটা স্পষ্ট জানতেন না, যেমন জানতেন না (এবং এখনও বলতে গেলে প্রায় জানেন না) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীরা। শুধু জানতেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করে গতিশীল উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আর জানা ছিল যে, শোষণমুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবেই, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে আটকে থাকাটাই মানব-ইতিহাসের চূড়ান্ত বিধিলিপি নয়। এখানে ‘চ্যালেঞ্জটা’ এত বড় যে বারবার ‘চেষ্টা’ করা ছাড়া অন্য কোনো সহজ পথ খোলা নেই। ৪ নভেম্বরের গণপরিষদ বিতর্কের সমাপনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে তাঁর মনের কথাটি বলেছিলেন:
‘সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে নাই। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না– অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। … সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে step by step এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই– সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির background নিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান– ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্যদিকে চলেছে। সেজন্য দেশের environment, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের ‘কাস্টম’, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। এক দিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই– আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।’
১৭। শেষের কথা
এবার বোধ হয় উপসংহারের দিকে যাওয়া চলে। প্রথমে আসি বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতাদর্শ প্রসঙ্গে। আমরা দেখেছি যে, বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ছিল একটি অসাধারণ ‘পলিটিক্যাল টেস্টামেন্ট’, যা থেকে তাঁর অর্থনৈতিক মতাদর্শের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে-কথাগুলো এখানে তুলে ধরব তা ত্রিশোত্তীর্ণ মুজিবের বিশ্বাসের কথা, তাঁর মনের অন্তস্তলের কথা, কাউকে শোনাবার জন্য নয়, এসব তো আদৌ প্রকাশিতব্য ছিল না। এটি নিজের চিন্তাকে কেবল একটি স্থায়ী উপলব্ধির কাঠামো দেওয়ার প্রয়াস, যেটি কখনোই তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি, আমৃত্যু যাকে তিনি লালন করেছেন। এখানে তাঁর ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। প্রথমে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:
“চীনের জনগণ সরকারের কাজে সাহায্য করছে এটা বুঝতে কষ্ট হলো না। জনমত দেখলাম চীন সরকারের সাথে। চীন সরকার নিজেকে ‘কমিউনিস্ট সরকার’ বলে ঘোষণা করে নাই, তারা তাদের সরকারকে ‘নতুন গণতন্ত্রের কোয়ালিশন সরকার’ বলে থাকে। কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্য মতাবলম্বী লোকও সরকারের মধ্যে আছে। যদিও আমার মনে হলো কমিউনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছুই। আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিবাদী সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা।”
এটিকে কাকতালীয় বিবৃতি বলে মনে করার দরকার নেই। পরবর্তীকালে, ১৯৬৪ সালের কোনো এক সময়ে শেখ মুজিবের সাথে তার কলকাতা জীবনের সতীর্থ ‘মুজিববাদ’ বইয়ের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের বৈঠক হয়। সে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ‘পুনরুজ্জীবিত’ আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো নিয়ে। পুরো উদ্ধৃতিটি তুলে ধরতে চাই এখানে।
‘শেখ মুজিব আমাকে বললেন : তোমরা বামপন্থিরা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু করেছ, সে সংগ্রাম সম্পাদন করতে হবে আমাকেই। তাঁর মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।
আমিও হেসে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : কীভাবে?
[ক্রমশ]
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ৭টি বৈশিষ্ট্য
অধ্যায়:: ১৬ [চলমান] [পূর্বে প্রকাশিতের পর]

একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধতা করার তৃতীয় কারণটি রাজনৈতিক। ব্যক্তি-উদ্যোগের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে উৎসাহিত করতে হবে জনকল্যাণের স্বার্থে। কিন্তু দেখতে হবে এটি করতে গিয়ে ব্যক্তি-পুঁজি যেন ‘রাষ্ট্রের পলিসি’ নিয়ন্ত্রণ করার মতো রাজনৈতিক অবস্থানে যেতে না পারে। রাজনীতি ও পলিসির রথের ঘোড়ার লাগাম থাকতে হবে রাজনীতিবিদ ও রাজ-কর্মচারীদেরই হাতে–সেখানে ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়া চাই। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নিকটবৃত্তের সহকর্মীরা এক্ষেত্রে যেমন সজাগ ছিলেন, তেমনি চিন্তিতও ছিলেন এনিয়ে। সেজন্যেই ইতোমধ্যে উদ্ধৃত অংশে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, ‘ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ আমরা ততটুকুই দেব, যতটুকু উৎসাহ দিলে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রভাব ঘটাবার সুবিধা ব্যক্তি মালিকানায় থাকে না।’ স্বাভাবিকভাবেই একচেটিয়া পুঁজি বা বৃহৎ শিল্প-মালিকদের পক্ষে এই রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ আরও বেশি। একথা শুধু বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দীন আহমদই বলেননি, বলেছেন অন্য সাংসদরাও। মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ গণপরিষদ বিতর্কে অংশ নিয়ে (১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর) বলেছিলেন, ‘সাবেক পাকিস্তানে যে সমস্যা ছিল, তা দূর করার জন্য যদি মহানবীর বাণীর শত ভাগের এক ভাগও মেনে নিত, তাহলে কুখ্যাত আদমজী, দাউদ, ইস্পাহানীর মতো লোক এদেশে জন্মলাভ করতে পারত না।’ দেখা যাচ্ছে যে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই সেদিনের গণপরিষদে ‘একচেটিয়া পুঁজির’ বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের পক্ষে সমর্থন জানানো হচ্ছিল। এজন্যেই সংবিধানের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, কেবল ‘আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই’ ব্যক্তি মালিকানাকে অপারেট করতে দেওয়া হবে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বরের সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার সমাপনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায়, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে শুধু সমাজতন্ত্রই (প্রচলিত মডেলের তুলনায়) অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত হবে তা-ই নয়, এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকেও ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে। সেদিনই পুঁজির অন্যায় রাজনৈতিক প্রভাবের বিরোধিতা করে তিনি প্রথম উচ্চারণ করলেন ‘শোষিতের গণতন্ত্র’ শব্দবন্ধটি। অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারণা আছে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাকশাল প্রবর্তনের সময় বুঝি বঙ্গবন্ধু প্রথম ‘শোষিতের গণতন্ত্র’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। বস্তুত এর ব্যবহার শুরু হয় ১৯৭২ সালেই। সেদিন তিনি বলেছিলেন:
‘মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলছে দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।
আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যেসব provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে– ঐ শোষকরা যাতে protection পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক schedule-এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনসিওরেন্স-কোম্পানি, কাপড়ের কল, জুট-মিল, সুগার ইন্ডাস্ট্রি– সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষক-গোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।’
১৬.৪। ‘সুযোগের সমতা’ ও ‘ইকুয়ালিটি অব আউটকাম’
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল। অন্তত সেগুলোকে বিবেচনায় নিতে হয়েছিল। তারপরও এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ‘স্বকীয়তা’ সম্পর্কে ১৯৭২ সালের গণপরিষদে একটি সার্বিক সচেতনতা বিরাজ করছিল। এই স্বকীয়তাকে ঢাকা থেকে নির্বাচিত আবু মো. সুবেদ আলী প্রকাশ করেছিলেন এভাবে: ‘‘আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘পিপলস ক্যাপিটালিজম’ গ্রহণ করি নি। আমরা যুক্তরাজ্যের ‘ওয়েলফেয়ার স্টেটে’ও বিশ্বাস রাখিনি। একটি মাত্র দলের কর্তৃত্বে চীন ও রাশিয়ার যে সমাজতন্ত্র, তাও আমরা পূর্ণভাবে গ্রহণ করি নি।’’ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা এসেছে। এরকম একটি প্রেরণা হচ্ছে ‘সুযোগের সমতা’। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজের সকল নাগরিকের জন্য ‘সুযোগের সমতা’ সৃষ্টি করার পাশাপাশি বাস্তবে জীবনযাত্রার মানেও যতটুকু সম্ভব সমতা আনা (যাকে বলা হয়ে থাকে– ‘ইকুয়ালিটি অব আউটকাম’)। জাতিসংঘের এমডিজি ও এসডিজি-এর কল্যাণে ‘equality of opportunity’ কথাটি এখন বহুল প্রচলিত একটি ধারণা। কিন্তু এদেশে এটির প্রথম সচেতন ব্যবহার হয় ১৯৭২ সালেই। বাহাত্তরের সংবিধানের ১৯(১) ধারায় প্রথম উচ্চারিত হয় ইকুয়ালিটি অব অপরচ্যুনিটি বা সুযোগের সমতার কথা। সেখানে বলা হয়েছিল: ‘সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন’। এবং এর আগে ১৫নং ধারায় এই ‘সুযোগের সমতাকে’ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল:
‘(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;
(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।’
১৮(১) ধারায় আলাদা করে পাবলিক হেলথ্ এবং নিউট্রিশন (পুষ্টির) কথাও বলা হয়েছিল: ‘জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।’ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ‘পুষ্টির’ এই সংযোজন ছিল একটি বিরল দৃষ্টান্ত।
দেখা যাচ্ছে, আজকের ‘সোশ্যাল প্রটেকশনের’ অনেক আগেই বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ‘সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের’ কথা বলেছিল। লক্ষণীয় যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখানে ‘অধিকারের ভাষায়’ কথা বলা হচ্ছে‒ এই রাইটস্ বেইজড্ অ্যাপ্রোচের জন্ম হবে আরও বহু পরে।
একটি কথা এখানে যোগ করা দরকার। এই যে মৌলিক প্রয়োজনের জন্য ‘অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-চিকিৎসার’ ধারা বা নির্দিষ্ট করে ‘সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার’ ১৫ ধারায় বলা হলো এগুলো এলো কোন উৎস থেকে? মার্কসের লেখাটিতে বলা ছিল যে সাম্যবাদী বিকাশের প্রথম বা নিচু পর্যায়ে বণ্টননীতি হবে নিম্নরূপ: ‘From each according to his abilities, to each according to his work’। এখানে প্রত্যেকে যেন তার সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়, সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারে, এবং কাজের পরিমাণ/গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেতে পারে–এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত।
মনে হতে পারে, এগুলো বুঝি ইউরোপীয় ‘সোশ্যাল স্টেট’ বা ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’-এর ধারণা থেকে উঠে এসেছে। হয়তো পশ্চিম ইউরোপের বা উত্তর ইউরোপের ‘সামাজিক গণতন্ত্রীরা’ এর পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক রসদ জুগিয়েছেন। আসলে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু থেকে এসব দাবি ‘প্রাণের দাবি, বাঁচার দাবি’ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বিশ্বজোড়া সমাজবদলের ডাকও এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই প্রশ্নের একটি মীমাংসা পাই ড. কামাল হোসেনের ব্যাখ্যায়। ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর মৌলিক প্রয়োজন ও অধিকারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন:
‘১৯, ২০, ২১ [ধারা]–এগুলোর ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি নেই। কারণ, এগুলো বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধান থেকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে কর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। সে সম্পর্কে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়। এটা সোভিয়েত সংবিধানে রয়েছে।’
এই ৩টি অনুচ্ছেদ (১৫, ১৯ ও ২০) সংবিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘সমাজতান্ত্রিক ধারা’। বলে রাখি, ১৯(১) ধারায় ‘সুযোগের সমতা’ এবং ১৯(২) ধারায় ‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ’ এবং ‘নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন’ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। যদি ১৯(১) ধারায় বলা হয়ে থাকে সুযোগের সমতা (Equality of Opportunity)-এর কথা, ১৯(২) এবং ২০(১) ধারায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ‘Equality of Outcome’-এর প্রতি। ২০(১) ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল মার্কসের ‘গোথা কর্মসূচির সমালোচনা’ লেখাটির সূত্র ধরে ‘প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্য অনুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী’ বণ্টনের নীতি। মোদ্দা কথা, ‘সুযোগের সমতা’ যার উল্লেখ আমরা পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক দর্শনে সুপ্রচুরভাবে পাই (যেমন, জন রাউলস-এর লেখায়) বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সেখান থেকে শুরু করলেও সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে দুর্ভাবনা ছিল জন্মসূত্রে সমাজের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির দুস্তর ফারাক নিয়ে। Initial conditions- এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকলে শুধু বর্তমান সময়ে ‘সুযোগের সমতার’ দাওয়াই দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য এবং সামর্থ্যের (capability) বৈষম্য দূর করা যায় না। জন্মসূত্রে ফারাকের সাথে যুক্ত করতে হয় ‘কপালের লিখন’-এর কথাও। অনেকেই আছেন, যারা বিশুদ্ধ দুর্ভাগ্যজনিত কারণে ব্যবসায় সফল হন না, অথবা আকস্মিক ট্রমার কারণে যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারেন না– এককথায়, ‘সুযোগের সমতার’ সদ্ব্যবহার করতে পারেন না এক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি, শুধু ‘সুযোগের সমতা’ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। একারণেই বঙ্গবন্ধু ও তার নিকটতম সহকর্মীরা Equality of Opportunity-এর পাশাপাশি ‘Equality of Outcome’-এর সাংবিধানিক বিধান রেখে গেছেন। এজন্যে তারা ১৯(২) ধারায় ‘সম্পদের সুষম বণ্টন’ নীতি এবং ২০(১) ধারায় মার্কসের ‘শ্রম অনুযায়ী বণ্টন’ নীতি–এ দুই নীতিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে গেছেন। আবার পাশাপাশি ১৫(ঘ) ধারায় আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন ‘অধিকারের ভাষা’ ব্যবহার করে।
১৬.৫। নানামাত্রিক শোষণের অবসান
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজের পঞ্চম বৈশিষ্ট্যের রাজনৈতিক ও মানবিক গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্যের মূল কথা নিহিত ‘শোষণহীন সমাজ’ গড়ার অঙ্গীকারের মধ্যে। ১৯৭২ সালের ৭ই জুনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের সরলতম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন (যেটা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি): ‘এ সমাজতন্ত্র হলো বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র, তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন।’ এর পূর্বলেখ (geneological trail) অনুসরণ করলে বহু পেছনে চলে যাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালের ‘পুনরুজ্জীবিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টোতে’ আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছিল: ‘আওয়ামী লীগের আদর্শ শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য ও দুর্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।’ ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল ‘শোষণের অবসান অবশ্যই করতে হবে’ এবং তাতে বলা ছিল– ‘বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।’ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪ নং ধারায় উল্লেখ আছে– এটি ড. আম্বেদকরের ভারতীয় সংবিধানেও নেই– ‘‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে–কৃষক ও শ্রমিককে–এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।’ সবশেষে উদ্ধৃতি দিতে চাই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার দলিল থেকে। সেখানে প্রথম পরিচ্ছেদের ১.১২ অধ্যায়ের শিরোনামই ছিল– শোষণের হ্রাসকরণ (reducing exploitation)। ব্যাখ্যায় বলা ছিল: ‘Under the prevailing objective conditions elements of exploitation can only be reduced in phases if the productive process is not to be disrupted।’ এখানে বিভিন্ন দলিল থেকে ‘শোষণহীন সমাজ’ গড়ার যে অঙ্গীকার তুলে ধরা হলো তা শুধু কথার কথা ছিল না। এই অঙ্গীকার ছিল গণমানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, ‘শোষণ’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে (সংগত কারণেই) ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো সেটা ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামের কৃষক জনগোষ্ঠীর ওপরে সামন্তবাদী জমিদারি-জোতদারি-জায়গিরদারি শোষণের অবসান প্রসঙ্গে। কখনো সেটা ব্যবহৃত হয়েছে শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও সকল প্রকার ‘অন-অর্থনৈতিক শোষণ’ (extra-economic exploitation) শোষণের অবসান প্রসঙ্গে। অর্থাৎ শুধু উৎপাদনকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক শ্রেণিসমূহ– যথা, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ– তাদের ক্ষেত্রেই দৃষ্টি সীমিত থাকেনি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার ‘অনগ্রসর অংশসমূহের’ ওপরে অর্থনৈতিক ও অন-অর্থনৈতিক (সামাজিক, সাংস্কৃতিক) শোষণের অবসান অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো সেটা ব্যবহৃত হয়েছে নারীর প্রতি শোষণমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির অবসানের কল্পে। আজকের যুগে সামাজিক-ধর্মীয়-ভাষাগত-জাতিগত-লিঙ্গগত শোষণ-বঞ্চনার–বৃহত্তর অর্থে, আইডেনটিটি-পলিটিক্সের ডিসকোর্সের–অন্তর্গত ন্যারেটিভ হিসেবে পড়তে হবে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ‘শোষণহীন সমাজ’ ধারণাটিকে। একে শুধু অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা ভাবা ভুল।
সংবিধানের ১৪নং ধারায় কৃষক-শ্রমিকের পাশাপাশি ‘জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের’ কথা উল্লেখ ছিল এবং তাদের ওপরে ‘সকল প্রকার শোষণের’ অবসানের সাংবিধানিক গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল। এটি বাংলাদেশের সংবিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এ নিয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদে বেশ বিতর্কও হয়েছিল সেদিন সাংসদদের মধ্যে, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। লারমা চেয়েছিলেন ১৪নং ধারার ‘অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান’ করার প্রতিশ্রুতিকে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে। ১৪নং ধারার পর ১৪ক শীর্ষক একটি নতুন অনুচ্ছেদ তিনি সংযোগ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রস্তাবে ছিল নিম্নোক্ত সংযোজনী:
‘১৪ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নতুন অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হোক:
১৪ক। সংখ্যালঘু জাতিসমূহ ও অনগ্রসর জাতিসমূহের
(ক) ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে;
(খ) শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ-অধিকার দেওয়া হইবে; এবং
(গ) অগ্রসর জাতিসমূহের সহিত সমান পর্যায়ে উন্নত হইবার পরিপূর্ণ সুযোগ রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।’
শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংশোধনী-প্রস্তাব গণপরিষদে গৃহীত হলো না। অথচ ভুল শব্দের ব্যবহার (‘সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর জাতি’) সত্ত্বেও একথা তো পরিষ্কার, তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে শুধু ‘অনগ্রসর অংশসমূহের’ ওপরে শোষণের অবসানের প্রতিশ্রুতিই নয়, সেটাকে আরও সাংবিধানিক ভাবে দৃঢ় করা হোক কংক্রিট পদক্ষেপের মাধ্যমে। সেকারণেই তিনি বলেছিলেন, (ক) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিসংক্রান্ত ‘বিশেষ অধিকার’ সংরক্ষণ করতে হবে; এবং (খ) রাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা দিতে হবে, যাতে করে কালক্রমে তারা ‘অগ্রসর’ অংশসমূহের সাথে ‘সমান পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়’। সেদিনের আনীত সংশোধনী প্রস্তাবে ‘জাতিসমূহ’ কথাটি বাদ দিয়ে লারমার প্রস্তাবিত মূল কথাগুলো ১৪নং অনুচ্ছেদে বাড়তি অনুচ্ছেদ হিসেবে রাখলে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না। সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদে এসব কথা তো এমনিতেই ছিল (যেমন ২৮ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে)। বরং এটা করা হলে পরবর্তীকালে সৃষ্ট জাতিগত বা নৃগোষ্ঠীগত মনঃকষ্ট তৈরি হওয়ার কোনো যৌক্তিক অবকাশই হয়তো আর থাকত না।
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ‘শোষণহীন’ সমাজ প্রতিষ্ঠার আরেকটি অর্থ হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান। এটি নানা অনুচ্ছেদেই এসেছে গুরুত্বের সাথে। সংবিধানের ‘মৌলিক অধিকারের’ অংশে ২৮(১) ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে:
(১) ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।’
(২) ‘নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।’
নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টিকে শিক্ষা লাভ, বিনোদন, ‘সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা’ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারের বিষয়টি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেসম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর পূর্ব-উপলব্ধি ছিল। এজন্যেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রয়োজনীয় নীতি-পদক্ষেপ নিতে কালবিলম্ব করেননি বঙ্গবন্ধু। ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থে তরুণ মুজিব লিখছেন:
“পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট” এই পুরানো প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে।…নয়াচীনের মেয়েরা আজকাল জমিতে, ফ্যাক্টরিতে, কলে-কারখানাতে, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে।…যে সমস্ত ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, সরকারি অফিসে আমি গিয়াছি সেখানেই দেখতে পেয়েছি মেয়েরা কাজ করছে; তাদের সংখ্যা স্থানে স্থানে শতকরা ৪০ জনের ওপরে। নয়াচীনের উন্নতির প্রধান কারণ পুরুষ ও মহিলা আজ সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের কাজে। সমানভাবে সাড়া দিয়াছে জাতিগঠনমূলক কাজে। তাই জাতি আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে।’
অন্যত্র তিনি বলেছেন, ‘সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনোদিন বড় হতে পারে না।’
[ক্রমশ]
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ৭টি বৈশিষ্ট্য
পর্ব :: ১৬

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোর আলোচনার মূল বার্তা ছিল তিনটি। প্রথমত, প্রথাগত সমাজতন্ত্র ও প্রথাগত (পুঁজিবাদী) গণতন্ত্রের বাইরে ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের’ একটি নিজস্ব অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য রয়ে গেছে। মার্কসীয় ও অ-মার্কসীয় উভয় ধারার মধ্য থেকেই এটি যুক্তিতর্ক-রসদ আহরণ করেছে। বার্নস্টাইন থেকে বার্নি স্যান্ডার্স, রবীন্দ্রনাথ থেকে বঙ্গবন্ধু নানাভাবে ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের’ প্যারাডাইম দাঁড় করাতে সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নানা দেশে নানা রূপ ধারণ করতে পারে দেশ-জাতি-ভূগোল এসব অবস্থা ভেদে। তবে বিভিন্ন সম্ভাব্য রূপ সত্ত্বেও আমরা মোটা দাগে দুটি ‘টাইপ’ আবিষ্কার করতে পারি। প্রথম ‘টাইপটি’ হচ্ছে, উন্নত ধনবাদী দেশের ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’, যার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষে জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসডিপি)-এর দ্বারা। এই ধারার মূলে ছিল ১৮৯১ সালের ‘এরফুর্ট প্রোগ্রাম’। এই কর্মসূচি ‘সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল’-এর অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় পার্টিসমূহের প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে, ‘সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল’ থেকে বের হয়ে গিয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিসমূহ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারাকে আরও বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় করে তোলে, এবং এসব দেশে রাষ্ট্রক্ষমতাতেও আসতে সক্ষম হয়। এর প্রভাব পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এই পারস্পরিক প্রভাবের কারণে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ব্যাপক চর্চার পাশাপাশি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতেও ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’ প্রতিষ্ঠা পায়। পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের এসব দেশে কথিত সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ও ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক ধারণা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এ দুইয়ের মধ্যে অন্তিম লক্ষ্যে‒ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির বেশ পার্থক্যও ছিল। যা হোক, যেটা বিশেষভাবে বলা দরকার, প্রথম টাইপের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মডেল তৃতীয় বিশ্বের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক ছিল না। এর মূল কারণ, ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে অবস্থার মৌলিক পার্থক্য। যেন দুই পৃথিবী দুই ‘ভিন্ন সময়ে’ বাস করছিল: একটি ছিল ‘আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসি’ আর আরেকটি ছিল প্রাগ-আধুনিক পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান ‘দুর্বল গণতন্ত্র’। দুই জায়গাতেই শোষণ-বঞ্চনা, শ্রেণিভেদ-জাতিভেদ ছিল, কিন্তু সোশ্যাল কনটেস্ট, জনগণের মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছিল ভিন্ন। এই শেষোক্ত পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদল কীরূপ দাঁড়াতে পারে তা নির্ধারণের দায়িত্ব এসে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের ওপরে।
তৃতীয়ত, উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কারণে প্রথম থেকেই পুঁজিবাদ-বিরোধিতা ও সমাজতন্ত্র-অভিমুখীনতা একটি স্পষ্ট ধারা হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে চলছিল রণজিৎ গুহ যাকে বলেছেন‒ Dominance without hegemony, কোনো প্রকার ‘সম্মতি’ আদায় করা ছাড়াই প্রত্যক্ষ নিবিড় শোষণ বা প্রভুত্ব-আরোপ। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বেগম রোকেয়া, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, কাজী আব্দুল ওদুদ, এমনকি পরবর্তীকালে এ দেশের প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক সমাজতন্ত্রের প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁরা সকলেই গণতন্ত্রও চেয়েছেন, আবার সমাজতন্ত্রও চেয়েছেন– একটির জন্য অন্যটিকে বিসর্জন দিতে রাজি হননি। বঙ্কিম লিখেছেন ‘সাম্য’; রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (উগ্র) জাতীয়তাবাদ বিরোধী ‘ন্যাশনালিজম’ প্রবন্ধত্রয়ী, ‘রাশিয়ার চিঠি’ এবং ‘সভ্যতার সংকট’; বিবেকানন্দ লিখেছেন ‘জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র’; নজরুল সম্পাদনা করেছেন বামপন্থি পত্রিকা ‘লাঙল’, লিখেছেন ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগুচ্ছ এবং ‘মৃত্যুক্ষুধা’ শীর্ষক রাজনৈতিক উপন্যাস, যেখানে সরাসরিভাবে সর্বহারা, রুশ বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণির কথা এসেছে; প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন ‘রায়তের কথা’; আবুল হুসেন লিখেছেন ‘বাংলার বলশী’; এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। রাজনীতিবিদেরাও– মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ সবাই বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই আদর্শকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উন্নত ধনবাদী দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বলা চলে না। তারা অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিচার করে বুঝেছিলেন, পশ্চিম ইউরোপের স্টাইলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, এমনকি ‘ওয়েলফেয়ার স্টেট’ গঠন করা এ দেশের কোনো সরকারের পক্ষে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণেই প্রায়-অসম্ভব। আবার, তারা এ-ও বুঝেছিলেন যে ভিন্নতর সামাজিক-শ্রেণি কাঠামো, রক্ষণশীল মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি মনোযোগ এবং গণতন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এসবের কারণে বাংলাদেশের মতো সমাজ-পটভূমিতে চীন-সোভিয়েত স্টাইলের অথরেটিরিয়ান সোশ্যালিজমের প্রতিষ্ঠা করাও প্রায়-অসম্ভব প্রস্তাব। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার নিকটবৃত্তের সহকর্মীদের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যেমন একটি সম্ভাবনার আলো দেখিয়েছিল, তেমনি ছুড়ে দিয়েছিল এক বিশাল তাত্ত্বিক ও পলিসি চ্যালেঞ্জ। এসবের প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে স্বাধীনতার আগে ও পরে শেখ মুজিবের বিভিন্ন স্টেটমেন্ট ও ভাষণ; তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্বে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ডকুমেন্টস্; ১৯৬৬ সালের ৬-দফা, ১৯৬৯ সালের ১১-দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও ১৯৭২ সালের সংবিধান; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল; স্বাধীনতার পরে স্বল্প সময়ের মধ্যে হাতে নেওয়া প্রতিকূল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিশ্ব-পরিস্থিতিতে গৃহীত বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপ। এসবের বিচারের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের একটি ‘অবয়ব’ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যার তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও আদর্শিক প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনেও সুপ্রচুরভাবেই রয়ে গেছে। এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের আয়ত্তের বাইরে। আমরা প্রবন্ধের এই অংশে শুধু বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রধান সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।
১৬.১। মিশ্র অর্থনীতি
বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এর ‘মিশ্র অর্থনৈতিক’ চরিত্র। যদিও ‘মিশ্র অর্থনীতি’ (mixed economy) শব্দটি তখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ডিসকোর্সের ‘লেঙ্কিনে’ প্রবেশ করেনি– বাহাত্তর সালের গণপরিষদ বিতর্কে কদাচিৎ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে– তাহলেও পরিকল্পনাবিদদের ‘অ্যাপ্রোচ’ ছিল এটাই। সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা ছিল ‘রাষ্ট্রীয়’, ‘সমবায়ী’ ও ‘ব্যক্তিমালিকানার’ কথা। একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশকে আধুনিক শিল্পোন্নত স্তরে উন্নীত করতে গেলে সচেতনভাবে বহু-গাঠনিকতাকে (multistructuralism) লালন করতে হবে। পশ্চাৎপদ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ শুধু দীর্ঘই হবে না, এটি হবে বহু-গাঠনিক কাঠামোসম্পন্ন। অর্থাৎ, এখানে যেমন থাকবে খুদে উৎপাদকদের খাত, তেমনি থাকবে সমবায়ী খাত; এর পাশাপাশি থাকবে পুঁজিবাদী খাত নানা টাইপের; আর থাকবে শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। এ সম্পর্কে লেনিন ‘নিউ ইকোনমিক পলিসি’ নীতিমালা আলোচনার সূত্রে পথিকৃত আলোচনা করেছিলেন সেখানে থাকতে হবে শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত– যেটি পরিকল্পনামতো স্ট্র্যাটেজিক খাতসমূহে বিনিয়োগ করবে এবং জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় আয়/সম্পদ পুনর্বণ্টনমূলক পদক্ষেপও নেবে। স্বাধীনতার উষালগ্নে অবাঙালি মালিকানাধীন কলকারখানা পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদেরকে জাতীয়করণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বাংলাদেশে ‘জাতীয়করণ’ নীতি যথেষ্ট কড়াকড়ি করে করা হয়; এজন্যে সংবিধানে ৪৭নং ধারা যুক্ত করা হয় যার বলে যে কোনো শিল্পকে জাতীয় স্বার্থে ‘ন্যাশনালাইজ’ করার এখতিয়ার সংসদকে দেওয়া হয়। কোনো কোর্ট বা বিচার ব্যবস্থা এই জাতীয়করণের উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত না। বঙ্গবন্ধু এই কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। কারণ, তার যৌক্তিক ভয় ছিল যে বিদেশ থেকে কলকারখানার অবাঙালি মালিকরা উচ্চ আদালতে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে পারেন। ঠিক একই কারণে বাঙালি মালিকানাধীন ইপিআইডিসি-সমর্থিত মুষ্টিমেয় কলকারখানাকেও জাতীয়করণ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। কেননা, একে তো এদের একটি অংশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন; তদুপরি যারা করেননি, তাদেরকে তাদের পাকিস্তান আমলের কলকারখানা রাখতে দিলে অবাঙালি মালিকানাধীন কলকারখানাকে জাতীয়করণ করা যেত না, বা সেটা উচ্চ আদালতে অবধারিতভাবে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ত। যেহেতু ১৯৭২ সালে এ দেশের বৃহদায়তন কলকারখানার সিংহভাগই (প্রায় ৮০ শতাংশ শিল্প-পরিসম্পদ) ছিল অবাঙালি মালিকানাধীন, এই প্রশ্নে কোনো ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ ছিল না সদ্য-স্বাধীন দেশের সরকারের পক্ষে। এটি বঙ্গবন্ধু ও তার নিকটতম সহকর্মীদের মনে ‘হাই-প্রায়োরিটি’ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত ছিল সেদিন। সংবিধানের খসড়া লেখার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু যে দুটো বিষয়ের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেগুলো হলো জাতীয়করণ ও জাতীয়করণকৃত শিল্পের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঝুঁকির বিষয়টি (অন্যটি ছিল সাম্প্রদায়িকতা দমন ও ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব)। অন্য আরেকটি বিষয়ও বঙ্গবন্ধুর তৎকালের উদ্বেগের কারণ ছিল। সেটি হচ্ছে Floor Crossing নিবারণের জন্য ৭০ নম্বর ধারা। বিষয়টি জটিল। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলের তিক্ত স্মৃতি মুজিবের মনে জাগরূক ছিল। ১৯৫০-র দশকে ‘ফ্লোর ক্রসিং’-এর কারণে প্রায়ই মন্ত্রিসভা ভেঙে যেত এবং সরকারের পতন হতো। সরাসরি সম্পর্কিত নয় বলে সেটি এখানে আলোচনা করা হলো না।
আনিসুজ্জামান (২০১৫) লিখেছেন:
‘১৯৭২ সালে বাজেট-বক্তৃতার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিশেষ বিশেষ শিল্প ও বাণিজ্যের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রতিশ্রুতি ছিল। তাছাড়া ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় এবং তার আগে-পরে নানা দলের ইশতেহারে কিংবা নানারকম সম্মেলনের প্রস্তাবে ব্যাংক, বীমা, চা ও পাটশিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি ছিল। এ নিয়ে বড় একটা আপত্তিও শোনা যায়নি। কিন্তু ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে যখন প্রধান প্রধান শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হলো, তখন ‘গেল, গেল’ রব পড়ে গেল এবং এই ব্যবস্থাগ্রহণের মধ্যে ভারতের স্বার্থ বা ইঙ্গিত আবিষ্কৃত হলো। সমালোচনা প্রবল হয় বাঙালি মালিকানাধীন শিল্প অধিগ্রহণ করায়। কিন্তু ব্যাংক-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করলে বাঙালি পরিচালনাধীন ব্যাংক তার থেকে বাদ দেওয়া কিংবা পাটশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করলে বাঙালি মালিকানাধীন পাটশিল্প তার আয়ত্তের বাইরে রাখা তো সম্ভবপর ছিল না। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান আমলের সরকারি উদ্যোগ এবং পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি …।’
‘গেল, গেল’ রব সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য আরও খতিয়ে দেখা দরকার। সেসময়ের দৈনিক পত্রপত্রিকা (‘হলিডে’, ‘হককথা’ সহ) ঘেঁটে আমি এর সপক্ষে কোনো ‘প্রকাশিত প্রমাণ’ পাইনি। বরং ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি জাতীয়করণ কর্মসূচি ঘোষণার সময়ে অতি অল্পই ‘বিরুদ্ধতা’ শনাক্ত করা যায়। জাতীয়করণ করার কারণে রাতারাতি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের চৌহদ্দি বেড়ে যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাত শক্তিশালী করা হলেও এই মডেলের সাথে ‘স্টেট-সোশ্যালিজম’ ধারার এক মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রের ছকে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বৃহদায়তন কলকারখানার প্রায় ১০০ শতাংশ জাতীয়করণ করে নেয়। কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ– যথা সোভিয়েত ইউনিয়নে– মাঝারি শিল্পের পুরোটাই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পকে প্রায় পুরোপুরিভাবে ব্যক্তি খাতে রাখা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, বেসরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমশ ‘সিলিং বাড়িয়ে’ বৃহদায়তন শিল্প-বাণিজ্য খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন উদ্যোক্তা শ্রেণির পলিসি গ্রহণের মাত্রা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার মাত্রাকেও (level of entrepreneurship) বিবেচনায় নিতে হবে। রুশ গবেষক সের্গেই বারানভের মতে, পাকিস্তান আমলের শেষে বৃহদায়তন শিল্প খাতে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার সংখ্যা একেবারেই হাতে-গোনা ছিল নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মাত্র ১৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ। বাদবাকি যারা বাঙালি উদ্যোক্তা ছিলেন, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী বা ইন্ডেন্টার, যাদের আধুনিক কলকারখানা চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না ১৯৭২ সালে। এটি বিশিষ্ট শিল্পপতি সালমান এফ রহমানও একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন।
এই ধারার ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের কাছে ইচ্ছে করলেই চটজলদি বৃহদায়তন শিল্প– তা সে একদা অবাঙালি মালিকানাধীন ‘পরিত্যক্ত’ কারখানাই হোক, আর নতুন করে সরকারি ব্যাংক-অর্থায়িত শিল্পই হোক– নিঃশর্তে ছেড়ে দেওয়া যেত না। এটাই প্রধান কারণ কেন ১৯৭৬-১৯৮১ পর্বে অ-সমাজতান্ত্রিক জেনারেল জিয়ার আমলে কোনো কলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়কৃত করা হয়নি– এমনকি পাকিস্তান আমলের বাঙালি মালিকানাধীন কলকারখানাগুলোও ঐ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। জিয়া চেষ্টা করেছিলেন সরকারি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ ঢেলে নতুন শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি করার, যারা ভবিষ্যতে আধুনিক কলকারখানা চালাতে সক্ষম হবেন। এই নীতি সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯৭৬-৮১ পর্বে প্রদত্ত ১০০০ কোটি টাকা শিল্পঋণের ৯০ শতাংশই আর কখনোই ব্যাংকে ফেরত আসেনি এবং সেদিনের ঋণগ্রহীতাদের ৯৬ শতাংশই ছিলেন আউটরাইট ডিফল্টার। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, ১৯৭২-৭৫ পর্বে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির ‘বিকাশের মাত্রা’ বিবেচনায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ‘সিলিং’ যথোপযুক্তই ছিল অর্থাৎ বেশিও ইনসেনটিভ দেওয়া হয়নি, কমও ইনসেনটিভ দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদের ব্যাখ্যাই যথার্থ:
‘ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়েছে দেখে সেটার জন্য সমাজতন্ত্রের দাবিদার একটা দল বলেছে যে, এটা সমাজতন্ত্র হয়নি, আবার আর একটা দল বলেছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা যা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিকভাবে দেওয়া হয়নি, খুব কম দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত মালিকরা বড় ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয়, দুই দলের কথায় যখন তাঁরা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের কারও কথায় কর্ণপাত না করে আমরা যেটা দিয়েছি, সেটাই তাঁদের গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এটা সুসামঞ্জস্য হয়েছে এবং সুসমন্বিত হয়েছে।’
১৬.২। ইকোনমিক প্র্যাগমেটিজম
প্রথাগত সমাজতন্ত্রের তুলনায় বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের একটি মৌলিক পার্থক্য হলো এটি রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনৈতিক উদ্যোগকে পূর্বনির্ধারিত আদর্শের বা আইডিওলজির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে একটি প্র্যাগমেটিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছে।
এই প্র্যাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ প্রথাগত সমাজতন্ত্রের মতো ১০০% বা ৮০-৯০ শতাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ‘কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার’ অর্থনীতি না করে মালিকানা-সম্পর্কের (property relations) বিষয়টিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত করা। কৃষিপ্রধান ও বন্যা/দুর্যোগপ্রবণ অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির অপরিসীম গুরুত্ব বঙ্গবন্ধুর নানা বক্তৃতায় সেসময়ে উঠে এসেছে। এর জন্য সবধরনের মালিকানা-সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছিল মুজিব সরকার। দ্বিতীয় কথা হলো, বিভিন্ন ধরনের মালিকানার মধ্যে ‘অনুপাত’ কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। কোনটা কখন কোন খাতে প্রাধান্য পাবে, সেই প্রশ্নটিকে কালক্রমে পরিবর্তনযোগ্য বলে ভাবা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে সরকারি-বেসরকারি-সমবায়ী খাতের মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব পরিবর্তিত হবে এটাই ছিল উপলব্ধি। গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য– উদাহরণস্বরূপ বলছি– ব্যক্তিমালিকানাধীন স্ব-উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায়ী-উদ্যোগ বা গ্রুপ-উদ্যোগ বা যৌথ-উদ্যোগের ভূমিকা সময়ের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মোট কথা, বিভিন্ন মালিকানা সম্পর্কের মধ্যে রেশিও (Ratio) কী দাঁড়াবে, ‘পরিকল্পনা’ ও ‘বাজার’-এর মধ্যে তুলনামূলক ঝোঁক কীরূপ হবে, তা খাতভেদে এবং সময়ের সাথে বদলাবে। দেশের মানুষের পছন্দ-অপছন্দও এখানে বিবেচনায় নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি বারবার এনেছেন ‘মাল্টিপারপাস’ কো-অপারেটিভের ওপরে নিরীক্ষামূলক কর্মসূচি ঘোষণার সময়ে: কোনোক্রমেই জবরদস্তি করা যাবে না; ব্যাপারটা পরীক্ষামূলকভাবে সফল হলে তবেই ছড়িয়ে দেওয়া হবে; যার যার কৃষিজমি তারই মালিকানায় থাকবে। প্রথাগত সমাজতন্ত্রে এই বিষয়গুলো মানা হয় না। জবরদস্তিমূলক সমবায়ীকরণ এ কারণেই ঘটেছে নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে, আর এর প্রতিফল উৎপাদন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হয়েছে মারাত্মক। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে মালিকানা-সম্পর্কের বিষয়টিকে উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও জনকল্যাণের অধীন পলিসি-ডিসিশন হিসেবে দেখা হয়েছে। এ জন্যই আমরা বলেছি যে, ইকোনমিক প্র্যাগমেটিজম হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্রের এই ‘বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান’ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদেশি অর্থনীতিবিদ-বিশেষজ্ঞদেরও নজর পড়েছিল।
শেখ মুজিবের প্রায়োগিক ও বাস্তবজ্ঞানমণ্ডিত মনের কথা যখন উঠলই, তখন আরও একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চাই। পাকিস্তানের অপশাসনের দিনগুলোর কথা মনে করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তার ‘ক্রমান্বয়ে চলার নীতি’: ‘আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বৎসর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না, আমি অ্যাডভেনচারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের নাজের জেনে করি, চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি সবকিছু নিয়ে।’ এদিক থেকে দেখলে শেখ মুজিব ও দেং শিয়াও পিং-এর মধ্যে একটি প্রচণ্ড মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এরা দু’জনেই ছিলেন (রবিনসনের ভাষায়) ‘প্র্যাকটিক্যাল ও প্র্যাগমেটিক’ মনের মানুষ। দেং শিয়াও পিং-এর মতো মুজিবও বলতে পারতেন যে বিড়াল কালো না সাদা সেটা বড় কথা নয়, এটি ইঁদুর ধরতে পারে কিনা সেটাই চূড়ান্তভাবে বিচার্য। মুজিবও এ রকম উদাহরণ দিয়ে তার প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছেন। ‘লার্নিং বাই ডুয়িং’-এর কথা বলেছেন তিনি: ‘কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর সবচেয়ে যে বেশি শেখে সে করে শেখে।’ যারা আইডিওলজির চশমা পরে পৃথিবীটাকে দেখে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন মাটির কাছাকাছি থাকার কথা:
‘এদের আমি বলতাম, জনসাধারণ চলেছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলেছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।’
প্র্যাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, জনকল্যাণের আদর্শ বিসর্জন দেওয়া, অথবা স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য থেকে সরে আসা। সেটি স্পষ্ট হয় বঙ্গবন্ধুর পূর্বাপর ‘একচেটিয়া পুঁজি’বিরোধী অবস্থানের মধ্য দিয়ে।
১৬.৩। একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে অবস্থান
পুঁজিবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ সমার্থক ধারণা নয়, যদিও পুঁজিবাদী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে ‘মনোপলি ক্যাপিটালিজম’-এর আবির্ভাব হয়। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট ছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও অনমনীয় অবস্থান। কোনোভাবেই পাকিস্তান আমলের মতো ‘বাইশ পরিবারের’ হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্যারাডাইমের জন্য একটি মৌলিক ডাইলেমা। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হলো ক্রমশ পুঁজির ‘কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন’ (centralizaation and concentration of capital)। এর ফলে প্রতিটি খাতেই কমবেশি আগে-পরে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটতে থাকে। বিংশ শতকের গোড়া থেকে উন্নত ধনবাদী প্রতিটি দেশে (সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কসহ) কার্টেল, সিন্ডিকেট, করপোরেশন প্রভৃতি ‘মনোপলি ফরমেশন’ ঘটতে থাকে। এখনকার দুনিয়ায় ট্রান্সন্যাশনাল, মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন এবং ‘বিগ বিজনেস হাউস’ ছাড়া আধুনিক পুঁজিবাদকে কল্পনাই করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এসব বৃহৎ করপোরেট পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের (technological leadership) কারণে। এর প্রচলিত উদাহরণ হেনরি ফোর্ড থেকে বিল গেটস অবধি বিস্তৃত। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাড়তি মুনাফা লাভ এবং দ্রুত পুঁজি সঞ্চয়ন অবধারিত হওয়ায় বা করপোরেট পুঁজির বিষয়টাকে আর ক্রিটিক্যালি দেখা যাবে না, ব্যাপারটা এমন নয়। এখানে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান থেকে মূল অভিযোগ তিনটি।
প্রথমত, একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণহীন বিকাশের কারণে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়ছে সমাজে। উন্নত ধনবাদী দেশসমূহে এই লক্ষণ গত তিরিশ বছরে আরও প্রকট হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেছেন এবং লিখছেন টমাস পিকেটি (২০১৪), ইমানুয়েল সায়েজ ও গাব্রিয়েল জুকম্যান (সায়েজ ও জুকম্যান, ২০১৯)। এদের নিজস্ব রচনা এবং যৌথভাবে লেখা ‘ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট’ (দেখুন, আলভারেডো ও অন্যান্য, ২০১৮) এ বিষয়ে তথ্য-পরিসংখ্যান জড়ো করেছে। অর্থনীতিবিদরা এ ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী বিজনেস গ্রুপ ও করপোরেশনসমূহের মেজর শেয়ারহোল্ডার এবং ‘ম্যানেজেরিয়াল ক্লাস’-এর জন্য বর্ধিত হারে ক্যাপিট্যাল ও ইনকাম ট্যাক্সের প্রস্তাব করেছেন। আমাদের দেশেও বহুদিন ধরে সম্পদ করের (wealth tax) বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে, যদিও এখনও পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়নের পর্যায়ে যেতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, বিষয়টা শুধু আয়বৈষম্যের নিরিখেও বিচার করলে চলবে না। উন্নত ধনবাদী দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যেসব খাতে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের মাত্রা বেশি, সেসব খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ‘মার্কেট শেয়ার’ তত কম, এবং শেষোক্ত শিল্পে ‘মর্টালিটি রেটও’ তত বেশি। এর কারণ, বৃহৎ করপোরেট পুঁজি আইনি ও বেআইনি যে কোনোভাবেই হোক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে দেয় না। বৃহৎ পুঁজির হাউসগুলো অনেক সময় নিজেদের মধ্যে এমন কিছু প্রযুক্তিগত ও প্রোডাক্টের ফিচারগত ‘অ্যালায়েন্স’ তৈরি করে নেয়, যার ফলে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনকারীরা স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। সমুদ্রে বড় মাছের পেছনে পেছনে যেমন কিছু ছোট মাছের দল ঘুরে বেড়ায়, বৃহৎ পুঁজির কাছে আনুগত্য স্বীকার করেই কেবল ক্ষুদ্র-মাঝারি পুঁজি ‘মার্কেটে টিকে থাকার’ চেষ্টা করে। এ কারণে প্রতিটি উন্নত ধনবাদী দেশেই শক্ত ধরনের ‘এন্টি-ট্রাস্ট’ আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল গত শতকের ৫০-৬০-এর দশকেই, কিন্তু তারপরও একচেটিয়া পুঁজির ঘনীভবনকে ঠেকানো যায়নি বেশির ভাগ দেশেই। এই সমস্যাটিকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করবে।
[ক্রমশ]
