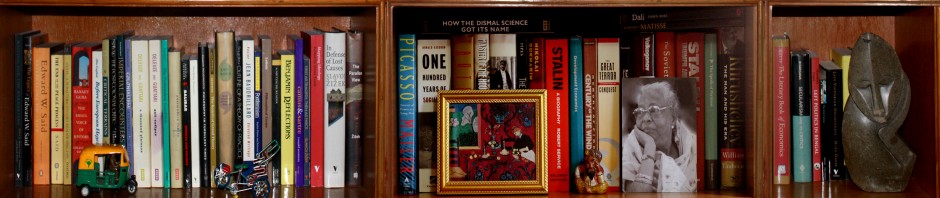পর্ব :: ১১০
[পূর্বে প্রকাশিতের পর]
অর্ধ-সত্যের ভিত্তিতে ডিজইনফরমেশন ক্যামপেইন চালানোর পটভূমি গড়ে দিয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার ঠান্ডা যুদ্ধ। ‘ঠান্ডা’ হলেও যুদ্ধের রক্তারক্তিতে সেটি প্রত্যক্ষ যুদ্ধের চেয়ে কম যায় না। ১৮ আগস্ট ১৯৭৫-এর সংখ্যায় ওয়াশিংটন পোস্ট তড়িঘড়ি করে লিখল যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে আবার সবকিছু পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে: ‘ইসলামাবাদ, পিকিং এবং ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়।’
এই সূত্রে প্রবন্ধের লেখক লুই সিমনস্ মৃত্যুর কারণও নির্দিষ্ট করলেন:
‘যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লি-মস্কোর সঙ্গে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল। অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণিকে অভিযুক্ত করেছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে, তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।’
লুই সিমনস্ আরও বললেন, ‘হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।’ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে বৃহৎ পরাশক্তির দ্বন্দ্ব, ভারত, চীন, পাকিস্তান ইত্যাকার শক্তির ভারসাম্যের সমীকরণ জড়িত এমনটাই ইঙ্গিত করা হলো।
এটা এখন অনেকটাই স্পেকুলেশনের বিষয় যে মুজিব-হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিক্সন প্রশাসন-সিআইএ জড়িত ছিল, কী ছিল না। মিজানুর রহমান খানের গবেষণাধর্মী বইটিও এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। লরেন্স লিফসুলজ্ তার ‘বাংলাদেশ :দ্য আনফিনিশড রিভোলিউশন’ বইতে স্পষ্ট ইংগিত করেছিলেন যে সিআইএ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার আয়োজন সম্পর্কে পূর্বাপর অবগত ছিল। খোন্দকার মোশতাক আমেরিকান লবির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বহুকাল থেকেই (অন্তত ১৯৭১ সাল থেকে তো বটেই)-একথা এখন প্রমাণিত। Rogue States এবং Killing Hope-র লেখক উইলিয়াম ব্লুমকে আমি চিঠি লিখেছিলাম মুজিব-হত্যায় সিআইএ-র জড়িত থাকা প্রসঙ্গে তিনি কিছু জানেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মুজিব-হত্যা তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল না। তিনি তার বইয়ে মূলত লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার ওপরেই মনোনিবেশ করেছেন। পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে একাধিক ব্যক্তিগত আলাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা সিআইএ-র জড়িত থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেননি। ঢাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে অভ্যুত্থানের বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ন্যাপ-সিপিবির পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুকে অরক্ষিত থাকার ব্যাপারে বারবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। কমরেড মণি সিংহ নিজে এ বিষয়ে বলেছিলেন, মোজাফফর আহমদও বলেছিলেন বাড়তি নিরাপত্তা গ্রহণের বিষয়ে। দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিংগার গ্রন্থের লেখক ক্রিস্টোফার হিচেন্স স্পষ্টত অবস্থান নিয়েছিলেন মুজিব-হত্যায় সিআইএ-র জড়িত থাকার পক্ষে। সেখানে হিচেনস সরাসরিভাবে অভিযোগটি তুলেছেন: ‘Kissinger was responsible for the killing of thousands of people, including Sheikh Mujibur Rahman’। একদিন নিশ্চয়ই এর পক্ষে বা বিপক্ষে অকাট্য প্রমাণ মিলবে। কোনো গোপন উইকিলিকসে ফাঁস হয়ে পড়বে মার্কিন প্রশাসনের আর্কাইভে লুকিয়ে থাকা, এখনও অপ্রকাশিত, কোনো দলিল-পত্রে বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনের দেশি-বিদেশি চক্রান্তের খুঁটিনাটি।
তবে মুজিব-হত্যার পরপরই যেভাবে ইং-মার্কিন মূলধারার পত্র-পত্রিকাগুলো সমস্বরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ক্যারেকটার-এসাসিনেশনে লেগে গিয়েছিল তা আজ কিছু অবাক করে বৈকি। তার জন্য বঙ্গবন্ধুকে শুধু ‘ডিক্টেটর’ বলে আক্রমণ করা নয়, তার পরিবারের সদস্যদের কারও কারও প্রতি কল্পিত অভিযোগ ছড়াতেও তারা সেদিন দ্বিধা করেনি। গুজবের প্রকাশ ও প্রচার করা সাধারণত সৎ সাংবাদিকতার নিয়ম-রীতিবিরুদ্ধ। প্রায় অসভ্যতার পর্যায়ে এটি পড়ে। ১৬ আগস্ট ১৯৭৫-এর সংখ্যায় ফিন্যান্সিয়াল টাইমস্ পত্রিকায় কেভিন রেপার্টি মুজিব সম্পর্কে কল্পিত অভিযোগ এনে লিখেছেন :’নিজের পরিবারের লোকজনের আর্থিক স্বার্থ আদায়ের প্রতি তার নজর ছিল। তিনি নিজে ঘুষ নিয়েছেন কিনা এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তা নেওয়ার তো তার প্রয়োজন ছিল না।…তবে অনেকেই তার ছেলেদের এবং অন্য আত্মীয়দের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।…গল্পটি সত্য না বানানো তা বিচার করতে যাওয়া অবান্তর, কারণ বহু লোক এ গল্পের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং এ গল্প বহু লোকের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়েছে।’ এই হচ্ছে পাশ্চাত্যের সৎ-সাংবাদিকতার নমুনা! দেশের সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করে- কখনও শেখ মনি, কখনও গাজী গোলাম মোস্তফাকে ঘিরে গাল-গল্প বানিয়ে এবং গুজব ছড়িয়ে। এর জন্য ঢাকার তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে মুজিববিদ্বেষী মনোবৃত্তিও কম দায়ী নয়। মুজিব খুব ভালো ছাত্র ছিলেন না; মুজিব বুদ্ধিজীবীদের অপছন্দ করেন; মুজিব সবসময় ইনসিকিওরিটিতে ভুগতে থাকেন; মুজিব তার অহমিকাবোধে আবদ্ধ; এসব কথা পাশ্চাত্যের অনেক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে অনর্গল লিখতে দ্বিধা করেননি। এভাবে ‘ফেইক নিউজ’ তারা তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে শুধু ‘হক-কথা’কে দায়ী করলে ভুল করা হবে। আজ তার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী,’ ‘আমার দেখা নয়াচীন’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ পড়ে সেদিনের জটিল-কুটিল সমালোচক স্বভাবের ঢাকার মধ্যবিত্তদের অনেকেরই কিছুটা হলেও বোধোদয় ঘটছে হয়তো। তারা এখন ভাবছেন যে শেখ মুজিবকে ‘যতটা অশিক্ষিত’ বলে মনে করে আন্ডারএস্টিমেট করেছিলাম, ততটা অশিক্ষিত তিনি নন আসলে। চিন্তাবিদ না হলেও সবকিছু নিয়েই চিন্তা করতে পারেন দেখছি! ঢাকার মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে এই অসাধুতা গত ৫০ বছর ধরে দেখে আসছি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে। ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মুজিব নাকি ইংরেজি বলতে ভুল করেছিলেন, সে নিয়ে কী হাস্য-তামাশা সেদিন মধ্যবিত্তদের ড্রইং রুমে। আজ তারাই বলছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে আমাদের তাকে বুঝতে। হি ওয়াজ আ গ্রেট, গ্রেট ম্যান।’ এই শঠতা আমাদের পীড়া দেয়। এই মধ্যবিত্তের সঙ্গে শঠতার দৌড়ে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটেছেন সেদিনের বিদেশি সাংবাদিকেরা। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করাই ভুল হয়েছিল এমন মন্তব্য ছিল তাদের। ১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারি সংখ্যায় বোস্টন হেরাল্ড মন্তব্য করেছে:
”আরও পরিহাস এই যে, যে পাকিস্তানের উৎপীড়ন থেকে তিনি তার দেশবাসীকে মুক্ত করেছিলেন, সেই পাকিস্তান আজ অধিকতর মুক্ত এবং সমৃদ্ধ। গত সোমবার ‘দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্’ প্রকাশ করেছে যে, তিন বছর আগে পরাজয় ও অবমাননা ভোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এশিয়া মহাদেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে সজীব দেশ হিসাবে দেখা দিয়েছে। যদিও এখনও গরিব দেশ, কিন্তু পাকিস্তানে অনাহারে লোক মরছে না। তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়ে চলেছে এবং ‘দি টাইমস্’ পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সরকার ধ্বংসাবশেষ কাটিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।…পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আদর্শবাদীরা যখন বাংলাদেশের মুক্তির জন্য চিৎকার করছিল, তখন আমেরিকার উচিত ছিল, পাকিস্তানকে আরও সবল সমর্থন দেওয়া।’
অবশ্য ভুট্টোর পাকিস্তানের এই প্রশংসা অচিরেই মুছে যাবে পাশ্চাত্যের সাংবাদিকবলয় থেকে। আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের পরে ঠান্ডা যুদ্ধের লড়াইয়ে বিশ্বস্ত সাথি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন জেনারেল জিয়াউল হক। এবং ভুট্টোকে ‘হঠকারী পপুলিস্ট’ বলে ছুড়ে দেওয়া হবে অস্বীকারের খাতায়।
১৫. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত প্রকল্প ও আজকের বাংলাদেশ
বাকশালের মাধ্যমে সমতামুখিন সমাজের স্বপ্টম্ন বাস্তবায়নের নতুন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বাহাত্তরের সংবিধানে যেসব অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাকশালের কর্মসূচিতে ধারণ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের একটি বড় স্তম্ভ ছিল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। সেটি বাকশালের কর্মসূচি ঘোষণার পূর্বে সেভাবে আলোচনায় আসেনি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ফলে বাহাত্তরের সংবিধান ও বাকশাল কর্মসূচিতে বিধৃত সমতামুখিন সমাজের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া হয়। শুধু ভুলে যাওয়াই নয়, অর্থনীতি-রাজনীতি চলতে থাকে এক নিষ্ঠুর অমানবিক সামরিক শাসন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫-১৯৯০ পর্বে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাই ছিল ক্ষমতাসীনদের কাছে একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সে সময়ে যারা ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদ’-এর গঠন বা তার কার্যাবলির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকতেন, তাদের প্রত্যেকেই নানা ধরনের দৈহিক-মানসিক-বৈষয়িক হয়রানির শিকার হতেন। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ১৯৭৭-১৯৮৬ সালে নিছক বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে ১৫ আগস্টের শোকসভায় উপস্থিত থাকাকে বিদেশের বাংলাদেশি দূতাবাসের কর্ণধাররা ভালো চোখে দেখতেন না। তা সে বিলেতেই হোক, আর তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নেই হোক। মৃত বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা হচ্ছে, তাকে প্রতীক রেখে তরুণ শিক্ষার্থীরা জড়ো হচ্ছে এক জায়গায়, তাকে মনে রেখে তারা সমতামুখিন সমাজের কথা বলছে, এটা জিয়া-এরশাদের সামরিক সরকার আর তাদের অধীন দূতাবাসগুলোর পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হতো। যারা সেদিন সেসব গোপন বা প্রকাশ্য সভায় জড়ো হতেন ওয়াশিংটনে, লন্ডনে, মস্কোয় কিংবা ঢাকায়; তারা ঝুঁকি নিয়েই অংশ নিতেন সেখানে। তাদের নামের তালিকা চলে যেত গোয়েন্দা দপ্তরে। জীবিত মুজিবের তুলনায় মৃত মুজিবের প্রভাব প্রতিবছরেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর নাম ক্রমশ অর্থনৈতিক সমতা, সামাজিক ন্যায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমার্থক ধারণায় পরিণত হচ্ছিল সচেতন অথবা অসচেতনভাবে। এই যোগাযোগ সময়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় গণভিত্তি পেয়েছে। আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এবং সমতামুখিন আকাঙ্ক্ষার আলোচনা তাই আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’? এ প্রশ্ন আজ উঠতেই পারে।
সমকালীন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে গতিধারা বিশ্নেষণের কাজটি বর্তমান লেখার আওতার বাইরে। কিন্তু কিছু প্রাথমিক মন্তব্য করা যায়। প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ ধারণাটি নিয়ে সর্বস্তরে (পাঠ্যবইসহ বলছি) যতটা আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল, ততটা এ দেশে এখনও হয়নি। ‘গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজতন্ত্র নির্মাণের’ বর্তমান কালের চ্যালেঞ্জ আলোচনা করার জন্য নূ্যনতম শর্ত হলোু সমাজতন্ত্রকে আগে ‘কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করা। বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতির অংশ হিসেবে ‘সমাজতন্ত্র’ ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে ঠিকই (২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে), কিন্তু এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে করা হয়নি। গণতন্ত্র ও মার্কেট-ইকোনমি রেখে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য কীভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প হতে পারে, তা নিয়ে গভীর আলোচনার দরকার রয়েছে। স্বাধীনতা, উৎপাদন-নৈপুণ্য এবং বণ্টনগত সাম্যু এই ত্রিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে সমীকরণ কষতে হবে এবং উন্নয়নের নানামাত্রিক ঝোঁকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কাজটি সহজ নয়। সামাজিক ন্যায়-দর্শনের একটি উদাহরণ দিয়ে সমস্যাটি চিহ্নিত করা যায়।
[ক্রমশ]