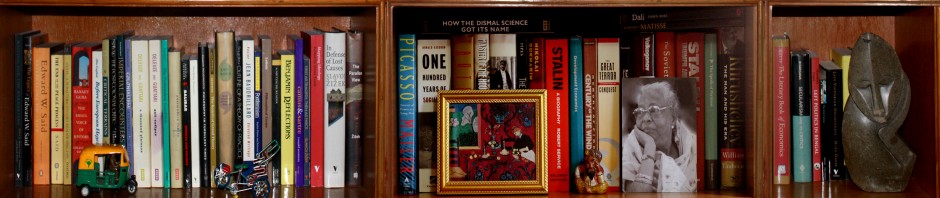পর্ব ::৭৮
পূর্বে প্রকাশিতের পর
সংবিধানের ১০নং ধারামতে ‘শোষণমুক্ত’ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হলেও এর অর্থ উক্ত ধারায় বা অন্য কোনো ধারাতেও স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়নি। এটা সংবিধান প্রণেতাদের বা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে ধ্রুপদি সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেই ঐকমত্য আগেও ছিল না, পরেও দেখা যায় না। কালক্রমে বিশেষত সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশে প্রথাগত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মাধ্যমে এটুকু অন্তত প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র মানে কেবল উৎপাদনের সব খাতে ‘রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা’ প্রতিষ্ঠা করা নয়। আমি বরং বলব যে, সুদূর ১৯৭২ সালে বসেই বঙ্গবন্ধু ও তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা সমাজতন্ত্রের প্রথাগত সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে আসার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্য আমরা এর আগেই উদ্ৃব্দত করেছি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা নয়, ব্যক্তিগত (পুঁজিবাদী) মালিকানাও থাকতে পারে, অবশ্যই নিয়ম-নীতির চৌহদ্দি মেনে চলাসাপেক্ষে। রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা ও ব্যক্তিগত (পুঁজিবাদী) মালিকানার মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকতে হবে এবং এ দুইয়ের পারস্পরিক অনুপাতে কালের বিচারে হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। যেটাই হোক না কেন, একদিকে পুঁজিপতিদের যেমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে দেওয়া হবে না, আবার অন্যদিকে তাদের অন্যায় প্রভাব খাটানোর সুযোগও দেওয়া হবে না। এক ভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের রূপকল্প নির্মাণের জন্য তাজউদ্দীনের বক্তব্যটি পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পুনরায় স্মরণযোগ্য:
‘আজকে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত পুঁজিতে যে সংশয়ভাব দেখা দিয়েছে, তাতে শুধু এটাই আমরা বলতে পারি, আইনের বিধান মোতাবেক ব্যক্তিগত মালিককে যেটা দেওয়া হবে সেটার মালিকানা সে নিশ্চয়ই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারবে। ….কিন্তু পুঁজিপতিদের তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। … ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ আমরা ততটুকু দেব, যতটুকু উৎসাহ দিলে ব্যক্তিগত শোষণ, ব্যক্তিগত বঞ্চনা এবং ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রভাব ঘটাবার সুবিধা ব্যক্তি মালিকানায় থাকে না। এটা পরিস্কার থাকা ভালো।’
পরবর্তীকালে প্রথাগত সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার নানা কারণের মধ্যে একটি ছিল বাজার-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে চালু না করতে পারার ব্যর্থতা। অর্থনীতির সবকিছু সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা Central Planning-র নামে ‘এক কেন্দ্র’ থেকে প্রশাসনিকভাবে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত এক পর্যায়ে সোভিয়েত ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাহাত্তরের সংবিধানের রূপকারেরা এই ভুল গোড়া থেকেই পরিহার করতে পেরেছিলেন। এবং পেরেছিলেন বলেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ের ১৩নং ধারায় রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী এবং ব্যক্তিগত মালিকানাকে যুগপৎ সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে রেখে ছিলেন। এই তিনটিই ছিল সংবিধান অনুযায়ী জনগণের মালিকানার তিনটি ধরন। Social Ownership of means of production বলতে বাহাত্তরে সংবিধানের রূপকারেরা শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাকে বোঝাননি, রাষ্ট্রের মালিকানার পাশাপাশি সমবায়ী ও ব্যক্তি-মালিকানাকেও বুঝিয়েছেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের Principles of Ownership বলতে গিয়ে ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্রের মালিকানা হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে ‘উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ’ : The People shall own or control the instruments and means of production and distribution, and with this end in view, ownership shall assume the following forms’- যথাক্রমে state ownership, ‘co-opertive ownership’, এবং‘private ownership’ (within such limits as may be prescribed by law) । এরকম সংজ্ঞা নিউ ইকোনমিক পলিসির লেনিনের বা সংস্কারপন্থী নিকোলাই বুখারিনের অথবা পোলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঙ্গের পছন্দ হতো তাতে আমার অন্তত সন্দেহ নেই।
সমাজতন্ত্র ও তার মধ্যে তিন ধরনের মালিকানা নিয়ে সেদিনের সংসদীয় বিতর্কে দুটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। একটি হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে পারে কিনা এ নিয়ে তত্ত্বগত বিতর্ক। অন্যটি হচ্ছে, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক। প্রথম দল চাইছেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি খাত থাকুক এবং শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই নয়, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে ব্যক্তি খাত কালক্রমে বিকাশও লাভ করুক। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও আছাদুজ্জামান খান অনেকটা এই লক্ষ্যে যুক্তির জাল বিস্তার করছিলেন। তাদের আলোচনার তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল বামধারার দল ও ভাবাদর্শের প্রতি। সংসদে যার কনক্রিট লক্ষ্যবিন্দু ছিলেন ন্যাপের সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত। সংখ্যায় এরা অবশ্য ছিলেন মাইনোরিটি। অন্যদিকে, যারা বিশেষভাবে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অসম্ভব- এদের মধ্যে ছিলেন মেজোরিটি গণপরিষদ সদস্য। তারা বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ও প্রতিতুলনা টেনে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকেই ‘অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে’ বিচরণ করতে হবে এবং ‘গতিশীল ভূমিকা’ পালন করতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এরা সে লক্ষ্যে সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদের মৌলিক গুরুত্বকে জোরেশোরে তুলে ধরেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ থেকে ড. কামাল হোসেন প্রাগ্রসর সব রাজনৈতিক নেতাই- যারা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন দীর্ঘকালের লড়াই-সংগ্রামে- এই ৪৭নং ধারার প্রশ্নে ছিলেন অবিচল। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলার দাবি রাখে।
বাহাত্তরের সংবিধানে যেসব গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তার পরিধি বিপুল। Liberty Principle-এর ক্ষেত্রে কোনো আপস না করে জোরেশোরে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। ৩৯(১) ধারায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, এর ‘ক’ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং এর ‘খ’ ধারায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ২৯(১) ধারায় সরকারি নিয়োগ লাভে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ এবং ৪০ অনুচ্ছেদে যে কোনো আইনসংগত পেশা, বৃত্তিগ্রহণ, কারবার বা ব্যবসা-পরিচালনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে। সেই সঙ্গে ৪২(১) ধারায় দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে সম্পত্তির অধিকার- ‘আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে’- প্রত্যেক নাগরিককে ‘সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা’ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তির ওপর অধিকারের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজার-অর্থনৈতিক ধারায় বিকাশের জন্যও সম্পত্তির অধিকার বা property rights একটি মৌলিক ধারণা। প্রপার্টি রাইটস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হচ্ছে : transaction costs-এর ধারণা। কোনো সম্পত্তির ওপরে মালিকানা প্রতিষ্ঠা, মালিকানার হাতবদল এবং মালিকানা রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত খরচকে :transaction costs বলে। যে সমাজে এই সম্পত্তি সংক্রান্ত :transaction costs কম সেই সমাজ উৎপাদন নৈপুণ্যে আরও বেশি এগিয়ে। তবে নিকোলাস স্টার্ন দেখিয়েছেন যে, property rights শুধু ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প, কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায়ী মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-কর্মকাণ্ডের সফল পরিচালনার জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রপার্টি রাইটস বলতে স্টার্ন মূলত তিনটি অধিকারকে বুঝিয়েছেন- এর মধ্যে রয়েছে ‘Right to Manage’, ‘Right to Income’ এবং ‘Right to Protect’। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এসব অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সেই প্রতিষ্ঠানটি ঠিক মতো চলতে পারে না। সেক্ষেত্রেই আমি ৪২(১) ধারায় প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকারকে ‘গণতান্ত্রিক অধিকারের’ মধ্যে গণ্য করেছি- শুধু পুঁজিবাদী সম্পত্তি-অধিকারের অংশ হিসেবে দেখিনি।
উপরোক্ত গণতান্ত্রিক ধারাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ৪১ নং অনুচ্ছেদের ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’ ধারাও। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা মনে রেখে এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের ‘যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের’ অধিকারের কথা। এমনকি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী ‘কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না’- এ কথাও ৪১(২) ধারায় আলাদা করে সংযোজিত হয়েছিল। এছাড়াও সংবিধানের ‘মৌলিক অধিকার’-এর অধ্যায়ের ২৭নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮নং ধারায় ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যরোধ এবং ধর্ম-বর্ণ নারীপুরুষ নির্বিশেষে সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা স্পষ্ট করে উল্লেখিত ছিল এই সংবিধানে। এসব কিছুকেই আমরা একদিক থেকে ‘গণতান্ত্রিক’ অধিকার, অন্যদিক থেকে ‘সেক্যুলার’ (ধর্ম-নির্বিশেষ) অধিকার হিসেবে পাঠ করতে পারি।
উল্লেখ্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে Libertarian ও Economic Egalitarian (তথা মার্কসবাদীরা) এক জোটে জড়ো হবেন, তা যতই এই নৈতিক সহাবস্থান তাদের রাজনীতির পক্ষে অস্বস্তিজনক হোক না কেন। কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দেখান তাদের বক্তব্যেও সপক্ষে। যেমন, মানুষ নিজে যা উৎপাদন করে তার ওপরে তার মৌলিক অধিকার রয়েছে বা মালিকানাস্বত্ব রয়েছে- এ কথা লিবারটারিয়ানরা জোরেশোরে বলে থাকেন। এজন্যই তারা মনে করে থাকেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকারেই (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা) হস্তক্ষেপ করার শামিল। অন্যদিকে, ‘আমার উৎপাদনের ওপরে কেবল আমার অধিকার’- একথাটা কট্টর বামপন্থিরা বুঝে না-বুঝে বলে থাকেন। Right to one’s labour- এটা এই ধারার প্রগতিশীলদের এক পুরোনা দাবি। (অবশ্য উৎপাদনের ফল যদি কেবল শ্রমের ফসল না হয়ে বিভিন্ন উপাদানের সমবেত অবদানের কারণে অর্জিত হয়- যেমন, Entrepreneourship, প্রযুক্তি বা উদ্ভাবনী প্রতিভার কারণে- তাহলে উৎপাদনের সবটুকু ফল কেবল আমার একথা আর বলা চলে না নিঃসংশয়ভাবে।) এরকম এক রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন ফার্দিনান্দ লাসাল (Lassalle)। শেষ জীবনের একটি লেখা ‘ক্রিটিক অব দ্য গথা প্রোগ্রামে’ মার্কস তৎকালীন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ফার্দিনান্দ লাসাল-এর Rights to Labour তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। ‘শ্রমিক হিসেবে আমি যা উৎপাদন করছি তার পুরোটাই কি আমার প্রাপ্য’- এ প্রশ্ন রেখে মার্কস দেখিয়েছিলেন বাস্তবে সেই উৎপাদনের কিছু অংশ যাবে পুঁজির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে বা নবায়নে, কিছু অংশ যাবে নতুন বিনিয়োগে, কিছু অংশ সামাজিক শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অবকাঠামো প্রভৃতি Social Consumption খাতে, কিছু অংশ আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায়- মোট কথা National Accounts-এর যাবতীয় বণ্টনের নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সাথে পালনের পরই কেবল যা অবশিষ্ট থাকবে তা শ্রমিকদের ‘বেতন তহবিলে’ ঢুকতে পারে (অবশ্য সেই বেতন তহবিল থেকেও একটা অংশ পেনশন জাতীয় ভবিষ্য-তহবিলের বাবদ কেটে রাখতে হবে বৈকি, শ্রমিকদেরই সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনে)। দেখা যাচ্ছে, মার্কস বণ্টনের ব্যাপারটাকে সম্যকভাবে এবং সূক্ষ্ণভাবে বিচার করেছিলেন। কিন্তু সেই সূক্ষ্ণতা অনেক সময়ই পরবর্তীকালের মার্কসবাদী আলোচনায় রক্ষিত হয়নি। এ কারণেই অমর্ত্য সেন তার ‘আইডিয়া অব জাস্টিস’ বইয়ে লিখতে পেরেছেন যে, The idea of the right to the fruits of one’s labour can unite right-wing libertarians and left-wing Marxists (no matter how uncomfortable each might be in the company of the other) এবং এটা লেখার পরপরই ফুটনোটে যোগ করেছেন যে, মার্কস এরকম কোনো মতে শামিল ছিলেন না : “As, it happens, Karl Marx himself became rather sceptical of the ‘right to one’s labour’ which he came to see as a ‘bourgeois right’, to be ultimately rejected in favour of ‘distribution according to needs’, a point of view he developed with some force in his last substantial work, The Critique of the Gotha Program.”
[ক্রমশ]